মতামত
ইরানের পরে পাকিস্তান পরবর্তী টার্গেট? পশ্চিমা বর্ণনা-রাজনীতি ও ভূরাজনৈতিক হুমকির ছায়া
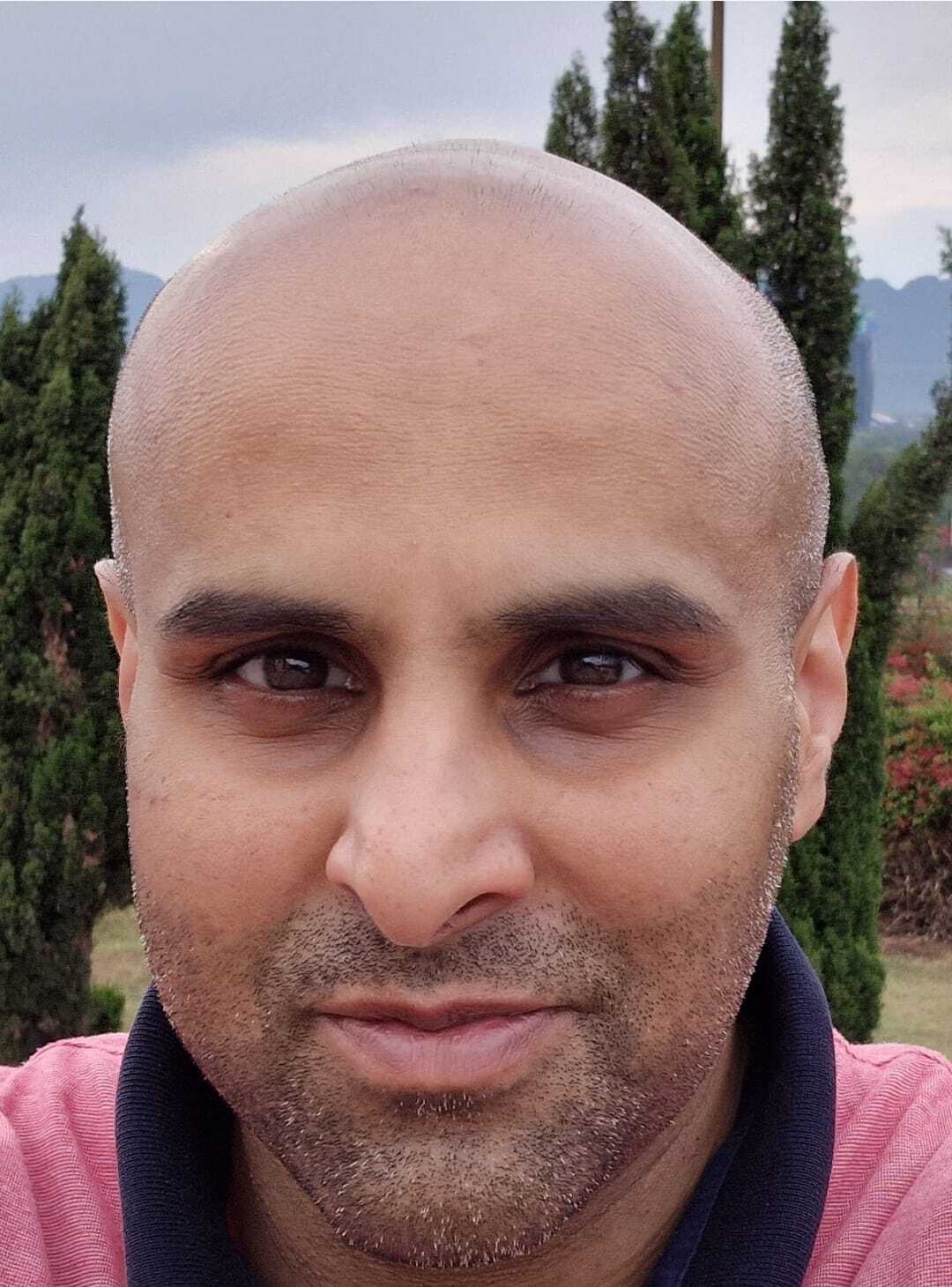
ফয়সাল হানিফ
মিডিয়া বিশ্লেষক, সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং

যখন গত মাসে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ সতর্ক করে বলেন, “মুসলিম দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে একে একে সবার পালা আসবে,” সেটি ছিল কেবল কূটনৈতিক আক্ষেপ নয়—বরং এক ধরনের সাংকেতিক এসওএস।
যখন ইসরায়েল গত মাসে সরাসরি ইরানি ভূখণ্ডে হামলা চালায় এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রনেতা ও গণমাধ্যম উল্টো ইরানকেই হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করে, তখন এক শীতল প্রশ্ন উঠে আসে: এরপর কার পালা?
অনেকে একে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন, তবে যেসব দেশকে "বৈশ্বিক নিরাপত্তা"র নামে দশকের পর দশক ধরে কালিমালিপ্ত, বৈধতাহীন এবং ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে—সেই চেনা ছককে আর অস্বীকার করার উপায় নেই।
আজকের পশ্চিম আর ট্যাংক বা জাতিসংঘের প্রস্তাবনার ওপর নির্ভর করে না। আজ তাদের হাতিয়ার শিরোনাম, অর্থনৈতিক অবরোধ ও ন্যারেটিভ যুদ্ধ। যখন এগুলো ব্যর্থ হয়, তখন ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে অজুহাত বানিয়ে আগাম হামলা জায়েজ করা হয়।
এই প্রসঙ্গে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে একটুখানি কৃতিত্ব দেওয়া যায়: তিনি অনেক সময়ই মুখের কথায় ভেতরের সত্যটা বলে ফেলেন। গত কয়েক দশক ধরেই তিনি মুসলিম দেশগুলোর পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন নিয়ে ভয় ছড়িয়েছেন। এক সময় ইরাককে বোমা মারা হলো, লিবিয়াকে নিঃশস্ত্র করা হলো, এখন ইরানকে চেপে ধরা হচ্ছে।
আর পাকিস্তান? এটি যেন শেষ 'ফ্রন্টিয়ার'—কারণ, পাকিস্তান কোনো দেশ দখল করেনি, বরং এটি পশ্চিমা ও জায়নবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত, আদর্শিক এবং প্রযুক্তিগত অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।
এই বক্তব্য ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি এমন একটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে যেখানে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তান এমন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে যা যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। এর সত্যতা প্রমাণের দরকার নেই—এই ধরনের সন্দেহ উস্কে দিতেই যথেষ্ট।
এই পরিস্থিতি ২০০১ সাল নয়। কেউ আজকাল আর ঝাপসা স্যাটেলাইট ছবিতে “নাশকতামূলক অস্ত্র” বিক্রি করছে না। তবে লক্ষ্য সেই পুরনোই: পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিকে বৈশ্বিক ঝুঁকি হিসেবে চিত্রায়ন করা।
ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ও নিরাপত্তা গবেষণা সংস্থাগুলো এখন নিয়মিত পাকিস্তানকে একটি অস্থিতিশীল, চরমপন্থার ঝুঁকিতে থাকা এবং পরমাণু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এক রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরছে।
সম্প্রতি ডেইলি মেইল একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে আবারো সেই পুরোনো আখ্যান সামনে আনে: পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নাকি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে, এবং তাদের পরিচালনা নাকি যুক্তি নয়—ধর্মীয় উন্মাদনায় চালিত। আর এই ব্যাখ্যা আবার এক ‘ভারতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক’-এর ওপর ভর করে পাকিস্তানকে একটি চরমপন্থী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করে।
পাকিস্তান নিয়ে পশ্চিমের সমস্যা হলো—ওরা কী করেছে তা নয়, বরং ওরা কী প্রতিনিধিত্ব করে—একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, একটি পারমাণবিক শক্তি, এবং চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র। বর্তমান বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামোয় এই ত্রয়ীই পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ‘রেড লাইন’।
কিন্তু যারা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে, তাদের কাছে এসব বক্তব্য ফাঁপা মনে হয়। সাত দশকের ইতিহাসে পাকিস্তান কখনোই কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে ক্ষমতায় আনেনি। জনসাধারণ ধারাবাহিকভাবে ধর্মতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
অপরদিকে, ভারত একাধিকবার একজন নেতাকে ক্ষমতায় এনেছে, যিনি ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং বহু পর্যবেক্ষক মনে করেন তিনি তা অনুমোদন করেছেন কিংবা চোখ বন্ধ রেখেছেন। আজ সেই নেতা, নরেন্দ্র মোদি, এমন একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করছেন যা প্রকাশ্যেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে—যেখানে মুসলিমসহ সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক করা হয়।
তবু ব্রিটিশ ও পশ্চিমা গণমাধ্যমে ভারতকে ‘সাবালক রাষ্ট্র’, ‘যুক্তিবাদী পক্ষ’, এবং ‘গণতন্ত্রের আলো’ হিসেবে দেখা হয়। এই দ্বৈত মানদণ্ড শুধু হাস্যকর নয়—প্রয়োজনে ভয়ানকও।
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলার ঘটনার পর, ভারতের প্রতিক্রিয়া দেখার মতো ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ ছাড়াই ভারত সীমান্ত পেরিয়ে সামরিক হামলা চালায়। পশ্চিমা গণমাধ্যম ভারতীয় সরকারের বিবৃতি চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে, আর পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের টেলিভিশনে এনে আবারো ‘সন্ত্রাসবাদ’-এর প্রশ্নে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়—এক বিষণ্ন পুনরাবৃত্তি।
এখানে এক নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট যুক্তি কাজ করে: হিন্দুত্ববাদী উগ্রতা যত ভয়ানকই হোক, সেটিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়—খারাপ হতে পারে, কিন্তু বৈধ। অন্যদিকে ইসলামপন্থা, ক্ষমতার ধারেকাছেও না থাকলেও, সবসময় অস্তিত্ববাদী হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়।
এটি কেবল অলস সাংবাদিকতা নয়, বরং এটি অবিচারের পক্ষে এক প্রাতিষ্ঠানিক রেহাই তৈরি করে। ভারতের চরমপন্থা বা আগ্রাসনকে প্রশ্ন না করে পশ্চিমা মিডিয়া দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যকে আরও বিকৃত করে তুলছে—যেখানে পাকিস্তান চিরকাল ‘উসকানিকারী’, আর ভারত সব সময় ‘শান্তিপূর্ণ শক্তি’, এমনকি যদি সেটি ক্রমাগত কর্তৃত্ববাদে নিমজ্জিত হয়।
এই প্রশ্নটি শুধু ন্যায়ের নয়, বরং আঞ্চলিক শান্তির—দক্ষিণ এশিয়ায় কখনো কি স্থিতিশীলতা আসবে, যদি একটি রাষ্ট্রের আগ্রাসনকে হালকা করে দেখা হয়, আর আরেক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া বহুদিন ধরেই ইসরায়েল, ভারত ও অ্যাংলো-আমেরিকান নিরাপত্তা কাঠামোর কাছে অস্বস্তির কারণ। এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমনকি মডার্ন ডিপ্লোমেসি–র মতো প্রকাশনাও প্রকাশ্যেই লিখছে, নীতিনির্ধারকেরা যেটি গোপনে হয়তো কল্পনা করছেন—ইরানকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর পাকিস্তানকে নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে।
এখানে কেবল ভূরাজনীতি নয়, মনস্তত্ত্বও কাজ করছে। জনমতকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে একটি পারমাণবিক ইসলামী প্রজাতন্ত্র—যার রয়েছে চীনের সঙ্গে কৌশলগত সেতুবন্ধ—তাকে আর স্বাধীন রাষ্ট্র নয়, বরং ‘বিশ্বব্যবস্থার জন্য হুমকি’ হিসেবে মনে হয়।
কেবল পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডার নয়, বরং তাদের ভূ-কৌশলগত অবস্থানই চিন্তার কারণ। ইসলামাবাদ যখন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে, বিশেষ করে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC)-এর মাধ্যমে, তখন এটি একটি পোস্ট-কলোনিয়াল নির্ভরতা থেকে এক বহুপাক্ষিক চ্যালেঞ্জে রূপ নিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর সব পথ এখন বেইজিংয়ের দিকে যায়—যুক্তরাষ্ট্র জানে, ব্রিটেন জানে, ইসরায়েলও জানে। আর এই করিডোরে পাকিস্তানের অবস্থানই একে আঞ্চলিক সমস্যা থেকে বৈশ্বিক কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।
সম্প্রতি ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার পটভূমিতে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনির যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ নিয়ে প্রশ্নের চেয়ে উত্তর কম। এটি কি মোহভঙ্গ প্রতিরোধ? হুঁশিয়ারি? কূটনৈতিক পুনর্মূল্যায়ন? উত্তর যাই হোক, এটি পাকিস্তানের বৈশ্বিক অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তাকে সামনে এনেছে—একটি রাষ্ট্রকে একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় আবার অবিশ্বাসিত হিসেবে দেখা হচ্ছে।
শেষ পর্যন্ত, পশ্চিমের সমস্যা পাকিস্তান কী করেছে, তা নয়। সমস্যা হলো—পাকিস্তান কী প্রতিনিধিত্ব করে: একদিকে এটি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তিধর, এবং তৃতীয়ত এটি চীনের মিত্র। বর্তমান বৈশ্বিক ক্ষমতা কাঠামোয় এই ত্রিমাত্রিক পরিচয়ই সবচেয়ে বড় সীমারেখা।
২০০৯ সালে, মঙ্গোল সাম্রাজ্য নিয়ে একটি পোস্টগ্র্যাজুয়েট সেমিনারে এক ব্রিটিশ অধ্যাপক ক্লাসরুমে একটি মানচিত্র ছুড়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—“তুমি কি জানো পাকিস্তানকে বিভক্ত করার নিওকনservative পরিকল্পনা আছে?” তিনি আমাকে প্ররোচিত করতে চাননি। তিনি জানতেন আমি পাকিস্তানের সংস্কৃতি ভালোবাসি, ক্রিকেট দলের ভক্ত, এবং দেশের বাস্তবতাকে স্পর্শ করি। ওটা ছিল সতর্কবার্তা—ষড়যন্ত্র নয়।
আজ, সেই মানচিত্র আর ষড়যন্ত্র বলে মনে হয় না। সেটা যেন এক চলমান কৌশলের খসড়া।
-ফয়সাল হানিফ সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং-এ একজন মিডিয়া বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি দ্য টাইমস এবং বিবিসি-তে সংবাদ প্রতিবেদক ও গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত।
ইসলামোফোবিয়া: বাংলাদেশে বাস্তবতার নাম, না রাজনৈতিক ঢাল

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
বাংলাদেশে “ইসলামোফোবিয়া” শব্দটা বহু সময় বাস্তবতা বোঝানোর জন্য নয়, রাজনীতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। শব্দটা উচ্চারণ করলেই এক ধরনের নৈতিক ঢাল পাওয়া যায়। আপনি যদি জামায়াত বা অন্য কোন রাজনৈতিক বর্গ যেমন হারুন ইজহারদের সমর্থকদের ইতিহাস, ধর্মকে শাসনের প্রকল্প বানানো, বা কট্টর রাজনীতির সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, সেটাকে সহজে “ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ” বানিয়ে দেওয়া যায়। তখন যুক্তির জবাব দিতে হয় না। ব্যক্তির কাজ কিংবা দলের রাজনৈতিক দায় নিয়ে কথা না বলে পরিচয়ের মামলা দাঁড় করানো যায়। আর পরিচয়ের মামলায় কথা বলা কঠিন, কারণ কেউই “ধর্মবিদ্বেষী” তকমা নিতে চায় না। ফলে সমালোচনার জায়গা সংকুচিত হয়, বিতর্কটা আবেগের দিকে সরে যায়, এবং একটি দল নিজেকে “বিপন্ন মুসলমানদের প্রতিনিধি” হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।
এই কৌশলের আরেকটা সুবিধা আছে, যেটা আরও গভীর। আইনশাসনের অভাব, গোয়েন্দা রিপোর্টের নামে নিয়োগে বৈষম্য, নিরাপত্তার নামে হয়রানি, অথবা মিডিয়ায় দাড়ি-টুপি নিয়ে স্টেরিওটাইপিং, এগুলো আসলে আলাদা আলাদা সমস্যা। প্রতিটির আলাদা দায় আছে, আলাদা সমাধান আছে। কিন্তু সবকিছুকে “ইসলামোফোবিয়া” বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললে দায়টা ঝাপসা হয়ে যায়। সবকিছু মিশে গিয়ে “সেকুলার শক্তি” নামে একটা অস্পষ্ট শত্রু তৈরি হয়। অস্পষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে কথা বলা সহজ, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত, নির্দিষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। তাই ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এক শব্দে সব ধরতে, জবাবদিহির চাপ কমাতে, সমর্থকদের সামনে একটা সরল গল্প দাঁড় করিয়েছে: "আমরা আক্রান্ত, তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশে ইসলামফবিয়া চরম ভাবে আছে"।
আসুন এই ফ্রেমটিকে প্রশ্ন করি, ক্রিটিকালি দেখি। এই ফ্রেম বুঝতে হলে আগে দুটো জিনিস আলাদা করা জরুরি। একদিকে আছে কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া, যেখানে রাষ্ট্রের আইন, নীতি, নিয়োগব্যবস্থা, নিরাপত্তা কাঠামো এমনভাবে সাজানো থাকে যে মুসলমান পরিচয়টাই ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে আছে সামাজিক ইসলামোফোবিয়া বা ধর্মচর্চা-বিদ্বেষ, যেখানে পোশাক, দাড়ি-টুপি, হিজাব, মাদ্রাসা শব্দটাই উপহাসের বস্তু হয়, এবং ধর্মীয় সিম্বল দেখলেই মানুষকে অগ্রিম “পিছিয়ে পড়া” বা “বিপজ্জনক” ধরে নেওয়া হয়। ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই দাবি করে বাংলাদেশে দুটোই “চরম” আকারে আছে, এবং এর জন্য দায়ী দেশীয় “সেকুলার এলিট”। আর এই “সেকুলার এলিট”-এর মধ্যে ধীরে ধীরে সবাই পড়ে, যারা ইসলামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা করবে। আগে এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পড়ত, এখন এর মধ্যে বিএনপিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, যে-ই ইসলামপন্থী রাজনীতির বিরোধী, সে-ই সম্ভাব্য “সেকুলার এলিট”। রাজনীতিতে এর থেকে শক্তিশালী ফ্রেম হতেই পারে না। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় দেখলে এই দাবিটা অনেক সময় ভুল জায়গায় দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে মুসলমান পরিচয়ের ভিত্তিতে ধারাবাহিক কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া ছিল, এমন শক্ত প্রমাণ হাজির করা কঠিন। বরং যা বেশি দেখা গেছে, তা হলো রাজনৈতিক পরিচয়ভিত্তিক সেগ্রিগেশন, ক্ষমতার আনুগত্য যাচাই, আর নিরাপত্তাকরণের নামে ধর্মীয় পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র এখানে মুসলমান পরিচয়কে শত্রু হিসেবে দেখেছে, এমন নয়। রাষ্ট্র দেখেছে বিরোধিতার সম্ভাবনা, এবং সেটাকে দমাতে গিয়ে ধর্মীয় প্রতীককে শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যটা ধরতে না পারলে আমরা সমস্যার নাম ভুল করি, আর নাম ভুল হলে সমাধানও ভুল দিকে যায়।নিয়োগের কথাই ধরা যাক। গত এক দশকে বাংলাদেশের বহু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় “গোয়েন্দা রিপোর্ট”, রাজনৈতিক আনুগত্য, দলীয় নেটওয়ার্ক, এবং “ঝুঁকিপূর্ণ পরিচয়” শনাক্ত করার প্রবণতার কথা শোনা গেছে। অনেকে বলেছেন, মাদ্রাসায় পড়েছে বলে বা দাড়ি-টুপি রাখে বলে চাকরিতে বাধা এসেছে। এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্লেষণটা “কারা বাধা পেল” থেকে “কী যুক্তিতে বাধা পেল” দিকে সরালে অন্য ছবি দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল পরিবারের জামায়াত সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, বিএনপি-ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আছে কি না, ক্যাম্পাস রাজনীতিতে শিবির বা বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিচয় নয়, রাজনৈতিক পরিচয় এবং সম্ভাব্য বিরোধিতার আশঙ্কাই ছিল মূল ফ্যাক্টর।
সমস্যাটা কোথায়? রাজনৈতিক স্ক্রিনিং যখন হয়, বাস্তবে ধর্মীয় চেহারার মানুষ বেশি ভোগে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে দৃশ্যমান ধর্মীয় প্রতীকের সঙ্গে জুড়ে গেছে। ফলে দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, মাদ্রাসা শিক্ষা, এগুলো অনেক সময় “রাজনৈতিক সন্দেহ”র শর্টকাট হয়ে ওঠে। একজন নির্দোষ মাদ্রাসা ছাত্রও সেই সন্দেহের আওতায় পড়ে। ক্ষতিটা বাস্তব। কিন্তু এটাকে ইসলামোফোবিয়া বললে ভুলটা হয় এই জায়গায় যে “ধর্মচর্চা” আর “রাজনৈতিক ইসলাম” একসাথে গুলিয়ে যায়। রাষ্ট্র এবং শহুরে মধ্যবিত্ত পরিসর অনেক সময় ইসলামকে নয়, ইসলামকে শাসনের প্রকল্প বানানো নেটওয়ার্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। সেই নিয়ন্ত্রণের পথে ডিউ প্রসেস ভেঙেছে, সন্দেহ প্রমাণে পরিণত হয়েছে, এবং নির্দোষ মানুষও ভুগেছে। কিন্তু এটাকে ধর্মবিদ্বেষ বলে ধরলে মূল অপরাধী, অর্থাৎ পার্টি-স্টেটের কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়া আড়াল হয়ে যায়। তখন প্রতিষ্ঠান, নীতি, পুলিশিং, নিয়োগ প্রক্রিয়া, এগুলোর জবাবদিহির বদলে আমরা “ধর্মীয় অনুভূতি”র ধোঁয়ায় ঢুকে পড়ি।
একই ভুল পাঠ দেখা যায় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাতেও। মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বা নাটকে রাজাকার চরিত্রকে দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি পরানো, তাকে ধর্মীয় সিম্বল দিয়ে “চিহ্নিত” করা নিয়ে অভিযোগ ওঠে যে এটি ধর্মচর্চাকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি করছে। এখানে দুটো সত্য পাশাপাশি আছে। পপুলার কালচার শর্টকাট ব্যবহার করে; ভিজুয়াল কোডিং করে; খলনায়ক দেখাতে দ্রুত কিছু প্রতীক ধরে। বাংলাদেশে দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি বহু বছর ধরে শুধু ধর্মীয় সিম্বল নয়; এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্মৃতি এবং রাজনৈতিক ঘরানার সাংস্কৃতিক চিহ্নও। বিশেষ করে যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা আসে তখন জামাত নেতাদের মিডিয়ায় উপস্থাপন করতে দাড়ি টুপি ব্যাবহার হয়। আপনি যদি বাস্তবে দেখেন জামাতের যে নেতারা সেই সময় পাকিস্তান আর্মির সাথে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল তাদের প্রায় সবারই তো দাড়ি ছিল ও টুপি পরতেন। এখন তাদের কি শেভ করে উপস্থাপন সম্ভব? বাস্তবতা হল, যুদ্ধাপরাধের বিচার, জামায়াতের ভূমিকা, ৭১ পরবর্তী ছাত্ররাজনীতি, এগুলোর কারণে এই পোশাক অনেক সময় “রাজাকার-পলিটিক্স” এর শর্টহ্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এতে যত না ধর্মীয় চরিত্র আকারে দেখানো হয় তার থেকে বেশি “রাজাকার-পলিটিক্স” এর সিম্বল আকারে দেখানো হয়ে থাকে।
এই উপস্থাপনাকে “ইসলামোফোবিয়া” বললে অতিরঞ্জন হয়। এখানে বেশি সঠিক হবে বলা: রাজনৈতিক শত্রুকে দেখাতে গিয়ে ধর্মীয় প্রতীককে অলসভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে সাধারণ ধর্মচর্চাকারী মানুষও স্টেরিওটাইপের শিকার হতে পারে। সমালোচনা এখানেই হওয়া উচিত। কারণ সমস্যাটা ইসলাম ঘৃণা নয়, সমস্যাটা অলস ভিজুয়াল রাজনীতি এবং স্মৃতির জটিলতা না মানার অভ্যাস।
শহুরে সমাজে বোরখা বা হিজাব নিয়ে তিরস্কার, “বোরখা মানেই গোঁড়া” টাইপ মন্তব্য, দাড়ি-টুপি দেখে অগ্রিম সন্দেহ, এগুলোও বাস্তব। ( পাশাপাশি সমাজে পশ্চিমা পোশাককে বিশেষ করে যারা ধর্মীয় পোশাক পরেন না তারাও খারাপ মেয়ে বা ছেলে এই সন্দেহের শিকার হয়ে থাকেন। ) কিন্তু এগুলোকে ইসলামোফোবিয়া বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললেও সমস্যা হয়। বাংলাদেশে ইসলাম পাবলিক লাইফের কেন্দ্রে। আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সামাজিক নর্ম, নৈতিকতা নির্মাণ, সবখানেই ইসলামের উপস্থিতি প্রবল এবং বহু জায়গায় মর্যাদাপ্রাপ্ত। কাজেই কিছু স্টিগমা থাকা মানেই “ইসলামবিদ্বেষী সমাজ” নয়। বরং এটা শহুরে মধ্যবিত্তের শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অহংকার, যেখানে ধর্মীয় অনুশীলনের নির্দিষ্ট ধরনকে “গ্রাম্য” বা “ব্যাকওয়ার্ড” আর কিছু ধরনকে "পশ্চিমা" ধরে নেওয়া হয়। এটাকে আমি ইসলামোফোবিয়ার চেয়ে “ক্লাস-কালচার স্টেরিওটাইপ” বলব।
সবচেয়ে কঠিন জায়গা আসে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। ২০০০ দশকের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, ধর্মীয় সংগঠন, এবং ধর্মভিত্তিক নেটওয়ার্কের ওপর নজরদারি, হয়রানি, আটক, নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এখানে কোনো দ্বিধা না রেখে বলা দরকার: বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সীমা লঙ্ঘন করেছে, মানবাধিকারের লঙ্ঘন করেছে। ডিউ প্রসেস ভেঙেছে। সন্দেহকে প্রমাণ বানিয়েছে। নিরাপত্তার নামে নাগরিক অধিকারকে সেকেন্ডারি করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা কি মুসলিম পরিচয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনীতি? আমার মনে হয় না। কারণ একই রাষ্ট্র একই সময়ে ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারও করেছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়েছে, ধর্মীয় নেতারা অনেক রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়েছেন, আর মাদরাসা বানিয়েছেন, এবং ইসলামকে সংবিধানিক ও সামাজিক পরিসরে স্বাভাবিক অবস্থানেই রেখেছে। এখানে টার্গেট ছিল “সন্ত্রাস” এবং “উগ্রপন্থী নেটওয়ার্ক”। ব্যর্থতা ছিল বড় জালের মতো করে ধর্মীয় পরিসরে জাল ফেলা, যেখানে নির্দোষ মানুষ ধরা পড়ে, আর রাজনৈতিক সুবিধার জন্য “জঙ্গি” তকমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। আর তাই হয়েছে। প্রকৃত সন্ত্রাসী আর রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। আওয়ামীলীগ সরকার হরে দরে সবাইকে জঙ্গি ট্যাগ করেছে। এই অবস্থাকে ইসলামোফোবিয়া বললে মূল ব্যর্থতা, অর্থাৎ আইনশাসনহীন নিরাপত্তা শাসন, আড়াল হয়ে যায়।
এইখানেই ইসলামপন্থী দলগুলোর ইসলামোফোবিয়া-থিসিসটা রাজনৈতিকভাবে লাভজনক ভাষা হয়ে ওঠে। প্রথমত, এটি রাজনৈতিক সমালোচনাকে ধর্মবিদ্বেষে রূপান্তর করে। আপনি যদি যুদ্ধাপরাধ, সহিংস ছাত্ররাজনীতি, বা ধর্মকে শাসনের প্রকল্প বানানোর সমালোচনা করেন, তারা বলবে আপনি ইসলামোফোবিক। বিতর্কের কেন্দ্রে রাজনীতি থাকে না, অনুভূতি এসে বসে। দ্বিতীয়ত, তাদের নিজেদের ভেতরের কঠিন প্রশ্ন, ক্ষমতা, নারী অধিকার, সংখ্যালঘু, ভিন্নমত সহনশীলতা, এগুলো চাপা দেওয়া সহজ হয়। তৃতীয়ত, বাস্তব সামাজিক স্টিগমাকে রাজনৈতিক পুঁজি বানানো যায়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ আর শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলকে তারা “সেকুলার বনাম ইসলাম” যুদ্ধ বানিয়ে দেয়।তাই বাংলাদেশে ইসলামোফোবিয়া আছে কি না, প্রশ্নটা হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর করা সহজ নয়। সামাজিক স্তরে কিছু স্টেরিওটাইপ আছে। নিরাপত্তা নীতির ভেতর ধর্মীয় পরিসরের ওপর অতিরিক্ত সন্দেহ এবং দমনও আছে। কিন্তু ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যে অর্থে বলেন, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজ মুসলমান পরিচয়কে কাঠামোগতভাবে টার্গেট করছে, সেই অর্থে বাংলাদেশকে ইসলামোফোবিক রাষ্ট্র বলা টেকে না। বাংলাদেশের বাস্তবতা বরং উল্টো দিকে টানে। এখানে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয়, পাবলিক লাইফের কেন্দ্রীয় নর্ম। এখানে বঞ্চনার বড় চালিকা শক্তি ছিল রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্ন, এবং নিরাপত্তাকরণের নামে বিরোধী সম্ভাবনাকে দমন করার প্রবণতা। আর সামাজিক স্তরের হেয় করার ঘটনাগুলোকে ইসলামোফোবিয়া বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললে আমরা সমস্যার সঠিক নাম হারাই।এই কারণেই আমি “ইসলামোফোবিয়া” বেশি সুনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করতে চাই, ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক প্রকল্পকে প্রশ্ন করতে চাই। চাকরি থেকে বঞ্চনা হলে বলব রাজনৈতিক বৈষম্য এবং পার্টি-স্টেটের লয়্যালটি টেস্ট। নিরাপত্তার নামে নির্যাতন হলে বলব ডিউ প্রসেস ভাঙা, আইনশাসনের ব্যর্থতা, নিরাপত্তা শাসনের স্বেচ্ছাচার। মিডিয়ায় দাড়ি-টুপি মানেই খলনায়ক হলে বলব সাংস্কৃতিক স্টেরিওটাইপিং এবং রাজনৈতিক প্রতীকের অপব্যবহার। কারণ নাম ঠিক থাকলে দায় ঠিক থাকে। দায় ঠিক থাকলেই সমাধান ধর্মীয় আবেগের নাটকে আটকে না থেকে নাগরিক অধিকারের বাস্তব রাজনীতিতে দাঁড়াতে পারে।
ব্যক্তিগত দায় বনাম প্রাতিষ্ঠানিক দায়: দায়মুক্তির এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের ঘটনা কাগজে পড়লে প্রথমে মনে হয় এটা যেন কোনো যুদ্ধের খবর। এক তরুণকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা প্রায় কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটা যুদ্ধ না, আমাদের এক সাধারণ গ্রাম। আর হামলাকারীও কোনো অজানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয়, অভিযোগ আছে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।
সুফিয়ানের অপরাধ কী? পরিবারের অভিযোগ, এক স্বজন কিশোরীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করেছিল সে। অর্থাৎ সে আসলে এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা শোনার বদলে কিছু লোক তাকে খুঁটিতে বেঁধে এমনভাবে কুপিয়েছে যে তার দুই হাত ও এক পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনা শুধু একটি বর্বর হামলার খবর না, এটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও আয়না।
ঘটনার পর আমরা দেখি পরিচিত চিত্র। শিবগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির সাদিকুল ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন, “কে বা কারা রাতের আঁধারে এ ঘটনা ঘটিয়ে জামায়াতের ওপর দোষ চাপাচ্ছে… জামায়াতের জড়িত থাকার প্রশ্নই আসে না।” স্থানীয় যে দুই জনের নাম উঠেছে, শাহ আলম ও আবদুর রাজ্জাক, তাদের তিনি দলের কর্মী হিসেবে মানেন, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। অর্থাৎ লোকগুলো জামায়াতের, কিন্তু কাজটি নাকি জামায়াতের না।
আমরা এই একই নাটক অন্য জায়গাতেও দেখেছি। উদীচী, ছায়ানট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমে হামলার আগে–পরে অনেক ছাত্রনেতা, বিশেষ করে ডাকসু, রাকসু, জাকসু আর শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু নেতা প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে। ফেসবুক লাইভে, মাইক হাতে মিছিলে তারা নাম–ধাম বলে বলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে, “ঘেরাও করতে হবে”, “শাস্তি দিতে হবে” ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে। কিন্তু হামলার পর যখন সমালোচনা শুরু হয়, মামলা হয়, আন্তর্জাতিক মহলেও খবর যায়, তখন হঠাৎ সব পাল্টে যায়। তখন শিবিরের প্রেস রিলিজ আসে, যেখানে বলা হয়, যারা উসকানিমূলক কথা বলেছে তারা নাকি “ব্যক্তিগতভাবে” বলেছে, দলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রনেতারা তখন বলেন, “আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে”, “আমি শুধু প্রতিবাদের কথা বলেছি”, “হামলার কথা বলিনি” ইত্যাদি।শিবগঞ্জের ঘটনার পরও আমরা একই কৌশল দেখি। লোকগুলো জামায়াতের সভা–সমাবেশে যায়, ব্যানারে থাকে, দলের নেতা–কর্মী হিসেবে পরিচিত; কিন্তু হামলার প্রশ্ন এলে সঙ্গে সঙ্গে দল বলে, “এরা কোনো দুষ্টচক্রের টার্গেট”, “নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতকে ফাঁসানো হচ্ছে।” এই জায়গাটাই আসল সমস্যা। জামায়াত ও শিবির একদিকে সংগঠিতভাবে রাজনীতি করবে, ধর্মের নামে জনমত তৈরি করবে, কর্মীদের নানা পদে বসাবে, আবার সহিংসতা বা সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠলেই সব দায় একেকটা ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেবে। দল সুবিধা নেবে, কিন্তু দায়িত্ব নেবে না।এই “ব্যক্তিগত দায়–দল দায়ী নয়” যুক্তি আসলে রাজনৈতিক পালানোর পথ। একটা সংগঠন যদি দাবি করে তার কর্মীরা খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ, আদর্শবান, কোরআন–হাদিসভিত্তিক জীবন চালায়, তাহলে সেই সংগঠনকেই প্রথমে আত্মসমালোচনা করতে হয় যে কেন তার কর্মীরা এমন ভয়াবহ সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। যদি সত্যি দলের ভূমিকা না থাকে, তাহলে দলই আগে এগিয়ে এসে তদন্ত দাবি করবে, ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়াবে, নিজেদের কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। বাস্তবে আমরা দেখি উল্টো ছবি: ভুক্তভোগীর বদলে অভিযুক্ত কর্মীদের সাফাই গাওয়া হয়, ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বানানো হয়, আর সবকিছুর জন্য “অজ্ঞাত” তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করা হয়।
এর মাধ্যমে কয়েকটা কাজ একসঙ্গে হয়। প্রথমত, কর্মীরা বুঝে যায় যে দল তাদের আড়াল করবে, ফলে সহিংসতা চালাতে তাদের ভয়ের মাত্রা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, দলের একটা “পরিষ্কার” ইমেজ তৈরির চেষ্টা চলে, যেন তারা মূলত শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দল, কিছু “উৎসাহী” ব্যক্তি মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, দলের তাতে কিছু করার নেই। তৃতীয়ত, আইন ও বিচারব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়, যাতে মামলা গায়ে লাগে না, রাজনৈতিক চাপও কম থাকে। এর ফল কী দাঁড়ায়? ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে ন্যায়বিচার দূরের স্বপ্ন হয়ে যায়। সুফিয়ানের মতো মানুষ সারাজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, আর যারা তাকে খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটেছে, তারা হয় “অজ্ঞাত লোক”, না হয় “ব্যক্তিগতভাবে ভুল করে ফেলা” কিছু মানুষ। সংগঠন থাকে নিরাপদে, আবার পরদিন একই ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে।
জামায়াত–শিবিরের রাজনীতি অনেক দিন ধরে এই দুই মুখে চলে আসছে। এক মুখে তারা নিজেদের “গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয়, ইসলামী” দল হিসেবে পরিচয় দেয়, ভোট চায়, মানবাধিকার আর ন্যায়বিচারের কথা বলে। আরেক মুখে মাঠের কর্মীদের মাধ্যমে তারা টার্গেট নির্ধারণ করে, কাদের “শাস্তি” দিতে হবে, কারা “ইসলামের শত্রু”, কারা “দেশদ্রোহী” – এসব ন্যারেটিভ ছড়ায়। পরে সেই ন্যারেটিভ বাস্তব হামলায় পরিণত হলে তারা বলে, “আমরা তো কাউকে কুপাতে বলিনি, আমরা শুধু কথা বলেছি।” এই দ্বিচারিতা দীর্ঘমেয়াদে শুধু প্রতিপক্ষের জন্য না, দেশের সব নাগরিকের জন্যই বিপজ্জনক। কারণ এতে একটি বার্তা স্পষ্ট হয়: সংগঠিত শক্তি সহিংসতার ভাষা ব্যবহার করতে পারে, কর্মীরা সেই ভাষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে, আর কোনো প্রতিষ্ঠানই তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারবে না। তখন রাজনীতি আর মতের লড়াই থাকে না; রাজনীতি হয়ে যায় ভয় দেখানোর খেলা।
আমার মনে হয়, সময় এসেছে এই খেলাটা স্পষ্ট করে ডেকে নাম ধরেই চেনার। যদি কোনো দলের কর্মীরা বারবার সহিংসতায় জড়ায়, যদি সেই দলের নেতারা নিয়মিতভাবে উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করেন, আর পরে প্রেস রিলিজ দিয়ে সব দায় “ব্যক্তিগত” বলে উড়িয়ে দেন, তাহলে সেখানে শুধু ব্যক্তিগত অপরাধের কথা বলে লাভ নেই। সেখানে সংগঠনগত দায়ের কথাও উঠবে, উঠতেই হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে না। জামায়াত–শিবির বা অন্য যে কোনো দলের ক্ষেত্রেই কথা একই: সংগঠন যদি সুবিধা নিতে পারে, তবে সংগঠনকেও দায়িত্ব নিতে হবে। আর রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে এই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়া, যাতে আর কোনো সুফিয়ানকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটে ফেলা না যায়, এবং কোনো সংগঠন তা “ব্যক্তিগত ভুল” ও "রাতের আঁধারের ঘটনা" বলে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে।
নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণ: বাংলাদেশে অবহেলিত এক সহিংসতার সংকট
.jpg)
ড. রাসেল হোসাইন ও ড. আনিসুর রহমান খান
শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের ঘটনা একটি গভীর উদ্বেগজনক সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ঘটনাগুলো সাধারণত পারিবারিক পরিসরে সংঘটিত হলেও এর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধ্বংসাত্মক। সাম্প্রতিক সময়ে জার্নাল অফ সাইকোসেক্সুয়াল হেলথ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য উদ্যোগ, আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতার একটি চরম ও নজরদারিহীন রূপকে সামনে এনেছে।
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে দেশে পুরুষের যৌনাঙ্গ বিচ্ছেদের ৪৩টি ঘটনা ঘটেছে এবং সব ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ছিলেন নারী। সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ৭০ শতাংশ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ওপর সহিংসতা চালিয়েছেন তাঁদের স্ত্রী। বাকি ঘটনাগুলোতে অপরাধী ছিলেন নিকটাত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে থাকা সঙ্গী যেমন বান্ধবী, অথবা সাবেক স্ত্রী। এই সহিংসতার প্রধান কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে পরকীয়া, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, যা মোট ঘটনার ৬৭.৪ শতাংশ। পাশাপাশি পারিবারিক ঝগড়া, প্রত্যাখ্যান, প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষার দাবি থেকেও এমন সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের চেষ্টার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এ ধরনের আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে চলমান তীব্র উত্তেজনা ও ভাঙনের ইঙ্গিত বহন করে।
ভুক্তভোগীদের সামাজিক প্রোফাইলও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ ভুক্তভোগীর বয়স ছিল ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। তাঁদের প্রায় ৭৪.৪ শতাংশ বিবাহিত এবং বেশিরভাগই নিম্ন আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আসা শ্রমিক, পোশাকশ্রমিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতের উপার্জনকারী। আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর আঘাত হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও ৫৮ শতাংশ ঘটনায় কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর পেছনে সামাজিক কলঙ্কের ভয়, পারিবারিক চাপ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যেহেতু বৈবাহিক সঙ্গী এই বাস্তবতা বড় ভূমিকা রেখেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ৬৩.৬ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়, যেখানে আইনি সহায়তা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত সীমিত। প্রায় ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ভুক্তভোগীদের আজীবন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি বহন করতে হয়েছে। অন্তত দুটি ঘটনায় মৃত্যুর তথ্যও পাওয়া গেছে।
এই গবেষণার ফলাফল একটি প্রায় অদৃশ্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরনকে উন্মোচিত করে, যা অবিলম্বে আইনি, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যগত মনোযোগ দাবি করে। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা মনে করি, এই সহিংসতা বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো ও লিঙ্গগত সম্পর্কের গভীর কাঠামোগত সংকটের প্রতিফলন। অর্থনৈতিক চাপ, অপূর্ণ বৈবাহিক প্রত্যাশা, বহুবিবাহ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ঘাটতি দাম্পত্য উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সামনে আসে, সহিংসতার আলোচনায় পুরুষ কোথায়।
বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের কথা শুনলে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন, কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও চান না। পরিসংখ্যানের বিচারে ঘটনাগুলো সংখ্যায় কম মনে হতে পারে, কিন্তু এর সামাজিক বার্তা ভয়াবহ। দাম্পত্য সম্পর্কে অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও টানাপোড়েন মিলিয়ে এক নীরব সংকট তৈরি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পুরুষ ভুক্তভোগীরা লজ্জা ও সামাজিক প্রত্যাশার চাপে মুখ খুলতে পারেন না। আমাদের সমাজে পুরুষ মানেই শক্ত, ব্যথা বা লজ্জা নেই, এই ধারণা তাঁদের নীরব করে রাখে। এর ফল হিসেবে গুরুতর অপরাধও আইনের আওতার বাইরে থেকে যায়। এই নীরবতার মূল্য দিতে হয় পরিবারকে, সন্তানকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।
এই বাস্তবতায় বাংলাদেশকে জেন্ডার-নিউট্রাল গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, দাম্পত্য কাউন্সেলিং এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণকে জাতীয় অগ্রাধিকারে আনতে হবে। দাম্পত্য সহিংসতা নারী বা পুরুষ কাউকেই ছাড়ে না। তাই সমস্যাটি স্বীকার করাই সমাধানের প্রথম ধাপ। সহিংসতা লুকিয়ে নয়, বরং তা স্বীকার করে, বোঝে এবং প্রতিরোধ করেই সমাজকে মানবিক করা সম্ভব।
আমাদের দৃষ্টিতে, এই ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় বহুস্তরের সরকারি প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। প্রথমত, আইনি ও বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। যৌনাঙ্গের ক্ষতির প্রতিটি ঘটনায় বাধ্যতামূলক তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার মামলার জন্য দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পারিবারিক সহিংসতা আইন সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেয়।
দ্বিতীয়ত, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা জোরদার করা জরুরি। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে বৈবাহিক সহিংসতার শিকার পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সংকটকালীন পরামর্শ বিভাগ চালু করতে হবে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের উচ্চঝুঁকিপূর্ণ দাম্পত্য দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পারিবারিক ও বিবাহ পরামর্শ সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
তৃতীয়ত, সামাজিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রটি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এনজিও ও স্থানীয় সরকার যৌথভাবে বিয়ের আগে ও পরে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি চালু করতে পারে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সহিংসতার শিকার পুরুষদের প্রতি সামাজিক কলঙ্ক মোকাবেলার প্রচারণা এবং বহুবিবাহ-সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উপযুক্ত আইনি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
চতুর্থত, দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কভারেজ নিশ্চিত করা জরুরি। যৌনাঙ্গে আঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগীদের লজ্জা ও মানসিক ক্ষতি কমে। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা ও চাঞ্চল্যকর উপস্থাপন পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন অনেক সময় ভুক্তভোগীদের মামলা চালাতে নিরুৎসাহিত করে।
সবশেষে, লিঙ্গ শিক্ষা ও দ্বন্দ্ব সমাধান বিষয়ে জোর দিতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, সম্মতি শিক্ষা এবং সুস্থ সম্পর্ক গঠনের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।
লক্ষণীয় যে, পুরুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গকে লক্ষ্য করে সংঘটিত সহিংসতা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার কারণে প্রায় আলোচনার বাইরে থাকে। এখানে প্রতিযোগিতামূলক অভিযোগ নয়, বরং সকল ধরনের আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলায় সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু পুরুষের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রটি প্রায় উপেক্ষিত। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে পুরুষ ভুক্তভোগীরা নীরবে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে এবং ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার গভীর কারণগুলো যেমন লিঙ্গ বৈষম্য, দুর্বল আইনি সহায়তা এবং তীব্র বৈবাহিক চাপ অমীমাংসিতই থেকে যাবে।
লেখক-
ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ড. আনিসুর রহমান খান, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
জুলাই আন্দোলনে ভাইরাল হওয়া এক শ্রমজীবীর আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন: সুযোগের দরজা নাকি নতুন শঙ্কা?

মো:রাকিবুল ইসলাম
সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই আন্দোলনের সময় ভাইরাল হওয়া এক রিকশাচালককে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ঘটনাটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, শ্রেণি-বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কাঠামো নিয়ে এক নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে এটি গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির এক চমৎকার উদাহরণ বলে মনে হতে পারে, যেখানে একজন প্রান্তিক মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এই প্রতীকী অন্তর্ভুক্তি কেবল সুযোগ নয়, বরং নতুন ধরনের সামাজিক ও নৈতিক শঙ্কাও তৈরি করে।
বাংলাদেশের রাজনীতি ঐতিহাসিকভাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এলিট শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে ছিল। শ্রমজীবী মানুষ বা নিম্ন আয়ের শ্রেণি সাধারণত রাজনীতির ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, নেতৃত্বের জায়গায় তারা প্রায় অনুপস্থিত। এই প্রেক্ষাপটে একজন রিকশাচালকের মনোনয়ন নিঃসন্দেহে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাইরে এক নতুন বার্তা বহন করে। এটি দেখায় যে, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রটি এখন কেবল অর্থবান ও প্রভাবশালীদের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের প্রতিও কিছুটা উন্মুক্ত হচ্ছে।
তবে, বাস্তবতা আরও জটিল। একজন শ্রমজীবী মানুষ, যার দৈনন্দিন জীবন নির্ভর করে অল্প আয়ের ওপর, হঠাৎ করে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে চলে গেলে তার জীবনে যে চাপ তৈরি হয় তা কল্পনা করা কঠিন নয়। রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সামাজিক প্রত্যাশা এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন মিলিয়ে সে এমন এক অচেনা বাস্তবতায় পড়ে যায়, যেখানে তার পুরনো জীবনের স্থিতি ভেঙে যায়। ফলে, যে মানুষটি সমাজের প্রতিনিধি হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রতীক বা প্রচারণার উপকরণ।
এই প্রতীকীকরণ প্রক্রিয়াই আসলে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে। কিন্তু যখন তাদের কেবল ভোট বা প্রচারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি হয়ে দাঁড়ায় একধরনের প্রতারণা। এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক মানুষ রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার হাতে থাকে না। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক চাপ, এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকি তার জীবনে নতুন অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
অন্যদিকে, গণতন্ত্রের মূল দর্শনই হলো অংশগ্রহণের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা। তাই একজন দরিদ্র মানুষ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছে, এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক অগ্রগতি। কিন্তু এই সুযোগ তখনই বাস্তব ক্ষমতায় রূপ নেবে, যখন তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তা এবং সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সত্যিই প্রান্তিক শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তবে তাদের কেবল মনোনয়ন নয়, বরং ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
এই ঘটনাটি আমাদের সামনে আরও বড় প্রশ্ন তোলে: বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা কি সত্যিই গণতান্ত্রিক হচ্ছে, নাকি কেবল তার প্রতিচ্ছবি তৈরি করা হচ্ছে? একজন শ্রমজীবীর মনোনয়ন গণতন্ত্রের মুখে মানবিক রঙ যোগ করলেও, যদি তার বাস্তব ক্ষমতা, সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত না হয়, তবে এটি কেবল রাজনৈতিক প্রতারণার আরেক রূপ।
একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্র মানুষ শুধু ভোটার নয়, নীতিনির্ধারকও হয়। কিন্তু সেই বাস্তবতা তৈরি করতে হলে দরকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন, যেখানে আর্থিক সক্ষমতা নয়, যোগ্যতা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা হবে নেতৃত্বের মানদণ্ড।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে, যদি তা প্রকৃত সহায়তা ও নৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অন্যথায় এই অন্তর্ভুক্তি হয়ে উঠবে সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রতীক, যার অন্তর্গত বাস্তবতা আরও নির্মম।
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চাই, নাকি কেবল তার প্রতীকী উপস্থাপনেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই?
কাদিয়ানী ইস্যু ও পাকিস্তানি সংযোগ: বাংলাদেশের ধর্মীয় রাজনীতিতে বিপজ্জনক অস্থিরতার ইঙ্গিত

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
বাংলাদেশে আহমদিয়া কমিউনিটি সংখ্যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আনুমানিক এক লাখ সদস্যের এই গোষ্ঠী দেশব্যাপী সামাজিক পরিসরে এতটাই অদৃশ্য যে অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে তাদের কাউকে পাওয়া যায় না। ফলে যে সমাজে তাদের অস্তিত্বই প্রায় অদৃশ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন শুরু হওয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের জন্ম দেয়। কেন এই ইস্যুটি স্থানীয় বাস্তবতা ছাড়াই এমনভাবে সামনে আনা হলো এবং কারা এর পিছনে সংগঠিতভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৫ নভেম্বর যে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে, তা আয়োজন করছে সম্মিলিত খতমে নবুওয়ত পরিষদ নামে একটি সংগঠন। কওমি ধারার আলেমদের একটি অংশ, হেফাজতপন্থী গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিকভাবে উগ্রপন্থি মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত কিছু ব্যক্তিরা এই আয়োজনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তারা অনলাইন এবং অফলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাচ্ছে এবং দাবি তুলছে যে বাংলাদেশে কাদিয়ানি বা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি, সামাজিক সহাবস্থান এবং ঐতিহ্যের আলোকে এই দাবির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং এটি একটি সংগঠিত রাজনৈতিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়।
এরই মধ্যে ১২ নভেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে ইন্তিফাদা বাংলাদেশ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের ভিডিও ও ছবি সমাজমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বৈঠকের আয়োজক ও বক্তাদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত আল কায়েদা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের কাউকে দেখা গেছে ৫ আগস্টের পর থানায় অবরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি এবং প্রথম আলো অফিস ঘেরাওয়ের মতো ঘটনাগুলোতেও। এছাড়া আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নেতা জসীমউদ্দিন রহমানীর সঙ্গেও এই গোষ্ঠীর যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। এই উপস্থাপনাগুলো দেখায় যে দেশের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থি নেটওয়ার্ক পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে এবং তারা কাদিয়ানী ইস্যুকে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।
এই সম্মেলনে অংশ নিতে পাকিস্তান, ভারত এবং নেপাল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামা বাংলাদেশে এসেছেন। সবচেয়ে আলোচিত নাম হলো পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সংগঠনের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মাওলানা ফজলুর রহমান, যিনি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন মহাসচিব মাওলানা আবদুল গফুর হায়দারি, মাওলানা আসাদ মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা। এছাড়াও রয়েছেন রাওয়ালপিন্ডি, করাচি ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন মাদ্রাসার উচ্চপদস্থ শিক্ষক ও বক্তারা। এই ব্যক্তিদের অনেকের বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও মার্কিন ডিপ স্টেটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ইমরান খানের পতনের সময়ও ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের বক্তা মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের জন্য কুখ্যাত।
প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণের এমন সংবেদনশীল মুহূর্তে এইসব বিতর্কিত ব্যক্তিরা কেন একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণায় অংশ নিতে এসেছেন। তাদের এই আগমন মোটেই নিরীহ বা সাধারণ কোনো ধর্মীয় সফর নয়। বরং এটি ইঙ্গিত দেয় যে দেশে অস্থিরতা তৈরিতে ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহার করা হতে পারে এবং এর পেছনে আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থ সক্রিয় থাকতে পারে।
পাকিস্তানের ইতিহাস এই বিষয়ে এক ভয়াবহ শিক্ষা দেয়। দেশটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আহমদিয়া ইস্যু সেখানে বারবার রাজনৈতিক সংকট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের লাহোর দাঙ্গা ছিল আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আকারের সহিংসতা, যা Munir Commission Report-এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এটি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না, বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। এরপর ১৯৭৪ সালে আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করা এবং ১৯৮৪ সালে Ordinance XX জারি করা হয়। প্রতিটি ঘটনা ছিল সামরিক বা আধা-সামরিক শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কৌশল।
মুফতি মাহমুদ, যিনি মাওলানা ফজলুর রহমানের পিতা, ভুট্টো সরকারের বিরুদ্ধে কাদিয়ানী ইস্যুকে ব্যবহার করেছিলেন এবং পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিলেন। আজ তাঁর পুত্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময়ে একই ধরনের ইস্যু নিয়ে ঢাকা সফর করছেন। এটি নিছক ধর্মীয় সফর নয়, বরং পাকিস্তানের অতীত অভিজ্ঞতার ভৌতিক পুনরাবৃত্তি।
বাংলাদেশেও এ কৌশল নতুন নয়। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর যখন গণতান্ত্রিক পথচলা শুরু হয় এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়, তখনই ১৯৯১ সালে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়। খুলনা, রাজশাহীসহ নানা স্থানে হামলা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে নবীন সরকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাপের মুখে পড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এইবারও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে সরকার শুরুতে এই সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। তাদের মনোযোগ এখন নির্বাচন নিয়ে বেশি, এবং হয়তো সমাবেশের ভূরাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। কিন্তু এখন যেহেতু বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, সরকারের দায়িত্ব হলো বিদেশি উগ্র মতাদর্শধারী ব্যক্তিদের যেকোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা। এমন আন্দোলন ও বিদেশি উলামাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য গভীর নিরাপত্তা সংকট তৈরি করতে পারে।
বাংলাদেশ একটি বহুধর্মীয়, সহনশীল এবং মানবিক সমাজ। এখানে ধর্মীয় সহাবস্থান ঐতিহাসিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। অথচ এখন সেই পরিবেশে বিদেশি প্রভাব ও উগ্র মতাদর্শ প্রবেশ করে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। কাদিয়ানী ইস্যু বাংলাদেশের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আলোচ্য বিষয় নয়। এটি মূলত আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার একটি কৃত্রিম কৌশল। বাংলাদেশের উচিত এখনই সচেতন হওয়া, কারণ ধর্মকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পরিণাম কখনোই শুভ হয় না। পাকিস্তানের ইতিহাসই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাংলাদেশ সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। এখন রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের উচিত সম্মিলিতভাবে এই ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়া।
ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা পুনরুদ্ধার করতে হবে

মো: রাকিবুল ইসলাম
সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রের ধারণাটি একসময় কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতা, আইনের শাসন এবং নিরাপত্তা প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা এখন বহুমাত্রিক এবং জটিল। রাষ্ট্র কেবল শাসনের প্রতীক নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক সত্তা, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। অথচ আজ আমরা এমন এক সময় পার করছি, যখন রাষ্ট্রের এই নৈতিক দায়বদ্ধতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ক্রমশ বাজারের যুক্তি ও পুঁজির অগ্রাধিকারের সঙ্গে অদ্ভুত এক সমঝোতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে রাষ্ট্রের পরিমণ্ডল নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেছে। এখন রাষ্ট্রের সফলতা মাপা হয় জিডিপি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, অবকাঠামোগত প্রকল্প বা বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে। কিন্তু এই তথাকথিত উন্নয়ন সূচকগুলো প্রায়ই মানবিক উন্নয়ন বা সামাজিক ন্যায়বিচারের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায় না। যখন একজন নাগরিক মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা নিরাপদ জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুক্তিতে রাষ্ট্র এখন প্রায়শই কর্পোরেট স্বার্থে বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ নাগরিকের চাহিদায় তুলনামূলকভাবে উদাসীন। এর ফলেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়-বৈষম্য বেড়েছে, সামাজিক শ্রেণি বিভাজন গভীর হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না, কৃষক উৎপাদনের দাম না পেয়ে ঋণের জালে জড়ায়, শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সেবার বাইরে থেকে যায়।
এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি নৈতিক বৈষম্যেরও প্রতিফলন। রাষ্ট্র যখন বাজারের যুক্তিকে মানবিক দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়, তখন নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো এক ধরনের নৈতিক সংকটে পড়ে যায়, যেখানে উন্নয়নের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় কেবল ধনীদের আরও ধনী হয়ে ওঠা এবং দরিদ্রদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।
রাষ্ট্রকে কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। রাষ্ট্র হলো এমন এক প্রতিষ্ঠান যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত মানুষ, তার জীবন, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের অধিকার। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূল দর্শনই হলো জনকল্যাণ। একটি মানবিক রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগ করে না, বরং এটি নাগরিকদের জন্য আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং সম্মানের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে বলা যায় একটি নৈতিক সম্প্রদায়, যা সমাজের দুর্বলতম ও প্রান্তিক শ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধ। কারণ একটি সমাজের সভ্যতা বিচার করা হয় তার সবচেয়ে দুর্বল মানুষটির প্রতি আচরণের মাধ্যমে।
রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্জাগরণ মানে হলো রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবিকতার চেতনায় পুনর্গঠন করা। যেখানে উন্নয়নের মানে হবে না কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং সমতার বিকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই আজকের রাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে মানবিকতার শূন্যতায় ঠেলে দিচ্ছে।
একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। উন্নয়ন ও কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কিছু মৌলিক দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা ও বিস্তৃতি বাড়াতে হবে। দরিদ্র, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদের জন্য কার্যকর নিরাপত্তা নেট তৈরি করা দরকার। এগুলোকে রাজনৈতিক প্রদর্শন নয়, বরং বাস্তব কল্যাণে রূপ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিকতা ও ন্যায়বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হলো মানবিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। শিক্ষা কেবল চাকরির উপকরণ নয়, এটি মূল্যবোধ, যুক্তি, সহানুভূতি ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। তাই রাষ্ট্রের উচিত গবেষণা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক চিন্তার বিকাশে বিনিয়োগ বাড়ানো, যাতে নাগরিকরা শুধু দক্ষ নয়, সচেতনও হয়।
তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যসেবাকে নাগরিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি মানবিক রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা কখনোই বাণিজ্যিক পণ্য হতে পারে না। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, প্রান্তিক অঞ্চলে চিকিৎসক নিয়োগ ও ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। চতুর্থত, শ্রমজীবী মানুষের জন্য ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ, যখন তা শ্রমিকের ঘামে নয়, মর্যাদায় দাঁড়িয়ে থাকে।
পঞ্চমত, রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। স্থানীয় সরকার, নাগরিক ফোরাম, যুবসংগঠন ও সিভিল সোসাইটির সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে নীতি প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে। এতে জনগণ নিজেদের রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে অনুভব করবে। ষষ্ঠত, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র মানে কেবল মানুষের ন্যায় নয়, প্রকৃতির প্রতিও দায়িত্বশীলতা।
মানবিক রাষ্ট্র কোনো আদর্শিক কল্পনা নয়, এটি টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি রাষ্ট্র তখনই স্থিতিশীল ও উন্নত হয়, যখন তার নাগরিকরা বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন রাষ্ট্রের কাছে মূল্যবান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ, যখন তা সামাজিক সমতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন হয়ে ওঠে অন্যায় প্রবৃদ্ধি, যা কেবল কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে।
যখন রাষ্ট্র তার নৈতিক দায়বদ্ধতা হারায়, তখন নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হয়ে যায় লেনদেনমূলক, আস্থাভিত্তিক নয়। মানুষ তখন রাষ্ট্রকে নিজের বলে অনুভব করে না। এই বিচ্ছিন্নতাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অসন্তোষ ও সহিংসতার জন্ম দেয়। তাই রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্জাগরণ প্রয়োজন তিনটি স্তরে। প্রথমত, নীতিগত স্তরে মানবিকতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়কে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় জবাবদিহিতা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক স্তরে সমাজে সহানুভূতি, দানশীলতা ও সামাজিক সংহতির চর্চা বাড়াতে হবে এবং গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।
ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। রাষ্ট্র যদি তার নৈতিক দায়িত্ব ভুলে যায়, তবে তার উন্নয়ন অবশেষে হয়ে উঠবে এক নির্মম শোষণের প্রক্রিয়া। তাই এখন সময় রাষ্ট্রের আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির। রাষ্ট্রকে ফিরতে হবে সেই মৌলিক দর্শনে, যেখানে নাগরিকই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু, আর শাসকগোষ্ঠী কেবল সেই উন্নয়নের তত্ত্বাবধায়ক।
একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হয়, যখন তার প্রতিটি নাগরিক বিশ্বাস করতে পারে যে এই রাষ্ট্র আমার, এই সমাজ আমার, এবং এখানে আমার জীবনের মর্যাদা আছে। ন্যায়, সমতা এবং মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই পারে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্রের এই নৈতিক পুনর্জাগরণই হতে পারে আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও নৈতিক বিজয়, একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের জন্য।
গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা: বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এক নতুন দিগন্ত

মো. রাকিবুল ইসলাম
সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠদান, দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। অথচ আজকের পৃথিবী জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবননির্ভর সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। তাই সময় এসেছে আমাদের উচ্চশিক্ষার কাঠামো ও দর্শনকে পুনর্বিন্যাস করার, যেখানে গবেষণা হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।
বিশ্বের ইতিহাসে যেকোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে গবেষণার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নতুন প্রযুক্তির বিকাশ, কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে উদ্ভাবন, কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সংস্কার—সব ক্ষেত্রেই গবেষণা জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণা শুধু তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া নয়, এটি এক গভীর চিন্তা, অনুসন্ধান ও সৃষ্টিশীলতার যাত্রা। তাই একটি জাতিকে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানসমৃদ্ধ করতে হলে গবেষণাকে শিক্ষার ভিত্তিতে পরিণত করা ছাড়া বিকল্প নেই।
বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জাতির চিন্তা, মেধা ও নেতৃত্ব গঠনের কারখানা। এখানেই গড়ে ওঠে নতুন ভাবনা, প্রশ্ন ও অনুসন্ধান। উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা পাঠদানের পাশাপাশি গবেষণাকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছে। হার্ভার্ড, এমআইটি, কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ যেভাবে বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার মূল কারণ হলো তাদের গবেষণানির্ভর শিক্ষা ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি।
সেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু ক্লাসরুমের পাঠে সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা গবেষণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। কেউ গবেষণা সহকারী হিসেবে (Research Assistant) কাজ করে, কেউ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানে সহায়তা করে (Teaching Assistant)। এতে তারা একদিকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে, অন্যদিকে আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণক্ষমতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা গড়ে তোলে।
দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো গবেষণানির্ভর সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা গবেষণায় সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় না। শিক্ষাদানের সহকারী হিসেবেও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। ফলে তারা কেবল ডিগ্রি অর্জন করলেও বাস্তব দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং সৃজনশীল চিন্তায় পিছিয়ে থাকে। এই ঘাটতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে।
এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উচ্চশিক্ষায় কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের রিসার্চ ও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আলাদা বাজেট, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত মূল্যায়ন। শুরুতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এটি চালু করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সফল হলে তা ধাপে ধাপে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত করা সম্ভব।
আজকের শিক্ষার্থীকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাকে হতে হবে অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী। গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা সেই পথই তৈরি করতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থী কেবল তথ্যের ভান্ডার নয়, বরং নতুন জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।
আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা শুধু সনদপ্রাপ্ত কর্মী তৈরি করবে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারবে এমন চিন্তাশীল নাগরিক তৈরি করবে। কারণ গবেষণানির্ভর শিক্ষাই একমাত্র পথ, যা বাংলাদেশকে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে।
সংষ্কারের নামে বিরাজনীতিকরণ: বিএনপির বাস্তববাদী অবস্থান ও এন্টি পলিটিক্সের ফাঁদ

ড. বাতেন মোহাম্মদ
শিক্ষক ও রাজনৈতিক গবেষক
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংষ্কার প্রসঙ্গটি এখন এক ধরনের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিএনপির অবস্থান নিয়ে আমার ব্যক্তিগত দ্বিমত থাকলেও, পুরো প্রক্রিয়ায় দলটি অন্তত সৎ থাকার চেষ্টা করেছে—এ কথাটি অস্বীকার করার উপায় নেই। বিএনপি সে মাত্রায়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে, যতটা তার মতো একটি বুর্জোয়া ড্রিভেন ও পার্টি ক্যাপিটালিস্ট দলের পক্ষে বাস্তবিকভাবে সম্ভব। বিএনপি কখনোই আদর্শবাদী দল নয়, বরং এটি বাস্তববাদী দল, যে দল রাজনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
চাইলেই বিএনপি সব সংষ্কার প্রস্তাবে “হ্যাঁ” বলে ক্ষমতায় গিয়ে নিজের সুবিধামতো যা পারত বাস্তবায়ন করত, আর যা পারত না সেটাকে নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যার ভেতর লুকিয়ে রাখত। অর্থাৎ সুযোগ ছিল সহজ পথে হেঁটে লোকদেখানো সংস্কারে অংশ নেওয়ার। কিন্তু দলটি সেই ইজি রাউট নেয়নি। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি মূলত “ইন্সট্রুমেন্টাল র্যাশনাল” অর্থাৎ যে যুক্তিবোধ ক্ষমতার ব্যবহার ও রিসোর্স একুমুলেশনকেই কেন্দ্রে রাখে।
বাংলাদেশের মতো ইনফরমাল অর্থনীতিনির্ভর রাষ্ট্রে এমন দলের কাঠামোতে র্যাডিকাল বা গভীর সংস্কারে রাজি হওয়া শুধু কঠিনই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। তবু বিএনপি তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি এগিয়েছে। একটা বিশাল দল, যার এখনো দলীয় পরিচালনার জন্য সংগঠিত কোনো অর্থনৈতিক কাঠামো নেই, সেই দলের কাছ থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আশা করাটা অবাস্তব। তার ওপর দেশের ভঙ্গুর প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকরণ নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র বা পকেট তৈরি করতে পারে, এটাও এক বাস্তব ঝুঁকি।
এই ঝুঁকি জেনেও বিএনপি সংষ্কারে যতটুকু রাজি হয়েছে, সেটিকে যদি কেবল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনের প্রত্যাশার ভিত্তিতে বিচার না করে, বরং এক গড়পড়তা শিক্ষিত, নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত চাকরিজীবী বা দলীয় কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে বিএনপি আসলে নিজের সামর্থ্যের চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়েছে। তবু যারা সংষ্কারভীতি ছড়িয়ে দলটিকে দুর্বল করতে চাইছে, তাদের আচরণ শেষ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ারই ক্ষতি করছে।
বিএনপি ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল, এটা নতুন কিছু নয়। তবে এই সংষ্কার আলোচনায় তার ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা অন্য যেকোনো দলের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। সাধারণত যার পাওয়ার এসেন্ডিং প্রোবাবিলিটি বেশি, সে নিজের শর্তে দরকষাকষি করে, আর যাদের সম্ভাবনা কম তারা দরকষাকষি করে যতটা আদায় করা যায় সেই যুক্তিতে। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেও বিএনপি সংষ্কারের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়েছে, এটিই তার বড় রাজনৈতিক পরিণতিবোধের পরিচায়ক।
অবশ্যই আমাদের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি আরও উদার হবে। কিন্তু যতটুকু উদার হয়েছে, সেটিও স্বীকার করতে হবে। বিএনপি যদি সত্যিই রিজিড হতো, তবে সংষ্কার প্রক্রিয়া এত দূর অগ্রসর হতো না। এই প্রেক্ষিতে দলটির “নোট অব ডিসেন্ট” বা ভিন্নমত প্রকাশের বিষয়টি যদি রাজনৈতিক অহংকার হিসেবে দেখা হয় এবং সেই সুযোগটিও না দেওয়া হয়, তবে সেটি হবে একপ্রকার এন্টি পলিটিক্স ট্রিক, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই অকার্যকর করে ফেলা হয়। কারণ নির্বাচনী রাজনীতিতে ইগো ও রেটরিক অনেক সময় রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
আজকের সংষ্কার প্রক্রিয়া যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে রাজনীতি বলা যাচ্ছে না। এটা এখন হয়ে উঠছে এক ধরনের বিরাজনীতিকরণ বা এন্টি পলিটিক্স। বিএনপির মতো একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যদি নিজেও এই ধরনের এন্টি পলিটিকাল টুল প্রয়োগ শুরু করে, তাহলে যতটুকু সংষ্কার অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক ততটাই পেছনে চলে যাবে। এর লাভ কারো হবে না, বরং দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতন্ত্রেরই ক্ষতি হবে শেষ পর্যন্ত।
এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে, আমরা আসলে রাজনীতি করছি, নাকি রাজনীতিকে ধ্বংস করছি? যে সংষ্কার কার্যক্রমকে এতদিন রাজনৈতিক পুনর্গঠন বলে গলা ফাটানো হলো, সেটাই কি শেষ পর্যন্ত এক এন্টি পলিটিক্স মেশিন হয়ে উঠছে না? সমাজবিজ্ঞানী জেমস ফার্গুসনের ভাষায়, যে প্রক্রিয়া রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক করার কথা ছিল, সেটিই যখন রাজনীতিকেই নির্বিষ ও অচল করে তোলে, তখন সেটি আর সংষ্কার নয়, এক ধরনের নীরব বিরাজনীতিকরণ।
এটাই আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংষ্কারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। সংষ্কারের নামে রাজনীতির মৃত্যু, আর রাজনীতির নামে সংষ্কারের অনন্তঅপূর্ণতা।
লেখক: ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোসিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।
বিএনপি ও সংস্কারের রাজনীতি: ম্যান্ডেট, কূটচাল ও টেকসই বৈধতার পরীক্ষায় বাংলাদেশ

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
বিএনপির অনেক নেতা–কর্মী মনে করছেন জামাত, সরকার ও এনসিপি মিলে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তিন ধরনের দল আছে, A, B ও C। A বড় দল, এই গ্রুপে আছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। B মাঝারি দল, এই গ্রুপে আছে জামাত ও জাতীয় পার্টি। C হলো বাকি দল—যেমন এনসিপি, এবি পার্টি, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ও অন্যান্য বামপন্থি দল। সাম্প্রতিক সময়ে যে সার্ভেগুলো হয়েছে তাতে যদিও দেখা যাচ্ছে জামাতের অবস্থান আওয়ামী লীগের থেকে ভালো, তবু আওয়ামী লীগ যদি ভয়হীন পরিবেশে নিজের মতামত দিতে পারে, নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থান জামাতের থেকে বেশি হবে। যাই হোক, সেই বিতর্কে না যাই। এই শক্তির মাত্রা মাথায় রেখেই বিএনপি গুড ফেইথে রাজনৈতিক ঐকমতের আলোচনায় অংশ নিয়েছে, অন্তত বিএনপি তাই মনে করে বলে আমার মনে হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি, জুলাই সনদ ও ঘোষণা নিয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এক ধরনের ঐকমতে এসেছে, যদিও এনসিপি তার বাইরে থেকেছে।
বাস্তবতা হলো, দেড় বছর ধরে সরকারের এই পরীক্ষামূলক সংস্কারে বিএনপি অংশ নিয়েছে মূলত গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরার আশায়। ঠিক এই প্রত্যাশাকেই বিএনপির দুর্বলতা ভেবে জামাত, এনসিপি ও নব্য এলিটরা দরকষাকষি করেছে, বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে আলাপে এমন ধারণাই পাওয়া যায়। কিন্তু এই দরকষাকষির সীমানা কোথায়? সীমানা ছিল, নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র না করা, নির্বাচন না পেছানো এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজন না করা। বিএনপি বারবার বলেছে, সংবিধান সংস্কার হবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে। যে কোনো সভ্য দেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সংসদের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার করেন। অনির্বাচিত কোনো সরকার, তা যেভাবেই আসুক, এই অধিকার রাখে না। জোর করে করা যায়, কিন্তু জোর কেটে গেলে সেই সংস্কার টেকে না, তা যতই মহৎ হোক। জনগণের ম্যান্ডেট অপরিহার্য, আর সেই ম্যান্ডেট পাওয়ার পথ হলো নির্বাচন।এখন যে সব সংস্কার প্রস্তাব উঠছে, সেগুলোর প্রতিটিতে হ্যাঁ–না ভোটে জনমত নেওয়া একদিকে কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ। প্রশ্ন কীভাবে ফ্রেম হবে, তথ্য কে দেবে, প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ থাকবে, সবকিছুই বিতর্কিত হতে পারে। এমন অবস্থায়, যেখানে আওয়ামী লীগ–সমর্থক ভোটাররা এই সংস্কারে তেমন সমর্থন দেবেন না, সেখানে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল বাকিদের সমর্থন নিশ্চিত করা, খানিকটা ছাড় দিয়ে হলেও যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যান্ডেট দাঁড়ায়। নিঃসন্দেহে জামাত, বিএনপি, এনসিপি ও বামপন্থি দলগুলো মিলে এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হতে পারত, যা এই ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তনকে জনগণের ম্যান্ডেটের বৈধতা দিত। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে সংস্কার কমিশন যে পথে হাঁটলেন, তা রাজনৈতিক ভুল বলেই মনে হতে পারে। এর ফলে হয়তো তারা বিএনপির সমর্থন হারানোর পথে।
আরও স্পষ্ট করে বলি, বাংলাদেশের বৈধতার কেন্দ্র A গ্রুপে। B–C গ্রুপ চাপ দিতে পারে, কিন্তু টেকসই বৈধতা বানাতে পারে না। তাই বিএনপি যদি সনদ থেকে সমর্থন ফিরিয়ে নেয়, জামাত–এনসিপি–সরকার মিলে চেষ্টা করলেও গণভোটে “জনগণের রায়” বলে যা দেখাতে চাইবেন, তা বাস্তবে টেকসই বৈধতা তৈরি করবে না। বিএনপি নব্য এলিট ও বিপ্লবীদের কাছে “সংস্কার–বিরোধী” তকমা পেতেই পারে; কিন্তু গণভোটের হার–জিতের ক্ষেত্রে সেই ফ্রেমিং বড় ভূমিকা নাও রাখতে পারে। কারণ, ম্যান্ডেটের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের রাজনীতি, এটি পাশ কাটানো যায় না।
আবার, রাজনৈতিক দল ও সরকারের ভেতরের যে অংশ নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে চায়, তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়া ধরে রাখা সম্ভব নয়। আজকের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কোনো শক্তিই তা রাজনৈতিক দল, আর্মি কিংবা অন্য কেউ, নির্বাচন ছাড়া সরকার গঠন করে টেকসই থাকতে পারবে না। এর শেষ পরিণতি ভয়াবহ। এই জটিল পরিস্থিতিতে সংস্কার কমিশনের উচিত ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখানো, সম্মতি জোগাড় করা, সীমা ঠেলে দেখা নয়। তারা উল্টোটা করেছেন, কতটা বাউন্ডারি পুশ করা যায়, বিএনপিকে কতটা বাঁধা দেওয়া যায়, এটাই যেন পরীক্ষা, অন্তত বিএনপির নেতা কর্মীরা তাই মনে করছেন।
প্রশ্ন এখন স্পষ্ট, এই রাজনৈতিক খেলায় বিএনপি কি পারবে নিজের অবস্থান শক্তভাবে জানাতে, না কি আরও ক্ষতির শিকার হবে? বিএনপি যদি আরও ছাড় দিতে থাকে, তৃণমূল এটাকে ভালোভাবে নেবে না; বরং একে দুর্বলতা হিসেবে পড়বে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও বিএনপির দুর্বলতা নিয়ে মজা নেবে। রাজনীতিতে ইমেজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিএনপির দায়িত্ব, রেডলাইন স্পষ্ট করা: নির্বাচন পেছানো যাবে না; সংবিধান–সংস্কার নির্বাচিত সংসদের ম্যান্ডেটে হবে। ইস্যুর ক্রম ঠিক করা: আগে নির্বাচন, তারপর সংসদীয় প্রক্রিয়ায় সংস্কার; প্রয়োজনে সীমিত, নির্দিষ্ট ধারায় গণভোট। এবং জোটের অঙ্ক কংক্রিট করা: বিচারব্যবস্থা, ইসি–রিফর্ম, মৌলিক অধিকার, ৩–৫টি কমন–মিনিমাম বিষয়ে সমঝোতা, বাকিগুলো সংসদে।
শেষ কথা, বিএনপি আজ ভেটো প্লেয়ার। বিএনপি আউট থাকলে গণভোটের রাস্তা বৈধতা আনতে পারবে না; বরং অনিশ্চয়তা বাড়াবে। তাই বিএনপির এখন দরকার পরিষ্কার সিগনাল, এক লাইনের বার্তা: আগে ম্যান্ডেট, পরে সংস্কার, কিন্তু আরও ভালোভাবে। নির্বাচন ছাড়া এই সঙ্কটের টেকসই সমাধান নেই; এবং নির্বাচন–পূর্ব যেকোনো শর্টকাট শেষতক নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।
(আমি শুরু থেকেই নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। আমি মনে করি না, নির্বাচনের মাধ্যমে দেয়া জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া কারও সংবিধান সংস্কারের অধিকার আছে। তাই এই লেখায় আমার অবস্থানগত পক্ষপাত থাকতে পারে।)
পাঠকের মতামত:
- নানিয়ারচর সেনা জোন কর্তৃক অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র ও নগদ অর্থ প্রদান
- ঢাকাসহ দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত
- অজানা মহাবিশ্বের সন্ধানে এআই: হাবল আর্কাইভে মিলল শত শত নতুন গ্যালাক্সি
- অজানা মহাবিশ্বের সন্ধানে এআই: হাবল আর্কাইভে মিলল শত শত নতুন গ্যালাক্সি
- বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে শীর্ষে তারেক রহমান: দ্য ইকোনমিস্ট
- অপরাধীরা বাধা দিলেও ভোটাররা কেন্দ্রে যাবেই: সেনাপ্রধান
- প্রতিরক্ষা খাতে বাংলাদেশ-জাপান ঐতিহাসিক চুক্তি
- ক্রিকেট বিশ্ব যখন টালমাটাল, তখন ভারতকে নতুন আঘাত দিল পাকিস্তান
- রাষ্ট্রপতির কার্যালয়কে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিল জামায়াত
- গায়ক নোবেল ও তাঁর মাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
- আমিও আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম: নুর
- বিটিআরসির নতুন বার্তা: পুরোনো মোবাইল ফোন বিক্রির আগে সাবধান!
- শেষ চমক দেখাতে কাল দক্ষিণে তারেক রহমান
- মুক্তিযোদ্ধাকে ‘ভাড়া’ করে সাইনবোর্ড দেখাচ্ছে জামায়াত: সালাহউদ্দিন আহমদ
- পাচারকারীদের পেটের ভেতর থেকে টাকা বের করে আনা হবে: জামায়াত আমির
- অচল চট্টগ্রাম বন্দর: আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ
- স্বর্ণের বাজারে নজিরবিহীন কাণ্ড! ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের বাড়ল দাম
- আজকের শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- আজকের শীর্ষ দরপতনকারী ১০ শেয়ার
- আজকের শীর্ষ দরবৃদ্ধিকারী ১০ শেয়ার
- হঠ্যাৎ কী কারণে বদলে যাচ্ছে র্যাবের নাম
- ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি? যা জানা গেল
- কোন সবজিতে কী পুষ্টি, জানুন বিস্তারিত
- শিক্ষাবৃত্তির আবেদন নিয়ে নতুন ঘোষণা, জানাল বোর্ড
- শবে বরাতের মহিমান্বিত রাতে ক্ষমা ও রহমত কামনায় তারেক রহমানের বার্তা
- আগামী ১৩ তারিখ থেকে বাংলাদেশে পরিবর্তনের সূচনা: জামায়াত আমির
- ফ্রিজে সবজি পচে যাওয়ার বড় কারণগুলো, জানুন সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি
- প্রথম শিকারকে যেভাবে ফাঁদে ফেলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তার প্রেমিকা
- মাদকসম্রাট ও হাসনাত আব্দুল্লাহ একসাথে থাকতে পারে না: দেবিদ্বারে হুঙ্কার
- চট্টগ্রামে বিএনপির নির্বাচনী পালে নতুন হাওয়া: ভোটের মাঠে ফিরলেন দুই হেভিওয়েট
- ভোটের মাঠে টাকার ঝনঝনানি: হলফনামার তথ্যে শীর্ষ ১০ ধনী প্রার্থী কারা?
- রাজধানীসহ ৪৮ স্থানে কম দামে মাংস-দুধ-ডিম বিক্রি
- বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পোশাকের দাপট: জানুয়ারিতে রেকর্ড আয়
- কুখ্যাত জেফ্রি অ্যাপস্টেইন ফাইলে শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেতার নাম
- এপস্টেইন কেলেঙ্কারি: তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে রাজি বিল ও হিলারি ক্লিনটন
- যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য যুদ্ধে ইতি! ট্রাম্পের ঘোষণার পরই চাঙ্গা ভারতের বাজার
- নির্বাচনি ব্যয়ের লাগাম টানার লড়াই: কালো টাকা রুখতে বিএফআইইউ-র কড়াকড়ি
- স্বর্ণের দামে বড় ধস: আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন মূল্য তালিকা
- আজ ঢাকায় যেসব এলাকার মার্কেট ও দোকান বন্ধ
- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- রাজধানীতে আজ কোথায় কী? বের হওয়ার আগে দেখে নিন কর্মসূচির তালিকা
- আজকের নামাজের সময়সূচি: জেনে নিন পাঁচ ওয়াক্তের ওয়াক্ত
- দেশে ফের ভূমিকম্প, কেঁপে ওঠে কয়েকটি জেলা
- শবে বরাতের রোজা ও তওবা-ইস্তিগফারের গুরুত্ব
- আজ পবিত্র শবেবরাত, খুলেছে রহমতের দরজা
- মঙ্গলের বুকে এআই-এর রাজত্ব: প্রথমবারের মতো মানুষের বদলে পথ দেখালো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
- বিশ্বজুড়ে তোলপাড়: এপস্টেইন ফাইলের ৩০ লাখ পৃষ্ঠায় ক্ষমতাধরদের অন্ধকার জগত
- রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের সুফল: শক্তিশালী অবস্থানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ
- নতুন নকশায় ১০ টাকার ব্যাংক নোট: এক নজরে দেখে নিন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
- সদরপুরে পদ্মা নদীর চর থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন: ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
- স্বর্ণের দামে বড় পতন, ট্রাম্পের ঘোষণায় স্বর্ণবাজারে অস্থিরতা
- তারেক রহমানকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন: ‘Bangladesh’s Prodigal Son’
- বিশ্ববাজারে রেকর্ড দরপতন; দেশেও কমল স্বর্ণের দাম
- স্বস্তি ফিরলো স্বর্ণের বাজারে; আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম
- স্বর্ণের দামে বড় ধস: আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন মূল্য তালিকা
- তিন দিনে ভরিতে বাড়ল ২৮ হাজার, স্বর্ণে রেকর্ড
- আজ ৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে একাধিক এলাকা
- রুপার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ, ভরি ছাড়াল যত
- কালিগঞ্জে জমি বিরোধে সংঘবদ্ধ হামলা, চারজন গুরুতর আহত
- একদিনে দুই দফা স্বর্ণের দাম কমাল বাজুস, এক ভরিতে কমল যত
- রেকর্ড ভেঙে ছুটছে স্বর্ণ ও রুপা: নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীরা
- আজ প্রাইজবন্ডের ১২২তম ড্র: জেনে নিন প্রাইজবন্ডের ফলাফল দেখার সহজ নিয়ম
- আগামী পাঁচ দিন কেমন থাকবে দেশের আবহাওয়া
- রিয়েল এস্টেটে বড় স্বস্তি, ফ্ল্যাট ও জমি নিবন্ধনে বিরাট সুখবর
- শবেবরাত পালনে কী করবেন, কী করবেন না











