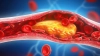একটি বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রবন্ধ
অভিভাবকতন্ত্রের প্রলোভন: জেনারেল ভূঁইয়ার বয়ান ও গণতন্ত্রের ঘড়ি থামানোর বিপদ

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া সম্প্রতি তাঁর ফেসবুক পেজে লিখছেন ধারাবাহিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী পোস্ট, যার শিরোনাম “আগামী পাঁচ বছরে আমরা কোথায় যাচ্ছি?” এর পঞ্চম অংশে তিনি আলোকপাত করেছেন “বিএনপি ক্ষমতায় এলে সম্ভাব্য চিত্র” বিষয়ে। অভিজ্ঞ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে মনোযোগ দাবি করে। তবে তাঁর লেখার রাজনৈতিক ফ্রেমিং ও বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত ধারা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে যখন সেই বয়ানে নির্বাচিত রাজনীতিকদের “সমস্যা” এবং অ-নির্বাচিত এলিট বা উপদেষ্টাদের “সমাধান” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
এই ফ্রেমটি প্রথমেই একটি মৌলিক অস্বস্তি তৈরি করে, কারণ এটি প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে কার্যকারিতাকে একমাত্র গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেন গণতন্ত্রের মূল যুক্তি, অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে ম্যান্ডেট অর্জন, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তার জায়গা নেয় “যোগ্য” অ-নির্বাচিত অভিভাবকদের শাসন। এটি একটি বিপজ্জনক স্লিপারি স্লোপ, যেখানে জনগণের ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে অভিভাবকতন্ত্রকে বৈধতা দেওয়া হয়। ইতিহাস বলছে, একবার যদি এই পথে যাত্রা শুরু হয়, নির্বাচনী রাজনীতির প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়।
জেনারেল ভূঁইয়ার লেখায় একটি স্পষ্ট কৌশল দেখা যায়, সেটি হলো ভয়কে রাজনৈতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা। তিনি ভারতীয় চাপ, অর্থনৈতিক সংকট, পুলিশের অকার্যকারিতা, রাস্তার সহিংসতা ইত্যাদি উদাহরণ টেনে এনে বলেছেন যে এসব কারণেই হয়তো অন্তর্বর্তী সরকারকে সময় বাড়াতে হবে বা “বিশেষ ব্যবস্থা” নিতে হতে পারে। এই ভয়নির্ভর বয়ান জনমনে এমন ধারণা তৈরি করে যে নির্বাচন অনিশ্চিত, ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিলম্বই নিরাপদ পথ। ফলত একটি “ইলেকশন-অপশনাল” মানসিকতা জন্ম নেয়, যেখানে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে ঐচ্ছিক হয়ে ওঠে। এটি গণতন্ত্রের শিকড় ক্ষয়ে দেওয়ার এক নীরব উপায়।
যখন তিনি লেখেন “রিফর্ম আগে, নির্বাচন পরে”, সেটি আসলে এক বিপরীত রাজনৈতিক সিকোয়েন্সের প্রচলন। টেকসই গণতন্ত্রে সংস্কারের বৈধতা আসে নির্বাচনের ম্যান্ডেট থেকে, কিন্তু তিনি উল্টো বলছেন নির্বাচনের আগেই সংস্কার হোক। বাস্তবে এর অর্থ দাঁড়ায় জনগণের ম্যান্ডেটহীন শক্তির হাতে রাজনৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া। “রিফর্ম-ফার্স্ট” চিন্তাধারা অচিরেই “ইলেকশন-লেটার” হয়ে যায়, আর পিছিয়ে দেওয়া ভোট খুব কম ক্ষেত্রেই ফিরে আসে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসই তার প্রমাণ।
আরও উদ্বেগজনক হলো, জেনারেল ভূঁইয়া তাঁর লেখায় নিরাপত্তা কাঠামোকে এক ধরনের “নিরপেক্ষ ম্যানেজার” হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পুলিশকে “অলস ঘোড়া” আখ্যা দিয়ে সেনাকে মাঠে রাখার বিষয়টি তিনি নিছক ম্যানেজমেন্ট ইস্যু হিসেবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেসামরিক জবাবদিহির প্রশ্নকে আড়াল করে এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে ডি-ফ্যাক্টো রাজনৈতিক রেফারিতে রূপান্তরিত করে। গণতন্ত্রে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কখনোই রাজনীতির ভারসাম্যরক্ষাকারী হতে পারে না, কারণ তাতে নির্বাচিত নেতৃত্বের জবাবদিহি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সরে যায় অদৃশ্য ব্যবস্থাপক মহলের হাতে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জেনারেল ভূঁইয়া সম্ভাব্য বিএনপি সরকারের প্রতি আগেভাগেই অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর পূর্বাভাসে দেখা যায়, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দুর্নীতি বাড়বে, ভারতীয় সম্পর্কের অবনতি ঘটবে, রাস্তায় সহিংসতা হবে। এই ধরনের পূর্বাভাস আসলে রাজনৈতিক আগাম অবমূল্যায়ন, যা একটি বিপজ্জনক বার্তা দেয় যে “ভুল দল” জিতলে সেটিকে “ম্যানেজ” করা ন্যায্য। এতে নির্বাচনী গণতন্ত্রের মৌলিক শর্ত, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ ক্ষমতার পালাবদল, শর্তাধীন হয়ে পড়ে।
তাঁর বয়ানে নাগরিকরা নায়ক নয়, বরং “ঝুঁকি”। সমাধান খোঁজা হয় এলিট মহলের ভেতরে, “যোগ্য উপদেষ্টা” বা “সমঝোতার সরকার”-এর মধ্যে। এটি একধরনের ক্লাসিক এলিট সাবস্টিটিউশন, যেখানে জনসম্মতি সরিয়ে পেছনের দরজার চুক্তি সামনে আনা হয়। এতে রাজনৈতিক দল, ভোটার ও নীতির স্বাভাবিক সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়ে; আস্থা কমে, অংশগ্রহণও হ্রাস পায়। ফলত গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় সীমিত থেকে যায়।
আরেকটি বিষয় হলো, তাঁর লেখায় বারবার “বহির্দেশের ভেটো”, বিশেষ করে ভারতের প্রভাব, একটি অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে হাজির হয়। এতে ইঙ্গিত মেলে যে নীতি-প্রসঙ্গগুলোতে বাইরের “রেড লাইন” অতিক্রম করা যায় না। এটি আসলে সার্বভৌম ভোটের অস্বীকৃতি, যেখানে জনমতকে আগে থেকেই সঙ্কুচিত বৃত্তে বন্দি করে ক্ষমতাবান এলিটরা সিদ্ধান্ত নেন কী সম্ভব আর কী নয়।
সব মিলিয়ে, জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়ার লেখার অন্তর্নিহিত বার্তা হলো ভয়নির্ভরতা, “রিফর্ম-ফার্স্ট” সিকোয়েন্স, এলিট ও টেকনোক্র্যাটিক সমাধান, এবং নিরাপত্তা কাঠামোর রাজনৈতিক ভূমিকার স্বাভাবিকীকরণ। এগুলো মিলে এক নতুন প্রকারের অভিভাবকতন্ত্রের ধারণা তৈরি করে, যেখানে জনগণ নয়, “দক্ষ ব্যবস্থাপক”-ই রাজনীতির নিয়ামক।
কিন্তু রাষ্ট্র কোনো ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প নয়, এটি জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিফলন। প্রজাতন্ত্র স্থিতি পায় ব্যালটের ঘড়িতে, যে ঘড়ির কাঁটা কারও ইচ্ছেমতো থামানো যায় না। নির্বাচনের সময়, গতি বা ফলাফল নিয়ে ভয় দেখানোর পরিবর্তে আমাদের দায়িত্ব হলো সেই ঘড়িটিকে সচল রাখা, যাতে জনগণই হয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস।
জেনারেল ভূঁইয়ার প্রস্তাবিত “প্রাগম্যাটিক” পথটি যতই বাস্তবসম্মত মনে হোক, তার ভেতরে নিহিত আছে গণতন্ত্রের স্থবিরতার বীজ। আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সেই স্থবিরতা থেকে মুক্ত থাকা, ব্যালটের ঘড়িকে চালু রাখা, এবং সব রাজনৈতিক শক্তিকে সেই সময়ের অধীন আনতে সক্ষম হওয়া। কারণ শেষ পর্যন্ত জনগণের ভোটই এই প্রজাতন্ত্রের প্রাণ, আর সেটিকে স্থগিত রাখা মানেই জাতির হৃদস্পন্দন থামিয়ে দেওয়া।
ইরান যুদ্ধ, পরিচয়ের রাজনীতি এবং বৈশ্বিক সংকটের নতুন সমীকরণ

মো. অহিদুজ্জামান
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতকে কেবল সামরিক পরিভাষায় ব্যাখ্যা করলে তার অন্তর্নিহিত বাস্তবতা ধরা পড়ে না। এটি কেবল ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও বিমান হামলার সংঘর্ষ নয়; বরং পরিচয়, আদর্শ, ভূরাজনীতি ও বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের লড়াই। ইরানকে বোঝার জন্য তাই তার সামরিক সক্ষমতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার রাষ্ট্রচেতনা, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং আদর্শিক কাঠামো। এই সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গভীর প্রশ্ন: ইরান নিজেকে কীভাবে দেখে, এবং বিশ্ব তাকে কীভাবে দেখতে চায়।
ইরানিদের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের আইডেন্টিটি। রাষ্ট্রের ভেতরে রয়েছে বহু জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য—পার্সিয়ান, আজারি, কুর্দি, বালুচি, আরবসহ নানা সম্প্রদায়। শিয়া মুসলিম সমাজের মধ্যেও রয়েছে মতাদর্শিক ভিন্নতা। কিন্তু সংকটের মুহূর্তে যে পরিচয়টি সবার আগে সামনে আসে, তা হলো পারস্য সভ্যতার ধারাবাহিকতা। এই পরিচয় আধুনিক জাতীয়তাবাদের চেয়েও গভীর; এটি হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যিক অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার।
ইরানের জাতীয় চেতনায় পরাজয়ের স্মৃতির চেয়ে প্রতিরোধ ও পুনরুত্থানের বয়ান অধিক প্রভাবশালী। আরব বিজয়, মঙ্গোল আক্রমণ, ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, দীর্ঘ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা—প্রতিটি অধ্যায় তারা টিকে থাকার সংগ্রাম হিসেবে পুনর্নির্মাণ করেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বর্তমান সংঘাতে তাদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করছে। ফলে বাইরের চাপ যত বাড়ছে, অভ্যন্তরীণ সংহতিও তত শক্তিশালী হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, ইরানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীরে রয়েছে শিয়া ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন। হযরত আলী রাঃ, ইমাম হাসান রাঃ ও ইমাম হোসেন রাঃ-এর আদর্শ তাদের নৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। কারবালার ঘটনা তাদের কাছে কেবল ইতিহাস নয়; এটি ন্যায়বিচার, আত্মত্যাগ ও অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থানের প্রতীক। শাহাদাত এখানে কেবল ধর্মীয় ধারণা নয়, বরং জাতি ও বিশ্বাস রক্ষার সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের চূড়ান্ত রূপ।
এই প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে পরিচিত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি-কে ঘিরে আবেগ ও রাজনৈতিক প্রতীকী শক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৮৬ বছর বয়সে তাঁর শাহাদাত নিয়ে যে আলোচনা তৈরি হয়েছে, তা অনেকের মতে জাতিকে আরও আবেগপ্রবণ ও সংঘবদ্ধ করেছে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, জীবিত নেতৃত্বের চেয়ে শহীদের বয়ান দীর্ঘমেয়াদে অধিক শক্তিশালী সামাজিক সমাবেশ ঘটায়। ইরানে এই প্রতীকী রাজনীতি রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধকে নৈতিক বৈধতা দিচ্ছে।
বর্তমান সংঘাতে ইরান এমন দেশগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করছে, যেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে অথবা যারা Abraham Accords-এর মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। এর মাধ্যমে তেহরানের কৌশলগত বার্তা স্পষ্ট: তারা এই সংঘাতকে সীমিত আঞ্চলিক বিরোধ নয়, বরং অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে দেখছে।
ইরানের ধারণা, হারানোর চেয়ে প্রমাণ করার বিষয় এখানে বড়। তাদের কৌশল “ডিটারেন্স বাই পানিশমেন্ট”—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের ভূখণ্ডে যুদ্ধের ব্যথা অনুভব করানো। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাপের মুখে পড়বে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা স্থাপত্য পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন তৈরি হবে। এই কৌশল সরাসরি সামরিক বিজয়ের চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল।
বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের হাতে এখনো কয়েক মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো ব্যালিস্টিক মিসাইল ও ড্রোন সক্ষমতা রয়েছে। এই অস্ত্রভাণ্ডারের একটি বড় অংশ ভূগর্ভস্থ টানেল, পাহাড়ি স্থাপনা ও সুরক্ষিত ঘাঁটিতে সংরক্ষিত। বহু বছর ধরে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি নিয়ে তারা প্রতিরক্ষা অবকাঠামো গড়ে তুলেছে।
শুধুমাত্র এয়ার স্ট্রাইক দিয়ে এই সক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা কঠিন। স্থলাভিযান ছাড়া সিদ্ধান্তমূলক ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইরানের পর্বতময় ভূখণ্ড, বিস্তৃত এলাকা ও সুসংগঠিত সামরিক প্রস্তুতি বিবেচনায় এমন অভিযান যে কোনো শক্তির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। ফলে সরাসরি স্থল অভিযান রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত হবে।
এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকান প্রভাব ও নিরাপত্তা স্থাপত্য গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি দীর্ঘদিন ধরে আরব দেশগুলোর নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি সেই ঘাঁটিগুলোই আক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে, তাহলে নিরাপত্তা কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
এর ফলশ্রুতিতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা দুর্বল হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো বিদেশি বিনিয়োগ হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার রাজনৈতিক ঝুঁকিকে দ্রুত মূল্যায়ন করে। অনিশ্চয়তা বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস, মুদ্রা চাপে পতন এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।
রাশিয়া ও চীন সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে এমন সম্ভাবনা কম, কিন্তু তারা কৌশলগতভাবে ইরানকে সহায়তা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রকে পরোক্ষভাবে চাপে রাখা তাদের দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য। জ্বালানি বাণিজ্য, সামরিক প্রযুক্তি সহযোগিতা ও কূটনৈতিক সমর্থনের মাধ্যমে তারা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। ফলে ইরানে পশ্চিমাপন্থী রেজিম পরিবর্তন সহজ হবে না। বরং দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা বা নিয়ন্ত্রিত সংঘাতের সম্ভাবনাই বেশি।
এই সংঘাতের প্রভাব বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি প্রায় ১০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতি বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি, সরবরাহ শৃঙ্খল সংকট ও ঋণচাপের মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত হলে জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি শিল্প উৎপাদন ও পরিবহন খাতে প্রভাব ফেলবে।
বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর ও স্বল্পোন্নত অর্থনীতির জন্য এটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। জ্বালানি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে, বাজেট ঘাটতি বাড়াবে এবং মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত করবে। সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে।
ইরানের বর্তমান অবস্থান বোঝার জন্য তার পরিচয়, আদর্শ ও কৌশলগত হিসাবকে একসঙ্গে দেখতে হবে। এটি কেবল একটি সামরিক সংঘর্ষ নয়; বরং শক্তির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের মুহূর্ত। ইরান তার পারস্য পরিচয় ও শিয়া আদর্শকে অস্তিত্বের প্রশ্নে রূপ দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নিরাপত্তা ও প্রভাবের প্রশ্নে অবস্থান নিয়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলো কৌশলগত সুযোগ খুঁজছে।
পরিস্থিতি জটিল ও অনিশ্চিত। সামরিক উত্তেজনার পাশাপাশি কূটনৈতিক উদ্যোগ ছাড়া স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। ইতিহাস দেখিয়েছে, অস্ত্র দিয়ে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু পরিচয় ও আদর্শকে দমন করা যায় না।
আমরা শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রত্যাশা করি। কারণ এই সংঘাত কেবল একটি অঞ্চলের সংকট নয়; এটি বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে অস্থিরতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।
বন্ধকী কূটনীতির দেশে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির স্বপ্ন

আলিফ ইফতেখার
গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট (বিইআই)
দীর্ঘ দুই দশক পর ক্ষমতায় ফিরেছে বিএনপি। সম্প্রতি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান যখন বললেন, "আমরা জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতিতে ফিরে যেতে চাই" তখন রাজনৈতিক বিশ্বস্ততার দিক থেকে বক্তব্যটি হয়তো অনুমানযোগ্যই ছিল। কিন্তু কূটনৈতিক কৌশলের দিক থেকে এটি একটি বিপজ্জনক সরলীকরণ। কারণ অতীতের আয়না দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখা যায় না! বিশেষত যখন সেই অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে ব্যবধান কেবল সময়ের নয়, বরং বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের।
জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করার যথেষ্ট কারণ আছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাঁক পরিবর্তনকারী অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তিনি রাজনৈতিকভাবে এক বিপর্যস্ত একটি দেশকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন। জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি মূলত 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও এর মূল প্রাণ ছিল 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' এবং 'জাতীয় স্বার্থ রক্ষা'।

১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে তিনি এক ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল একটি স্বনির্ভর ও মর্যাদাবান রাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে জাতীয় স্বার্থই হবে প্রধান অগ্রাধিকার। তিনি স্নায়ুযুদ্ধের উত্তাল সময়ে কোনো পরাশক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সব ব্লকের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা ছিল তাঁর সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৌশলগত পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর থেকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি যে একমুখী নির্ভরতা তৈরি হয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারসাম্য আনাই ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় প্রেক্ষাপট। এই সময়ে ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন তথা ফারাক্কা বাঁধ ইস্যু এবং সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চরম টানাপোড়েন চলছিল। অন্যদিকে, অনেক মুসলিম দেশ তখনও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে দেখত এবং পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এমন একটি জটিল সময়ে জিয়াউর রহমান জাতিসংঘে ফারাক্কা ইস্যুটি উত্থাপন করে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য নতুন অর্থনৈতিক ও শ্রমবাজারের দ্বার উন্মোচন করেন।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জাপানকে হারিয়ে অস্থায়ী আসন জেতা ছিল সেই কূটনৈতিক দূরদর্শিতারই ফসল। সার্কের ধারণার বীজ বপনেও তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। কিন্তু প্রশ্নটি হলো যে সেই নীতি কি এখন হুবহু প্রযোজ্য? উত্তর হলো: না! জিয়াউর রহমানের সময় বিশ্ব ছিল দুই মেরুতে বিভক্ত। ভারসাম্য রাখার কাজটি ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ কারণ দুটি পরাশক্তির প্রত্যেকেই চাইত বাংলাদেশ তার শিবিরে থাকুক। সেই টানাটানিতে বাংলাদেশের হাতে একটি স্বাভাবিক দরকষাকষির সুযোগ ছিল। আজকের বিশ্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একমেরু যুগ শেষ হয়ে বিশ্ব এখন বহুমেরু বা 'মাল্টিপোলার' কাঠামোর দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। চীন এখন আর কেবল একটি বড় দেশ নয় সে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি, যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা কার্যত একটি নতুন ঠান্ডা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবার নিজের ভূরাজনৈতিক উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। ভারত এখন আর শুধু আঞ্চলিক শক্তি নয়, সে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর নেতৃত্বের দাবিদার এবং কোয়াড-এর অংশীদার। এই জটিল সমীকরণে বাংলাদেশকে যদি কেউ ১৯৭৫-৮১ সালের মানচিত্র দিয়ে পথ চলতে বলেন, তাহলে সেটি কেবল অকার্যকর নয় বরং কিছুক্ষেত্রে বিপজ্জনকও।
বিশ্বে ভারসাম্যের দাবি আরও কঠিন, কারণ এখন প্রতিটি শক্তিকেন্দ্র অনেক বেশি শর্ত আরোপ করে। চীন-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় ঢাকার ওপর চাপ আসছে উভয় দিক থেকে। যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ চীনা অবকাঠামো বিনিয়োগে সতর্ক থাকুক। চীন চায় বাংলাদেশ তার কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগাক। ভারত চায় তার নিজস্ব নিরাপত্তা স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকুক। এই তিন দিক থেকে আসা টানে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' নীতিটি এখনও সর্বজন গ্রহণযোগ্য কারণ বাংলাদেশ কোনো দেশের সাথে শত্রুতা পোষণ করার বিলাসিতা বা ঝুঁকি নিতে পারে না।এটি অবাস্তব। তবে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কোন মাঠের কৌশল নয়।
 প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনে জেতার আগে ও পরে "সবার আগে বাংলাদেশ" নীতির কথা বলেছেন। কথাটি শুনতে সুন্দর এবং রাজনৈতিকভাবে হয়তো কার্যকরও। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে স্লোগান আর কৌশল এক জিনিস নয়। "বাংলাদেশ প্রথম" নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে যা দরকার, তার তালিকাটি দীর্ঘ। দরকার একটি শক্তিশালী, দলনিরপেক্ষ ও পেশাদার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দরকার থিংকট্যাংক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে নিবিড় সংযোগ যাকে কূটনীতির ভাষায় আমরা বলে থাকি 'ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি'। আজকের বাস্তবতায় এর কতটুকু আছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ ও পদায়নের শিকার ও সেটি সকল সরকারের সময় থেকেই চলমান। দূতাবাসগুলোতে রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে মেধাভিত্তিক নেতৃত্ব কতটুকু নিশ্চিত সেটি একটি বিষয়। থিংকট্যাংকের সংখ্যা বাড়লেও নীতিনির্ধারণে তাদের প্রকৃত প্রভাব প্রশ্নবিদ্ধ! এই ভিত্তি না গড়ে কেবল "জিয়ার নীতিতে ফিরে যাব" বললে সেটি একটি প্রতীকী অঙ্গীকার হয়ে থাকবে, কার্যকর কৌশল হবে না। সব কিছুর মূলে যেটি দরকার সেটি হলো পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য, যাতে এক, সরকার বদলালে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিও বদলে না যায়। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীরের একটি মন্তব্য এই আলোচনার কেন্দ্রে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের কূটনীতির বড় সমস্যা বাইরে নয়, ভেতরে। এটি শুধু একটি কূটনৈতিক পর্যবেক্ষণ নয় এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা নির্ণয়ও বটে। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশ ৫৪ বছরে মাত্র দুইবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক সংস্কার করেছে ১৯৮২ ও ১৯৯৫ সালে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীন নিয়মিতভাবে তাদের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি পর্যালোচনা করে। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে এবং সরকার ও বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের দীর্ঘস্থায়ী অভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক কার্যক্রমকে কাঠামোগতভাবে দুর্বল করে রেখেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার আরও একটি উদ্বেগজনক ও কম আলোচিত মাত্রা আছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের সমালোচনা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিষয়টি আর স্বাভাবিক থাকে না। এটিকে হয়ে যায় কূটনৈতিক দ্বৈততা।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনে জেতার আগে ও পরে "সবার আগে বাংলাদেশ" নীতির কথা বলেছেন। কথাটি শুনতে সুন্দর এবং রাজনৈতিকভাবে হয়তো কার্যকরও। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে স্লোগান আর কৌশল এক জিনিস নয়। "বাংলাদেশ প্রথম" নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে যা দরকার, তার তালিকাটি দীর্ঘ। দরকার একটি শক্তিশালী, দলনিরপেক্ষ ও পেশাদার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দরকার থিংকট্যাংক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে নিবিড় সংযোগ যাকে কূটনীতির ভাষায় আমরা বলে থাকি 'ট্র্যাক টু ডিপ্লোম্যাসি'। আজকের বাস্তবতায় এর কতটুকু আছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর দীর্ঘদিন ধরে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ ও পদায়নের শিকার ও সেটি সকল সরকারের সময় থেকেই চলমান। দূতাবাসগুলোতে রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে মেধাভিত্তিক নেতৃত্ব কতটুকু নিশ্চিত সেটি একটি বিষয়। থিংকট্যাংকের সংখ্যা বাড়লেও নীতিনির্ধারণে তাদের প্রকৃত প্রভাব প্রশ্নবিদ্ধ! এই ভিত্তি না গড়ে কেবল "জিয়ার নীতিতে ফিরে যাব" বললে সেটি একটি প্রতীকী অঙ্গীকার হয়ে থাকবে, কার্যকর কৌশল হবে না। সব কিছুর মূলে যেটি দরকার সেটি হলো পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য, যাতে এক, সরকার বদলালে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিও বদলে না যায়। সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবীরের একটি মন্তব্য এই আলোচনার কেন্দ্রে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের কূটনীতির বড় সমস্যা বাইরে নয়, ভেতরে। এটি শুধু একটি কূটনৈতিক পর্যবেক্ষণ নয় এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা নির্ণয়ও বটে। তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশ ৫৪ বছরে মাত্র দুইবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক সংস্কার করেছে ১৯৮২ ও ১৯৯৫ সালে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীন নিয়মিতভাবে তাদের পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি পর্যালোচনা করে। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে এবং সরকার ও বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের দীর্ঘস্থায়ী অভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক কার্যক্রমকে কাঠামোগতভাবে দুর্বল করে রেখেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার আরও একটি উদ্বেগজনক ও কম আলোচিত মাত্রা আছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের সমালোচনা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রীয় পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিষয়টি আর স্বাভাবিক থাকে না। এটিকে হয়ে যায় কূটনৈতিক দ্বৈততা।
বাস্তবতাটি অনেকটা এইরকম যে সরকার যখন কোনো দেশের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়, তখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের একটি অংশ সেই দেশের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক ও অপ্রকাশিত সখ্যতা গড়ে তোলে। অনেকগুলো উদ্দেশ্যের মাঝে একটি উদ্দেশ্য সম্ভবত থাকে সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগকে দুর্বল করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। বাহ্যত এটিকে মতপার্থক্য বলে দেখানো হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি নীরব বিশ্বাসঘাতকতা যা সরকারি দল ও বিরোধীদল ক্রমান্বয়ে এদেশে করে আসছে।
এর ক্ষতিও বহুমাত্রিক। বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আর বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘমেয়াদী কূটনৈতিক কৌশল তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ প্রতিটি সরকার পরিবর্তনে পররাষ্ট্রনীতিও পুনর্লিখিত হয়। জিয়াউর রহমানের সময়ে এই বিভেদ এতটা তীব্র ছিল না এবং বিদেশি শক্তির এটি ব্যবহার করার সুযোগও ছিল সীমিত। তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং বৈশ্বিক সংযুক্তির এই যুগে সেই সুযোগ এখন উন্মুক্ত এবং অনেক বেশি কার্যকর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, নতুন সরকার জিয়াউর রহমানের সেই ঐতিহাসিক পররাষ্ট্রনীতিতে ফিরে যেতে চায় যে নীতির মূল ছিল কোনো পরাশক্তির অনুসারী না হওয়া, পূর্ব বা পশ্চিম কোনো ব্লকে নয়, বরং সবার সঙ্গে সম্মানজনক ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক। এই বক্তব্য যখন শোনা যাচ্ছে, তখন একটি প্রশ্ন অবধারিতভাবে সামনে আসে যে নতুন সরকার যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে, সেই মঞ্চের মেঝে কি আদৌ তার নিজের?
নির্বাচনের মাত্র অল্প কয়দিন আগে, বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি সই করে যায়। চুক্তির খসড়া গোপন রাখতে আগেই নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট সই করা হয়েছিল। অর্থাৎ, জনগণকে না জানিয়ে কেবল বাস্তবায়নের দায়টি পরের সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে চুক্তিটি সম্পন্ন করা হয়েছে। চুক্তির শর্তগুলো পড়লে স্পষ্ট হয়, এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক চুক্তি নয় এটি একটি ভূরাজনৈতিক শপথপত্র। চুক্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কোনো 'নন-মার্কেট ইকোনমি'র সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবে না। এটি চীন, রাশিয়াসহ একাধিক দেশের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। শর্ত ভঙ্গ হলে যুক্তরাষ্টি পারস্পরিক শুল্ক পুনর্বহাল করতে পারবে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ তাই সরাসরি বলেছেন, এই চুক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান "সবার আগে" নয় বরং সবার পেছনে! এখন খলিলুর রহমানের বক্তব্যের পাশে এই চুক্তিটি রেখে দেখা যেতে পারে। একদিকে সরকার বলছে জিয়ার আদর্শে ফিরবে। কোনো ব্লকে নয়, ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির দিকে এগোবে। অন্যদিকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া একটি চুক্তি বলছে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করলে হয়তো শাস্তি আসবে। জিয়াউর রহমান স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, কোনো ব্লকের চাপে তা ছাড়েননি। সরকার সেই জিয়ার নীতির কথা বলছে, কিন্তু হাতে পেয়েছে এমন একটি দলিল যা সেই নীতির ঠিক বিপরীত।
এখানেই প্রশ্নটি কেবল কূটনৈতিক থাকে না, রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। এই চুক্তি কি সত্যিই কোনো অর্থনৈতিক সুবিধার বিবেচনায় হয়েছিল? নাকি এটি সেই কূটনৈতিক দ্বৈততার একটি চরম ও স্পষ্ট রূপ যেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্তে নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির হাত ও পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে? চুক্তির সময়কাল, গোপনীয়তার শর্ত এবং দায় চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল এই তিনটি একসঙ্গে দেখলে উত্তরটি অনুমানের জায়গায় থাকে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি সত্যিই জিয়ার নীতিতে ফিরতে চান, তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত এই চুক্তির পূর্ণ পর্যালোচনা এবং সংসদে প্রকাশ্য বিতর্ক! কারণ যে নীতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে যে চুক্তি উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে এই দুটো একসঙ্গে টেকে না।
ধরা যাক, সংসদে চুক্তিটি বাতিলের প্রস্তাব উঠল। পরিণতি সবার জানা যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক পুনর্বহাল করবে। কিন্তু এখানেই থামবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপর চাপ আসবে। আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর মনোভাব বদলাবে। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রশ্নটি আর কূটনৈতিক থাকবে না, হয়ে উঠবে অস্তিত্বের। এটি এমন এক শিকল যে শিকলের শিকড় আমাদের অর্থনীতির একমাত্রিকতায়। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক থেকে, এবং সেই পোশাকের সিংহভাগ গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। অর্থাৎ যে দেশ বা জোট আমাদের রপ্তানির দরজা নিয়ন্ত্রণ করে, সে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির দরজাও কার্যত নিয়ন্ত্রণ করে। এই বাস্তবতায় "ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি"র কথা বলা যায় বক্তৃতামঞ্চে বাস্তবের কূটনৈতিক টেবিলে নয়। বরং এখান থেকেই শুরু হয় আরও গভীর একটি সংকটের আখ্যান।
এখানেই জিয়াউর রহমানের সময়ের সঙ্গে আজকের সবচেয়ে নীরব কিন্তু সবচেয়ে গভীর পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। জিয়া ভারসাম্য রাখতে পেরেছিলেন কারণ তখন বাংলাদেশের অর্থনীতি কোনো একক বাজারের এতটা মুখাপেক্ষী ছিল না। তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, কারণ সেই সম্পর্ক ছিন্ন করলে পশ্চিম তাঁকে যেভাবে শাস্তি দিতে পারত, তার একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। আজকের বাংলাদেশ সেই সুবিধার জায়গায় নেই। কারণ আমরা গত তিন দশকে পোশাক খাতের সাফল্যের আড়ালে একটি চরম বিপজ্জনক একমাত্রিকতা তৈরি করেছি যা এখন আমাদের কূটনৈতিক গলায় ফাঁস হয়ে বসেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে একে বলেছেন "মাদার অফ অল ডিলস"। এই চুক্তির আওতায় ভারতের টেক্সটাইল, পোশাক ও চামড়াজাত পণ্য ইউরোপীয় বাজারে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে ঠিক সেই পণ্যগুলো, যেগুলো বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের সরাসরি প্রতিযোগী।

এই একটি চুক্তি বাংলাদেশের জন্য যা করতে পারে, তা কোনো যুদ্ধ বা অবরোধও পারে না। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় বাজারে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি মর্যাদা থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে সেই সুবিধা ধীরে ধীরে কমবে। আর সে কারণেই বোধকরি সরকার এই উত্তরণ পিছিয়ে দেবার কথা ভাবছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভারত ইউরোপে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়ে যাচ্ছে, অনেক বড় উৎপাদনসক্ষমতা ও অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য নিয়ে।
এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সামনে যে প্রশ্নটি দাঁড়িয়ে, সেটি আর কেবল পররাষ্ট্রনীতির নয়, এটি জাতীয় অস্তিত্বের। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি আমাদের পূর্বমুখী কূটনীতির হাত বেঁধে দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত-ইইউ চুক্তি আমাদের প্রধান রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতার সমীকরণ মৌলিকভাবে বদলে দিচ্ছে। আর মাঝখানে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী স্লোগান নিয়ে, একটিমাত্র একমাত্রিক অর্থনীতি নিয়ে, যার পোশাক খাতের উপর অতিনির্ভরতা এখন জাতীয় দুর্বলতার সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে!
তাহলে পররাষ্ট্রনীতিতে আসলে কী দরকার? শুধু অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য কি যথেষ্ট? একদমই নয়। ঐকমত্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঐকমত্য একটি শক্ত শর্ত মাত্র, কোনভাবেই সমাধান নয়। কারণ একটি দুর্বল অর্থনীতির পিঠে বসে শক্তিশালী কূটনীতি করার চেষ্টা অনেকটা বালির উপর প্রাসাদ গড়ার কল্পনার মতো হয়ে যায়। আসল সমাধান হলো একটি সমন্বিত জাতীয় অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যেখানে পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিল্প এবং অর্থ মন্ত্রণালয় একটি অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করবে।
সেই পরিকল্পনার তিনটি স্তম্ভ হওয়া দরকার। প্রথমত, রপ্তানি বাজারের জরুরি বৈচিত্র্যায়ন। আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকায় নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, যাতে কোনো একটি বাজার বন্ধ হলে পুরো অর্থনীতি ধসে না পড়ে। দ্বিতীয়ত, পোশাকের পাশাপাশি প্রযুক্তি, ওষুধ, কৃষিপ্রক্রিয়াজাত পণ্য ও সফটওয়্যারে রপ্তানি সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে নয়তো ভারত-ইইউ চুক্তির ধাক্কা সামলানো সম্ভব হবে না। তৃতীয়ত, চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু ঋণনির্ভরতা থেকে বের করে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পারস্পরিক বাজার সম্পর্কে রূপান্তর করতে হবে।কূটনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভবত কোনো ঘোষণাপত্রে লেখা থাকে না, এটি অর্জিত হয় বিকল্পের শক্তি থেকে। যে দেশ নিজের অর্থনৈতিক বিকল্প তৈরি করতে পারে না, সে দেশ পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতাও কোনভাবেই অর্জন করতে পারে না।
জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি ও তাঁর মূলনীতি যা ছিল স্বাধীনচেতা, ভারসাম্যপূর্ণ, বাংলাদেশকেন্দ্রিক কূটনীতি তা এখনও প্রাসঙ্গিক। তা একই সাথে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশের চেতনাকেও ধারণ করে কিন্তু সেই মূলনীতি বাস্তবায়িত করতে হবে ২০২৬ সালের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায়, ১৯৭৮ সালের মানচিত্রে নয়।আজকের সরকার যদি সত্যিই জিয়াউর রহমানের পথে হাঁটতে চায়, তাহলে শুধু তাঁর কূটনৈতিক দর্শন নয়, তাঁর সেই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার স্বপ্নটিকেও ধারণ করতে হবে। তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে সত্যিকারের সম্মান জানাতে হলে তাঁর নীতির হুবহু অনুকরণ করে কোন লাভ নেই, তাঁর মতো করে নিজের সময়ের, বর্তমানের প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। জিয়াউর রহমান তাঁর সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলেন সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে। তাঁরই পুত্র আজকের প্রধানমন্ত্রী সেই সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কিভাবে দেবেন তা সময় বলে দেবে।
লেখক- -আলিফ ইফতেখার, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট (বিইআই)
বয়ান বদলের রাজনীতি: বিএনপির নতুন কমিউনিকেশন স্থাপত্য ও আগামীর শাসনচিন্তা

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনের ছাত্র হিসেবে রাজনৈতিক যোগাযোগ আমাকে সবসময় তাত্ত্বিক কৌতূহল আর বাস্তব পর্যবেক্ষণের এক দ্বৈত জায়গায় দাঁড় করায়। নির্বাচনকালীন প্রচারণা আমার কাছে শুধু পোস্টার, মিছিল বা টকশো নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বার্তা-ব্যবস্থার প্রয়োগক্ষেত্র। এবারের নির্বাচনে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি কীভাবে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি নিজেদের প্রচারণা নির্মাণ করেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সৃজনশীলতা দেখিয়েছে। কিন্তু নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিএনপির প্রচারণায় যে নাটকীয় রূপান্তর ঘটল, তা বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে। এটি কেবল ভিজ্যুয়াল বা ভাষার পরিবর্তন নয়; বরং একটি গভীর কৌশলগত পুনর্গঠন।
রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক প্রশ্ন জরুরি: কে করছে, কী করছে, কীভাবে করছে এবং কেন করছে। এই ফ্রেমে বিএনপির প্রচারণাকে বিশ্লেষণ করলে একটি সমন্বিত কমিউনিকেশন আর্কিটেকচার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, মুখপাত্রের অবস্থানকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। শান্ত, সংযত কিন্তু দৃঢ় ভাষার একজন স্পোকসপারসন হিসেবে মাহদী আমিনের আবির্ভাব দলীয় বার্তার টোনালিটি পাল্টে দেয়। একই সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে নেটওয়ার্ক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন ড. জিয়া হায়দার। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বার্তা নির্মাণ ও ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেন এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান এপোলো। কেন্দ্র, তৃণমূল ও ডিজিটাল স্তরে এই ত্রিস্তরীয় সমন্বয় একটি কাঠামোগত পরিণতির ইঙ্গিত দেয়।
তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সংক্ষিপ্ত ভিডিও কনটেন্টের ধারাবাহিকতা। এক মিনিট থেকে দেড় মিনিটের ক্লিপ, স্পষ্ট বার্তা, নিয়ন্ত্রিত আবেগ এবং ধারাবাহিক ন্যারেটিভ নির্মাণ। অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি, এই কনটেন্টগুলোর পেছনে কাজ করছেন ড. সাইমুম পারভেজ। তাঁকে আমি পূর্বে চিনতাম গবেষক হিসেবে, র্যাডিকালাইজেশন ও রাজনৈতিক ইসলাম বিষয়ক গবেষণায় তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিসরে স্বীকৃত। নীতিনির্ধারণী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় তাঁর অবদান তাঁকে একজন বিশ্লেষণী মস্তিষ্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই মানুষ যখন সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগের ময়দানে নেমে আসেন এবং সৃজনশীলভাবে ন্যারেটিভ নির্মাণ করেন, তখন সেটি নিছক ক্যাম্পেইন নয়; এটি জ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগ।
এই ভিডিওগুলোর কৌশলগত দিক বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। ধর্মীয় বিভ্রান্তি ভাঙতে তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা, “ফ্যামিলি কার্ড” ধারণাকে সাধারণ ভাষায় উপস্থাপন, জুলাইয়ের আহত এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে এক আবেগীয় ধারায় যুক্ত করা। এগুলো কেবল ইমোশনাল কনটেন্ট নয়; এগুলো ন্যারেটিভ শিফটের প্রয়াস। একটি দলকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে বের করে আক্রমণাত্মক কিন্তু সংযত বয়ানে স্থানান্তর করা হয়েছে। কমিউনিকেশনের ভাষায় এটি রিফ্রেমিং। বিরোধীদের নির্ধারিত প্রশ্নে প্রতিক্রিয়া না দিয়ে, নিজস্ব প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সাধারণত উচ্চকণ্ঠ, সংঘাতমুখর এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাষা প্রাধান্য পায়। বিশ্লেষণী, সংযত এবং তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত ব্যক্তিদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। অতীতে আওয়ামী লীগের মধ্যে গওহর রিজভির মতো কিছু নীতিনির্ধারণী বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি ছিল, কিন্তু সেই ধারাটি ক্রমে দুর্বল হয়েছে। বিএনপির সাম্প্রতিক কমিউনিকেশন কাঠামো দেখে মনে হয়েছে, তারা হয়তো একটি নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর তৈরি করার চেষ্টা করছে যেখানে গবেষক ও টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা দৃশ্যমান ভূমিকা রাখছেন।
তবে নির্বাচন জেতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা দুটি ভিন্ন প্রকল্প। ক্ষমতায় যাওয়ার পর রাজনৈতিক যোগাযোগের চ্যালেঞ্জ আরও জটিল হবে। এতদিন বিরোধী অবস্থানে থাকায় সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমিকদের একটি অংশ বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গেলে একই পরিসরের বড় অংশ সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করবেন, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিক। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দলকে এমন এক যোগাযোগনীতি গ্রহণ করতে হবে যা সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে না দেখে, নীতিগত সংলাপের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।
এখানেই একাডেমিকভাবে প্রশিক্ষিত, নীতি-বিশ্লেষণে দক্ষ এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ব্যক্তিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। গুড গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কেবল ব্যবসায়িক স্বার্থগোষ্ঠী বা মাঠের সংগঠকদের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। প্রয়োজন হবে জ্ঞানভিত্তিক নীতি-প্রস্তুতি এবং যুক্তিনির্ভর যোগাযোগ। বাংলাদেশের আগামীর রাজনীতি বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে টেকসই হবে না। এটি টিকবে নীতির স্বচ্ছতা, যুক্তির দৃঢ়তা এবং সহমর্মিতার ওপর।
বিএনপি এই নির্বাচনে যে ট্যালেন্ট ও দক্ষতাকে ব্যবহার করেছে, ক্ষমতায় গেলে সেই দক্ষতাকে কতটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে, সেটিই হবে তাদের শাসনদক্ষতার পরীক্ষা। কমিউনিকেশন টিমকে যদি কেবল নির্বাচনকালীন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্জিত ন্যারেটিভ সুবিধা দ্রুত ক্ষয় হবে। কিন্তু যদি তাদের নীতি-প্রণয়ন, জনসম্পৃক্ততা এবং সংকট-ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে জায়গা দেওয়া হয়, তবে এটি একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে।
শেষ পর্যন্ত দল টিকে থাকে স্লোগানে নয়, টিকে থাকে কাঠামোগত সক্ষমতায়। নীরবে যারা চিন্তা, গবেষণা এবং কৌশল দিয়ে রাজনৈতিক বয়ান নির্মাণ করেন, তারাই দীর্ঘমেয়াদে রাজনীতির রূপ নির্ধারণ করেন। বিএনপির সামনে এখন সুযোগ রয়েছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সজ্জিত, সংযত কিন্তু দৃঢ় রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার। তারা সেই পথ বেছে নেবে কিনা, সেটিই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের শাসনচিত্র।
২০০৮–এর পর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন: গণতন্ত্রের গুণগত মানের এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা

মো. অহিদুজ্জামান
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক
বাংলাদেশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার বহুল প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। নির্বাচন কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয়; এটি রাষ্ট্রের নৈতিক পরিপক্বতার মাপকাঠি, নাগরিক চেতনার আয়না এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন। ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক ৫ আগস্টের গণআন্দোলনের পর এই নির্বাচন একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার পরীক্ষা। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি গণতন্ত্রকে কেবল ভোটের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখব, নাকি এটিকে সামাজিক সংহতি, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক জবাবদিহির ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারব?
২০০৮ সালের পর এই প্রথম দেশ একটি প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে অংশগ্রহণ, গ্রহণযোগ্যতা এবং বৈধতা নিয়ে যে বিতর্ক আমাদের রাজনৈতিক পরিসরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবারের নির্বাচন তা অতিক্রম করার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা গণতন্ত্রের প্রাণ; কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি সহিংসতা, অবিশ্বাস এবং প্রতিহিংসায় রূপ নেয়, তবে তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী না করে দুর্বল করে।
এবারের নির্বাচনের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একই দিনে দুটি পৃথক ব্যালটে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য, অন্যটি গণভোটের জন্য। এই দ্বৈত প্রক্রিয়া একদিকে নাগরিক অংশগ্রহণকে বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি করেছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক দক্ষতা ও সময় ব্যবস্থাপনার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে নির্বাচনটি কেবল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নয়; এটি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সাংগঠনিক দক্ষতারও পরীক্ষা।
গণতন্ত্রের শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে নয়; বরং অংশগ্রহণের বিস্তৃতিতে। একটি কম্পিটিটিভ ইলেকশনের প্রধান শর্ত হলো ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। ভোটার উপস্থিতি যত বেশি, নির্বাচনের সামাজিক বৈধতা তত দৃঢ় হয়। ২০০৮–এর পর যে বিতর্ক আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিভক্ত রেখেছে, এবারের নির্বাচন তা নিরসনের সুযোগ এনে দিয়েছে।
কিন্তু অংশগ্রহণ কেবল ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নয়; এটি আস্থার প্রশ্ন। ভোটার যদি মনে করেন তার ভোট নিরাপদ, গণনা স্বচ্ছ এবং ফলাফল সম্মানিত হবে, তবেই তিনি অংশ নেবেন। এই আস্থা তৈরি করা রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং নাগরিক সমাজ—সবার সম্মিলিত দায়িত্ব।
বিশেষত তরুণ ভোটারদের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, যুবসমাজ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, সেই শক্তি কি প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হবে, নাকি তা কেবল আবেগের বিস্ফোরণে সীমাবদ্ধ থাকবে?
একই দিনে সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট আয়োজন একটি উচ্চাভিলাষী প্রশাসনিক উদ্যোগ। দুটি ব্যালট মানে ভোটারকে দুইবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ভোটকর্মীদের দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বাড়তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। দীর্ঘ সারি, ধীরগতির ভোটগ্রহণ বা ব্যালট বিভ্রান্তি সহজেই উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। এখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা এবং ভোটারদের দ্রুত ও নির্বিঘ্নে ভোট প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করা। ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, স্পষ্ট নির্দেশনা এবং বুথ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অপরিহার্য। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণ ও আপত্তি জানানো গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু তা যেন প্রক্রিয়াকে অচল করে না দেয়। নির্বাচন একটি ফলাফল নয়; এটি একটি প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি যদি সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ হয়, তবে ফলাফল নিয়ে বিতর্কের সুযোগ কমে যায়।
প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে উত্তেজনা স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তেজনা যেন সহিংসতায় রূপ না নেয়, সেটিই রাজনৈতিক পরিণততার প্রমাণ। ভোটকেন্দ্রে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদের ধৈর্য ধারণ করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করা অপরিহার্য।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে গুজব দ্রুত ছড়ায়। একটি ভুল তথ্য মুহূর্তে সংঘাতে রূপ নিতে পারে। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো কর্মীদের সংযত রাখা এবং উত্তেজনা প্রশমনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরও দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি। বিজয়ী ও বিজিতদের আচরণই নির্ধারণ করবে এই নির্বাচন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে, নাকি দুর্বল করবে। পরাজয় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি ছাড়া গণতন্ত্র টেকসই হয় না।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আমরা একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মতাদর্শিক বিভাজন সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ঐক্যের একটি মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কাদা ছোড়াছুড়ি, তীব্র ভাষা ও সমালোচনা গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেমে যায়, রাষ্ট্র শুরু হয়।
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা কেবল প্রাণহানি বা সম্পদ নষ্ট করে না; এটি অর্থনীতি, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক আস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিতে পারে। তাই সংযম, সংলাপ এবং আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা রাখা জরুরি।
বাংলাদেশ বর্তমানে এক জটিল অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ, কর্মসংস্থান সংকট এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। এই বাস্তবতায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য।
একটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সরকারকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক সমর্থন দেয়। অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগ নীতি বা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অবস্থান তখন অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু নির্বাচনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হলে প্রতিটি নীতিই রাজনৈতিক বিতর্কে আটকে যায়।
আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়শই প্রতিহিংসায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু একটি পরিণত গণতন্ত্রে বিরোধী দল শত্রু নয়; তারা বিকল্প মতের প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষমতার পরিবর্তন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া; প্রতিহিংসা নয়। ধৈর্য, ভালোবাসা, মহানুভবতা ও ক্ষমা—এই শব্দগুলো আবেগঘন শোনাতে পারে, কিন্তু এগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বাস্তব উপাদান। দীর্ঘমেয়াদে যে রাজনীতি সংযম ও সহনশীলতার চর্চা করে, তারাই টিকে থাকে।
আগামীকাল আমরা কেবল ভোট দেব না; আমরা আমাদের রাজনৈতিক চরিত্রের পরীক্ষা দেব। ২০০৮–এর পর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন এবং একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট—এই যুগপৎ বাস্তবতা আমাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে।
শত মতবিরোধ সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। বিজয়ী যদি বিনয়ী হন এবং পরাজিত যদি উদার হন, তবে এই নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের পুনর্গঠনের মাইলফলক। গণতন্ত্র কেবল ব্যালট বাক্সে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আচরণে, ভাষায় এবং পরাজয় মেনে নেওয়ার সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের—আমরা কি উত্তেজনার পথ বেছে নেব, নাকি পরিণত গণতন্ত্রের?
আসুন, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে হাতে হাত রেখে আগামীর একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাই। ইতিহাস আমাদের দেখছে; ভবিষ্যৎ আমাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।
-লেখক মো. অহিদুজ্জামান ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। ইমেইল:[email protected]
আইনের রক্ষক পুলিশ কেন ভয়ের প্রতীকে পরিণত হয়?

রাকিবুল ইসলাম
সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
গতকাল ঢাকার যমুনা এলাকা ও শাহবাগে যা ঘটেছে, তা কেবল একটি দিনের সহিংস ঘটনার বিবরণ নয়; বরং এটি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পুরোনো ও গভীর সংকটকে আবারও সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন, ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ইনকিলাব মঞ্চের কর্মী জাবেরসহ বহু মানুষ আহত হয়েছেন।
কিন্তু এই ঘটনার বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকলে আমরা মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাব। প্রশ্নটি আরও গভীর এবং আরও অস্বস্তিকর—বাংলাদেশে কেন আন্দোলন হলেই পুলিশ এমন মাত্রায় বলপ্রয়োগে যায়?
এই দেশে সরকার বদলায়, ক্ষমতার ভাষ্য বদলায়, রাজনৈতিক স্লোগান পাল্টায়। কিন্তু রাজপথে নাগরিক প্রতিবাদ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকার একটি ভয়ংকর ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, নাগরিকের প্রতিবাদ মানেই যেন পুলিশের চোখে ‘শত্রু’ হয়ে ওঠা। এটি কেবল দুঃখজনক বাস্তবতা নয়; এটি সংবিধান, গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের চেতনার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিককে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব সেই অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা প্রায়ই দেখি, পুলিশ সেই ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে ক্ষমতার একটি নগ্ন ও কঠোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানেই মৌলিক প্রশ্নটি উঠে আসে—এই নিষ্ঠুরতা কি কয়েকজন সদস্যের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফল, নাকি এটি একটি গভীর কাঠামোগত সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ?
পুলিশ সদস্যরাও এই সমাজেরই অংশ। তাঁদেরও পরিবার আছে, জীবন আছে, ঝুঁকি আছে। কিন্তু এই বাস্তবতা কোনোভাবেই অকারণ বলপ্রয়োগ, অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার বা নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানোর নৈতিক বৈধতা দিতে পারে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে যদি আইনই ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার আস্থার ভিত্তি কোথায় দাঁড়াবে?
আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো—এই ধরনের ঘটনার পর খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা স্বচ্ছ তদন্ত, দায় নির্ধারণ বা দৃশ্যমান শাস্তির নজির দেখি। অধিকাংশ সময় ঘটনাগুলো চাপা পড়ে যায়, কিংবা “পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়েছি” এই পরিচিত ও দায়সারা বিবৃতিতেই সব প্রশ্নের ইতি টানা হয়। এর ফলে পুলিশের ভেতরে জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না; বরং এক ধরনের দায়মুক্তির নিশ্চয়তা আরও পোক্ত হয়।
এখানে রাষ্ট্রের দায় দ্বিমুখী। একদিকে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে পুলিশ কোনো রাজনৈতিক শক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর ভেতরে মানবাধিকারভিত্তিক প্রশিক্ষণ, স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা এবং কঠোর ও কার্যকর জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্দোলন মানেই শত্রুতা—এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে না এলে পরিস্থিতির কোনো টেকসই পরিবর্তন সম্ভব নয়।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আন্দোলন একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র যদি প্রতিটি আন্দোলনকে শক্তি দিয়ে দমন করতে চায়, তাহলে সে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নিজের নাগরিকদের থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভয়ের মাধ্যমে শাসন কখনোই টেকসই হয় না—ইতিহাস তার বহু প্রমাণ দিয়েছে।
যমুনা ও শাহবাগের ঘটনাগুলো আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয়, প্রশ্নটি শুধু ‘কে গুলি করল’ তা নয়; প্রশ্নটি হলো—‘কেন বারবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়?’ এই প্রশ্নের সৎ, নিরপেক্ষ ও সাহসী উত্তর না খুঁজলে আজ যে লাঠিচার্জ অন্যের ওপর হচ্ছে, কাল সেটি যে কার ওপর পড়বে, তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না।
রাষ্ট্র যদি সত্যিই জনগণের হয়, তাহলে পুলিশের প্রধান অস্ত্র লাঠি বা গুলি নয়—আইন, সংবেদনশীলতা এবং জবাবদিহিই হওয়া উচিত তার মূল ভিত্তি।
-লেখক রাকিবুল ইসলাম গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী
আবেগ নয়, অর্থনৈতিক বাস্তবতা: জামায়াতের নারী শ্রমনীতি কেন আত্মঘাতী

মো. অহিদুজ্জামান
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক
জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মজীবী মায়েদের জন্য একটি আপাতদৃষ্টিতে মানবিক ও কল্যাণমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীদের কর্মঘণ্টা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হবে, কিন্তু তাদের মজুরি কমবে না। বরং বাকি অংশ সরকার বহন করবে। অর্থাৎ একজন নারী প্রতিটি সন্তানের জন্য প্রায় আড়াই বছর অর্ধেক সময় কাজ করেও পূর্ণ বেতন পাবেন। শুনতে এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, এমনকি সহানুভূতিশীলও মনে হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা অর্থনীতি আবেগ দিয়ে নয়, কাঠামোগত বাস্তবতা ও উৎপাদন সম্পর্ক বোঝার মধ্য দিয়েই পরিচালিত হয়। এই প্রস্তাব সেই বাস্তবতার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটাই মূল প্রশ্ন।
এই প্রস্তাবের বাস্তবতা বোঝার জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দিয়েই আলোচনা শুরু করা যুক্তিযুক্ত। কারণ এই খাতেই দেশের নারী শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় অংশ যুক্ত। বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী, তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী। একই সঙ্গে এটিই বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস এবং সামগ্রিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড।
বাংলাদেশ বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে মূলত একটি কাঠামোগত কারণে: স্বল্প শ্রমমূল্য। এই শিল্পে কাঁচামালের প্রায় পুরোটাই আমদানি নির্ভর। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে পোশাক রপ্তানি সম্ভব হয় মূলত শ্রমের উপবৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ surplus value of labour-এর মাধ্যমে। সহজ ভাষায় বললে, শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে, তার পুরোটা মজুরি হিসেবে দেওয়া হয় না; একটি বড় অংশ মালিকের হাতে উদ্বৃত্ত হিসেবে থেকে যায়।
বিষয়টি সংখ্যায় বোঝা যাক। ধরুন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের প্রতি ঘণ্টার প্রকৃত উৎপাদনমূল্য ২০০ টাকা। অর্থাৎ দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করলে তার দৈনিক উৎপাদনমূল্য দাঁড়ায় ১৬০০ টাকা এবং মাসে প্রায় ৪৮ হাজার টাকা। অথচ বাস্তবে তাকে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার মতো মজুরি। অর্থাৎ প্রায় ৩৬ হাজার টাকা মালিকের কাছে উদ্বৃত্ত হিসেবে থেকে যায়। এই উদ্বৃত্তের কারণেই বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার কিংবা ভিয়েতনামের তুলনায় কম দামে পোশাক রপ্তানি করতে সক্ষম হয়।
এখন প্রশ্ন হলো, যদি কর্মঘণ্টা অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয় এবং মজুরি ভাগ করে সরকার ৬ হাজার ও মালিক ৬ হাজার টাকা দেয়, তাহলে কী হবে। প্রথমত, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে মালিকের সরাসরি উৎপাদন ক্ষতি হবে প্রায় ১৮ হাজার টাকার সমপরিমাণ। কারণ অর্ধেক সময় কাজ মানে অর্ধেক উৎপাদন। অথচ বাজারে তাকে একই সময়ের মধ্যে একই পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতে হবে।
কিন্তু সমস্যাটি শুধু এখানেই শেষ নয়। অর্ধেক কর্মঘণ্টা মানে সামগ্রিক উৎপাদন সক্ষমতার একটি বড় ধস। গার্মেন্টস শিল্প আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনের সঙ্গে যুক্ত। এখানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে ক্রেতারা অপেক্ষা করে না। তারা বিকল্প দেশ খোঁজে। একবার কোনো দেশ সরবরাহে অনিয়মিত হয়ে পড়লে সেই বাজার পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়।
আরেকটি মৌলিক বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প মূলত এসেম্বলি লাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখানে উৎপাদন একটি সমন্বিত শৃঙ্খলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। একজন শ্রমিক অনুপস্থিত থাকলেও পুরো চেইন ব্যাহত হয়। ধরুন, ৫০০ শ্রমিকের একটি কারখানায় মাত্র ১০ জন শ্রমিক অর্ধেক সময় কাজ করল। এর প্রভাব পড়বে পুরো ৫০০ জনের উৎপাদন সক্ষমতার ওপর। সময়মতো কাজ শেষ না হওয়ায় পুরো ব্যাচের ডেলিভারি ঝুঁকিতে পড়বে। কোনো মালিকই এমন অনিশ্চয়তা নিতে চাইবে না।
এই বাস্তবতা থেকে একটি অনিবার্য সিদ্ধান্ত আসে: মালিকরা ধীরে ধীরে নারী শ্রমিক নিয়োগে নিরুৎসাহিত হবে। বিশেষ করে যাদের সন্তান আছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি বলে বিবেচিত হবে। ফলাফল হিসেবে এই নীতির উদ্দেশ্য যেখানে নারীদের সুরক্ষা দেওয়া, বাস্তবে সেখানে নারীরাই শ্রমবাজার থেকে ছিটকে পড়বে।
এখানে একটি বড় বিভ্রান্তি কাজ করছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে, সরকার এই বাড়তি মজুরি বহন করতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন অর্থ দিয়ে। বাংলাদেশের বাজেট কাঠামো ইতোমধ্যেই উচ্চ ভর্তুকি, ঋণনির্ভরতা ও রাজস্ব ঘাটতিতে জর্জরিত। লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিকের অর্ধেক মজুরি সরকার বহন করলে বছরে অতিরিক্ত হাজার হাজার কোটি টাকার বোঝা তৈরি হবে। সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে। কর বাড়িয়ে? ভর্তুকি কেটে? নাকি আরও বিদেশি ঋণ নিয়ে।
অর্থনৈতিক বাস্তবতা হলো, রাষ্ট্র কোনো উৎপাদন না করে দীর্ঘমেয়াদে মজুরি ভর্তুকি দিতে পারে না। এটি করলে একদিকে মূল্যস্ফীতি বাড়বে, অন্যদিকে অন্যান্য সামাজিক খাতে ব্যয় সংকুচিত হবে। অর্থাৎ এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরও বড় সমস্যার জন্ম দেওয়া হবে।
সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, এই প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। পুরুষ শ্রমিকরা এত কম মজুরিতে কাজ করতে আগ্রহী নয়। নারী শ্রমিকরা যদি ধীরে ধীরে শিল্প থেকে বাদ পড়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ তার প্রতিযোগিতামূলক শ্রম সুবিধা হারাবে। ফলস্বরূপ বাজার চলে যাবে ভারত, ভিয়েতনাম কিংবা অন্যান্য দেশে। দেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস কার্যত অচল হয়ে পড়বে এবং এর প্রভাব পড়বে পুরো অর্থনীতির ওপর। একটি ইতোমধ্যেই ভঙ্গুর অর্থনীতি মারাত্মক ধাক্কা খাবে।
এখানেই প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি অবাস্তব ও অর্থনৈতিকভাবে আত্মঘাতী প্রস্তাব কীভাবে একটি বড় রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে জায়গা পায়। এর উত্তর সম্ভবত রাজনৈতিক পপুলিজম। আবেগঘন স্লোগান, নৈতিকতার মোড়ক ও বাস্তবতা-বিবর্জিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা কোনো নৈতিক বক্তৃতার মঞ্চ নয়; এটি একটি জটিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।
নারীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও শিশুযত্ন সুবিধা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে শিল্পের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন, কার্যকর ডে-কেয়ার, পর্যাপ্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধির পথ তৈরি করা। কর্মঘণ্টা অর্ধেক করে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির ওপর দাঁড় করানো কোনো টেকসই সমাধান নয়।
নীতিনির্ধারণ আবেগ দিয়ে নয়, বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক কাঠামো বোঝার ভিত্তিতেই করতে হয়। অন্যথায়, ভালো উদ্দেশ্যের নামে নেওয়া সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সমাজ ও অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ডেকে আনে।
ইসলামোফোবিয়া: বাংলাদেশে বাস্তবতার নাম, না রাজনৈতিক ঢাল

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
বাংলাদেশে “ইসলামোফোবিয়া” শব্দটা বহু সময় বাস্তবতা বোঝানোর জন্য নয়, রাজনীতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। শব্দটা উচ্চারণ করলেই এক ধরনের নৈতিক ঢাল পাওয়া যায়। আপনি যদি জামায়াত বা অন্য কোন রাজনৈতিক বর্গ যেমন হারুন ইজহারদের সমর্থকদের ইতিহাস, ধর্মকে শাসনের প্রকল্প বানানো, বা কট্টর রাজনীতির সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, সেটাকে সহজে “ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ” বানিয়ে দেওয়া যায়। তখন যুক্তির জবাব দিতে হয় না। ব্যক্তির কাজ কিংবা দলের রাজনৈতিক দায় নিয়ে কথা না বলে পরিচয়ের মামলা দাঁড় করানো যায়। আর পরিচয়ের মামলায় কথা বলা কঠিন, কারণ কেউই “ধর্মবিদ্বেষী” তকমা নিতে চায় না। ফলে সমালোচনার জায়গা সংকুচিত হয়, বিতর্কটা আবেগের দিকে সরে যায়, এবং একটি দল নিজেকে “বিপন্ন মুসলমানদের প্রতিনিধি” হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।
এই কৌশলের আরেকটা সুবিধা আছে, যেটা আরও গভীর। আইনশাসনের অভাব, গোয়েন্দা রিপোর্টের নামে নিয়োগে বৈষম্য, নিরাপত্তার নামে হয়রানি, অথবা মিডিয়ায় দাড়ি-টুপি নিয়ে স্টেরিওটাইপিং, এগুলো আসলে আলাদা আলাদা সমস্যা। প্রতিটির আলাদা দায় আছে, আলাদা সমাধান আছে। কিন্তু সবকিছুকে “ইসলামোফোবিয়া” বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললে দায়টা ঝাপসা হয়ে যায়। সবকিছু মিশে গিয়ে “সেকুলার শক্তি” নামে একটা অস্পষ্ট শত্রু তৈরি হয়। অস্পষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে কথা বলা সহজ, কিন্তু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত, নির্দিষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। তাই ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এক শব্দে সব ধরতে, জবাবদিহির চাপ কমাতে, সমর্থকদের সামনে একটা সরল গল্প দাঁড় করিয়েছে: "আমরা আক্রান্ত, তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশে ইসলামফবিয়া চরম ভাবে আছে"।
আসুন এই ফ্রেমটিকে প্রশ্ন করি, ক্রিটিকালি দেখি। এই ফ্রেম বুঝতে হলে আগে দুটো জিনিস আলাদা করা জরুরি। একদিকে আছে কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া, যেখানে রাষ্ট্রের আইন, নীতি, নিয়োগব্যবস্থা, নিরাপত্তা কাঠামো এমনভাবে সাজানো থাকে যে মুসলমান পরিচয়টাই ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে আছে সামাজিক ইসলামোফোবিয়া বা ধর্মচর্চা-বিদ্বেষ, যেখানে পোশাক, দাড়ি-টুপি, হিজাব, মাদ্রাসা শব্দটাই উপহাসের বস্তু হয়, এবং ধর্মীয় সিম্বল দেখলেই মানুষকে অগ্রিম “পিছিয়ে পড়া” বা “বিপজ্জনক” ধরে নেওয়া হয়। ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই দাবি করে বাংলাদেশে দুটোই “চরম” আকারে আছে, এবং এর জন্য দায়ী দেশীয় “সেকুলার এলিট”। আর এই “সেকুলার এলিট”-এর মধ্যে ধীরে ধীরে সবাই পড়ে, যারা ইসলামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা করবে। আগে এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পড়ত, এখন এর মধ্যে বিএনপিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, যে-ই ইসলামপন্থী রাজনীতির বিরোধী, সে-ই সম্ভাব্য “সেকুলার এলিট”। রাজনীতিতে এর থেকে শক্তিশালী ফ্রেম হতেই পারে না। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় দেখলে এই দাবিটা অনেক সময় ভুল জায়গায় দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে মুসলমান পরিচয়ের ভিত্তিতে ধারাবাহিক কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া ছিল, এমন শক্ত প্রমাণ হাজির করা কঠিন। বরং যা বেশি দেখা গেছে, তা হলো রাজনৈতিক পরিচয়ভিত্তিক সেগ্রিগেশন, ক্ষমতার আনুগত্য যাচাই, আর নিরাপত্তাকরণের নামে ধর্মীয় পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র এখানে মুসলমান পরিচয়কে শত্রু হিসেবে দেখেছে, এমন নয়। রাষ্ট্র দেখেছে বিরোধিতার সম্ভাবনা, এবং সেটাকে দমাতে গিয়ে ধর্মীয় প্রতীককে শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যটা ধরতে না পারলে আমরা সমস্যার নাম ভুল করি, আর নাম ভুল হলে সমাধানও ভুল দিকে যায়।নিয়োগের কথাই ধরা যাক। গত এক দশকে বাংলাদেশের বহু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় “গোয়েন্দা রিপোর্ট”, রাজনৈতিক আনুগত্য, দলীয় নেটওয়ার্ক, এবং “ঝুঁকিপূর্ণ পরিচয়” শনাক্ত করার প্রবণতার কথা শোনা গেছে। অনেকে বলেছেন, মাদ্রাসায় পড়েছে বলে বা দাড়ি-টুপি রাখে বলে চাকরিতে বাধা এসেছে। এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু বিশ্লেষণটা “কারা বাধা পেল” থেকে “কী যুক্তিতে বাধা পেল” দিকে সরালে অন্য ছবি দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল পরিবারের জামায়াত সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, বিএনপি-ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আছে কি না, ক্যাম্পাস রাজনীতিতে শিবির বা বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিচয় নয়, রাজনৈতিক পরিচয় এবং সম্ভাব্য বিরোধিতার আশঙ্কাই ছিল মূল ফ্যাক্টর।
সমস্যাটা কোথায়? রাজনৈতিক স্ক্রিনিং যখন হয়, বাস্তবে ধর্মীয় চেহারার মানুষ বেশি ভোগে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে দৃশ্যমান ধর্মীয় প্রতীকের সঙ্গে জুড়ে গেছে। ফলে দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, মাদ্রাসা শিক্ষা, এগুলো অনেক সময় “রাজনৈতিক সন্দেহ”র শর্টকাট হয়ে ওঠে। একজন নির্দোষ মাদ্রাসা ছাত্রও সেই সন্দেহের আওতায় পড়ে। ক্ষতিটা বাস্তব। কিন্তু এটাকে ইসলামোফোবিয়া বললে ভুলটা হয় এই জায়গায় যে “ধর্মচর্চা” আর “রাজনৈতিক ইসলাম” একসাথে গুলিয়ে যায়। রাষ্ট্র এবং শহুরে মধ্যবিত্ত পরিসর অনেক সময় ইসলামকে নয়, ইসলামকে শাসনের প্রকল্প বানানো নেটওয়ার্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। সেই নিয়ন্ত্রণের পথে ডিউ প্রসেস ভেঙেছে, সন্দেহ প্রমাণে পরিণত হয়েছে, এবং নির্দোষ মানুষও ভুগেছে। কিন্তু এটাকে ধর্মবিদ্বেষ বলে ধরলে মূল অপরাধী, অর্থাৎ পার্টি-স্টেটের কর্তৃত্ববাদী প্রক্রিয়া আড়াল হয়ে যায়। তখন প্রতিষ্ঠান, নীতি, পুলিশিং, নিয়োগ প্রক্রিয়া, এগুলোর জবাবদিহির বদলে আমরা “ধর্মীয় অনুভূতি”র ধোঁয়ায় ঢুকে পড়ি।
একই ভুল পাঠ দেখা যায় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাতেও। মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বা নাটকে রাজাকার চরিত্রকে দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি পরানো, তাকে ধর্মীয় সিম্বল দিয়ে “চিহ্নিত” করা নিয়ে অভিযোগ ওঠে যে এটি ধর্মচর্চাকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি করছে। এখানে দুটো সত্য পাশাপাশি আছে। পপুলার কালচার শর্টকাট ব্যবহার করে; ভিজুয়াল কোডিং করে; খলনায়ক দেখাতে দ্রুত কিছু প্রতীক ধরে। বাংলাদেশে দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবি বহু বছর ধরে শুধু ধর্মীয় সিম্বল নয়; এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্মৃতি এবং রাজনৈতিক ঘরানার সাংস্কৃতিক চিহ্নও। বিশেষ করে যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা আসে তখন জামাত নেতাদের মিডিয়ায় উপস্থাপন করতে দাড়ি টুপি ব্যাবহার হয়। আপনি যদি বাস্তবে দেখেন জামাতের যে নেতারা সেই সময় পাকিস্তান আর্মির সাথে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল তাদের প্রায় সবারই তো দাড়ি ছিল ও টুপি পরতেন। এখন তাদের কি শেভ করে উপস্থাপন সম্ভব? বাস্তবতা হল, যুদ্ধাপরাধের বিচার, জামায়াতের ভূমিকা, ৭১ পরবর্তী ছাত্ররাজনীতি, এগুলোর কারণে এই পোশাক অনেক সময় “রাজাকার-পলিটিক্স” এর শর্টহ্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এতে যত না ধর্মীয় চরিত্র আকারে দেখানো হয় তার থেকে বেশি “রাজাকার-পলিটিক্স” এর সিম্বল আকারে দেখানো হয়ে থাকে।
এই উপস্থাপনাকে “ইসলামোফোবিয়া” বললে অতিরঞ্জন হয়। এখানে বেশি সঠিক হবে বলা: রাজনৈতিক শত্রুকে দেখাতে গিয়ে ধর্মীয় প্রতীককে অলসভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে সাধারণ ধর্মচর্চাকারী মানুষও স্টেরিওটাইপের শিকার হতে পারে। সমালোচনা এখানেই হওয়া উচিত। কারণ সমস্যাটা ইসলাম ঘৃণা নয়, সমস্যাটা অলস ভিজুয়াল রাজনীতি এবং স্মৃতির জটিলতা না মানার অভ্যাস।
শহুরে সমাজে বোরখা বা হিজাব নিয়ে তিরস্কার, “বোরখা মানেই গোঁড়া” টাইপ মন্তব্য, দাড়ি-টুপি দেখে অগ্রিম সন্দেহ, এগুলোও বাস্তব। ( পাশাপাশি সমাজে পশ্চিমা পোশাককে বিশেষ করে যারা ধর্মীয় পোশাক পরেন না তারাও খারাপ মেয়ে বা ছেলে এই সন্দেহের শিকার হয়ে থাকেন। ) কিন্তু এগুলোকে ইসলামোফোবিয়া বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললেও সমস্যা হয়। বাংলাদেশে ইসলাম পাবলিক লাইফের কেন্দ্রে। আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সামাজিক নর্ম, নৈতিকতা নির্মাণ, সবখানেই ইসলামের উপস্থিতি প্রবল এবং বহু জায়গায় মর্যাদাপ্রাপ্ত। কাজেই কিছু স্টিগমা থাকা মানেই “ইসলামবিদ্বেষী সমাজ” নয়। বরং এটা শহুরে মধ্যবিত্তের শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অহংকার, যেখানে ধর্মীয় অনুশীলনের নির্দিষ্ট ধরনকে “গ্রাম্য” বা “ব্যাকওয়ার্ড” আর কিছু ধরনকে "পশ্চিমা" ধরে নেওয়া হয়। এটাকে আমি ইসলামোফোবিয়ার চেয়ে “ক্লাস-কালচার স্টেরিওটাইপ” বলব।
সবচেয়ে কঠিন জায়গা আসে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রেক্ষিতে। ২০০০ দশকের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, ধর্মীয় সংগঠন, এবং ধর্মভিত্তিক নেটওয়ার্কের ওপর নজরদারি, হয়রানি, আটক, নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এখানে কোনো দ্বিধা না রেখে বলা দরকার: বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সীমা লঙ্ঘন করেছে, মানবাধিকারের লঙ্ঘন করেছে। ডিউ প্রসেস ভেঙেছে। সন্দেহকে প্রমাণ বানিয়েছে। নিরাপত্তার নামে নাগরিক অধিকারকে সেকেন্ডারি করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা কি মুসলিম পরিচয়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনীতি? আমার মনে হয় না। কারণ একই রাষ্ট্র একই সময়ে ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারও করেছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়েছে, ধর্মীয় নেতারা অনেক রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়েছেন, আর মাদরাসা বানিয়েছেন, এবং ইসলামকে সংবিধানিক ও সামাজিক পরিসরে স্বাভাবিক অবস্থানেই রেখেছে। এখানে টার্গেট ছিল “সন্ত্রাস” এবং “উগ্রপন্থী নেটওয়ার্ক”। ব্যর্থতা ছিল বড় জালের মতো করে ধর্মীয় পরিসরে জাল ফেলা, যেখানে নির্দোষ মানুষ ধরা পড়ে, আর রাজনৈতিক সুবিধার জন্য “জঙ্গি” তকমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। আর তাই হয়েছে। প্রকৃত সন্ত্রাসী আর রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। আওয়ামীলীগ সরকার হরে দরে সবাইকে জঙ্গি ট্যাগ করেছে। এই অবস্থাকে ইসলামোফোবিয়া বললে মূল ব্যর্থতা, অর্থাৎ আইনশাসনহীন নিরাপত্তা শাসন, আড়াল হয়ে যায়।
এইখানেই ইসলামপন্থী দলগুলোর ইসলামোফোবিয়া-থিসিসটা রাজনৈতিকভাবে লাভজনক ভাষা হয়ে ওঠে। প্রথমত, এটি রাজনৈতিক সমালোচনাকে ধর্মবিদ্বেষে রূপান্তর করে। আপনি যদি যুদ্ধাপরাধ, সহিংস ছাত্ররাজনীতি, বা ধর্মকে শাসনের প্রকল্প বানানোর সমালোচনা করেন, তারা বলবে আপনি ইসলামোফোবিক। বিতর্কের কেন্দ্রে রাজনীতি থাকে না, অনুভূতি এসে বসে। দ্বিতীয়ত, তাদের নিজেদের ভেতরের কঠিন প্রশ্ন, ক্ষমতা, নারী অধিকার, সংখ্যালঘু, ভিন্নমত সহনশীলতা, এগুলো চাপা দেওয়া সহজ হয়। তৃতীয়ত, বাস্তব সামাজিক স্টিগমাকে রাজনৈতিক পুঁজি বানানো যায়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ আর শ্রেণিভিত্তিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলকে তারা “সেকুলার বনাম ইসলাম” যুদ্ধ বানিয়ে দেয়।তাই বাংলাদেশে ইসলামোফোবিয়া আছে কি না, প্রশ্নটা হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর করা সহজ নয়। সামাজিক স্তরে কিছু স্টেরিওটাইপ আছে। নিরাপত্তা নীতির ভেতর ধর্মীয় পরিসরের ওপর অতিরিক্ত সন্দেহ এবং দমনও আছে। কিন্তু ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যে অর্থে বলেন, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজ মুসলমান পরিচয়কে কাঠামোগতভাবে টার্গেট করছে, সেই অর্থে বাংলাদেশকে ইসলামোফোবিক রাষ্ট্র বলা টেকে না। বাংলাদেশের বাস্তবতা বরং উল্টো দিকে টানে। এখানে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয়, পাবলিক লাইফের কেন্দ্রীয় নর্ম। এখানে বঞ্চনার বড় চালিকা শক্তি ছিল রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্ন, এবং নিরাপত্তাকরণের নামে বিরোধী সম্ভাবনাকে দমন করার প্রবণতা। আর সামাজিক স্তরের হেয় করার ঘটনাগুলোকে ইসলামোফোবিয়া বলে এক শব্দে বেঁধে ফেললে আমরা সমস্যার সঠিক নাম হারাই।এই কারণেই আমি “ইসলামোফোবিয়া” বেশি সুনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহার করতে চাই, ডানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক প্রকল্পকে প্রশ্ন করতে চাই। চাকরি থেকে বঞ্চনা হলে বলব রাজনৈতিক বৈষম্য এবং পার্টি-স্টেটের লয়্যালটি টেস্ট। নিরাপত্তার নামে নির্যাতন হলে বলব ডিউ প্রসেস ভাঙা, আইনশাসনের ব্যর্থতা, নিরাপত্তা শাসনের স্বেচ্ছাচার। মিডিয়ায় দাড়ি-টুপি মানেই খলনায়ক হলে বলব সাংস্কৃতিক স্টেরিওটাইপিং এবং রাজনৈতিক প্রতীকের অপব্যবহার। কারণ নাম ঠিক থাকলে দায় ঠিক থাকে। দায় ঠিক থাকলেই সমাধান ধর্মীয় আবেগের নাটকে আটকে না থেকে নাগরিক অধিকারের বাস্তব রাজনীতিতে দাঁড়াতে পারে।
ব্যক্তিগত দায় বনাম প্রাতিষ্ঠানিক দায়: দায়মুক্তির এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আসিফ বিন আলী
শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের ঘটনা কাগজে পড়লে প্রথমে মনে হয় এটা যেন কোনো যুদ্ধের খবর। এক তরুণকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা প্রায় কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটা যুদ্ধ না, আমাদের এক সাধারণ গ্রাম। আর হামলাকারীও কোনো অজানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয়, অভিযোগ আছে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।
সুফিয়ানের অপরাধ কী? পরিবারের অভিযোগ, এক স্বজন কিশোরীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করেছিল সে। অর্থাৎ সে আসলে এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা শোনার বদলে কিছু লোক তাকে খুঁটিতে বেঁধে এমনভাবে কুপিয়েছে যে তার দুই হাত ও এক পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনা শুধু একটি বর্বর হামলার খবর না, এটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও আয়না।
ঘটনার পর আমরা দেখি পরিচিত চিত্র। শিবগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির সাদিকুল ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন, “কে বা কারা রাতের আঁধারে এ ঘটনা ঘটিয়ে জামায়াতের ওপর দোষ চাপাচ্ছে… জামায়াতের জড়িত থাকার প্রশ্নই আসে না।” স্থানীয় যে দুই জনের নাম উঠেছে, শাহ আলম ও আবদুর রাজ্জাক, তাদের তিনি দলের কর্মী হিসেবে মানেন, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। অর্থাৎ লোকগুলো জামায়াতের, কিন্তু কাজটি নাকি জামায়াতের না।
আমরা এই একই নাটক অন্য জায়গাতেও দেখেছি। উদীচী, ছায়ানট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমে হামলার আগে–পরে অনেক ছাত্রনেতা, বিশেষ করে ডাকসু, রাকসু, জাকসু আর শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু নেতা প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে। ফেসবুক লাইভে, মাইক হাতে মিছিলে তারা নাম–ধাম বলে বলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে, “ঘেরাও করতে হবে”, “শাস্তি দিতে হবে” ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে। কিন্তু হামলার পর যখন সমালোচনা শুরু হয়, মামলা হয়, আন্তর্জাতিক মহলেও খবর যায়, তখন হঠাৎ সব পাল্টে যায়। তখন শিবিরের প্রেস রিলিজ আসে, যেখানে বলা হয়, যারা উসকানিমূলক কথা বলেছে তারা নাকি “ব্যক্তিগতভাবে” বলেছে, দলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রনেতারা তখন বলেন, “আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে”, “আমি শুধু প্রতিবাদের কথা বলেছি”, “হামলার কথা বলিনি” ইত্যাদি।শিবগঞ্জের ঘটনার পরও আমরা একই কৌশল দেখি। লোকগুলো জামায়াতের সভা–সমাবেশে যায়, ব্যানারে থাকে, দলের নেতা–কর্মী হিসেবে পরিচিত; কিন্তু হামলার প্রশ্ন এলে সঙ্গে সঙ্গে দল বলে, “এরা কোনো দুষ্টচক্রের টার্গেট”, “নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতকে ফাঁসানো হচ্ছে।” এই জায়গাটাই আসল সমস্যা। জামায়াত ও শিবির একদিকে সংগঠিতভাবে রাজনীতি করবে, ধর্মের নামে জনমত তৈরি করবে, কর্মীদের নানা পদে বসাবে, আবার সহিংসতা বা সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠলেই সব দায় একেকটা ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেবে। দল সুবিধা নেবে, কিন্তু দায়িত্ব নেবে না।এই “ব্যক্তিগত দায়–দল দায়ী নয়” যুক্তি আসলে রাজনৈতিক পালানোর পথ। একটা সংগঠন যদি দাবি করে তার কর্মীরা খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ, আদর্শবান, কোরআন–হাদিসভিত্তিক জীবন চালায়, তাহলে সেই সংগঠনকেই প্রথমে আত্মসমালোচনা করতে হয় যে কেন তার কর্মীরা এমন ভয়াবহ সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। যদি সত্যি দলের ভূমিকা না থাকে, তাহলে দলই আগে এগিয়ে এসে তদন্ত দাবি করবে, ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়াবে, নিজেদের কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। বাস্তবে আমরা দেখি উল্টো ছবি: ভুক্তভোগীর বদলে অভিযুক্ত কর্মীদের সাফাই গাওয়া হয়, ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বানানো হয়, আর সবকিছুর জন্য “অজ্ঞাত” তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করা হয়।
এর মাধ্যমে কয়েকটা কাজ একসঙ্গে হয়। প্রথমত, কর্মীরা বুঝে যায় যে দল তাদের আড়াল করবে, ফলে সহিংসতা চালাতে তাদের ভয়ের মাত্রা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, দলের একটা “পরিষ্কার” ইমেজ তৈরির চেষ্টা চলে, যেন তারা মূলত শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দল, কিছু “উৎসাহী” ব্যক্তি মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, দলের তাতে কিছু করার নেই। তৃতীয়ত, আইন ও বিচারব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়, যাতে মামলা গায়ে লাগে না, রাজনৈতিক চাপও কম থাকে। এর ফল কী দাঁড়ায়? ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে ন্যায়বিচার দূরের স্বপ্ন হয়ে যায়। সুফিয়ানের মতো মানুষ সারাজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, আর যারা তাকে খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটেছে, তারা হয় “অজ্ঞাত লোক”, না হয় “ব্যক্তিগতভাবে ভুল করে ফেলা” কিছু মানুষ। সংগঠন থাকে নিরাপদে, আবার পরদিন একই ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে।
জামায়াত–শিবিরের রাজনীতি অনেক দিন ধরে এই দুই মুখে চলে আসছে। এক মুখে তারা নিজেদের “গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয়, ইসলামী” দল হিসেবে পরিচয় দেয়, ভোট চায়, মানবাধিকার আর ন্যায়বিচারের কথা বলে। আরেক মুখে মাঠের কর্মীদের মাধ্যমে তারা টার্গেট নির্ধারণ করে, কাদের “শাস্তি” দিতে হবে, কারা “ইসলামের শত্রু”, কারা “দেশদ্রোহী” – এসব ন্যারেটিভ ছড়ায়। পরে সেই ন্যারেটিভ বাস্তব হামলায় পরিণত হলে তারা বলে, “আমরা তো কাউকে কুপাতে বলিনি, আমরা শুধু কথা বলেছি।” এই দ্বিচারিতা দীর্ঘমেয়াদে শুধু প্রতিপক্ষের জন্য না, দেশের সব নাগরিকের জন্যই বিপজ্জনক। কারণ এতে একটি বার্তা স্পষ্ট হয়: সংগঠিত শক্তি সহিংসতার ভাষা ব্যবহার করতে পারে, কর্মীরা সেই ভাষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে, আর কোনো প্রতিষ্ঠানই তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারবে না। তখন রাজনীতি আর মতের লড়াই থাকে না; রাজনীতি হয়ে যায় ভয় দেখানোর খেলা।
আমার মনে হয়, সময় এসেছে এই খেলাটা স্পষ্ট করে ডেকে নাম ধরেই চেনার। যদি কোনো দলের কর্মীরা বারবার সহিংসতায় জড়ায়, যদি সেই দলের নেতারা নিয়মিতভাবে উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করেন, আর পরে প্রেস রিলিজ দিয়ে সব দায় “ব্যক্তিগত” বলে উড়িয়ে দেন, তাহলে সেখানে শুধু ব্যক্তিগত অপরাধের কথা বলে লাভ নেই। সেখানে সংগঠনগত দায়ের কথাও উঠবে, উঠতেই হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে না। জামায়াত–শিবির বা অন্য যে কোনো দলের ক্ষেত্রেই কথা একই: সংগঠন যদি সুবিধা নিতে পারে, তবে সংগঠনকেও দায়িত্ব নিতে হবে। আর রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে এই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়া, যাতে আর কোনো সুফিয়ানকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটে ফেলা না যায়, এবং কোনো সংগঠন তা “ব্যক্তিগত ভুল” ও "রাতের আঁধারের ঘটনা" বলে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে।
নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণ: বাংলাদেশে অবহেলিত এক সহিংসতার সংকট
.jpg)
ড. রাসেল হোসাইন ও ড. আনিসুর রহমান খান
শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের ঘটনা একটি গভীর উদ্বেগজনক সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ঘটনাগুলো সাধারণত পারিবারিক পরিসরে সংঘটিত হলেও এর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধ্বংসাত্মক। সাম্প্রতিক সময়ে জার্নাল অফ সাইকোসেক্সুয়াল হেলথ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য উদ্যোগ, আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতার একটি চরম ও নজরদারিহীন রূপকে সামনে এনেছে।
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে দেশে পুরুষের যৌনাঙ্গ বিচ্ছেদের ৪৩টি ঘটনা ঘটেছে এবং সব ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ছিলেন নারী। সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ৭০ শতাংশ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ওপর সহিংসতা চালিয়েছেন তাঁদের স্ত্রী। বাকি ঘটনাগুলোতে অপরাধী ছিলেন নিকটাত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে থাকা সঙ্গী যেমন বান্ধবী, অথবা সাবেক স্ত্রী। এই সহিংসতার প্রধান কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে পরকীয়া, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, যা মোট ঘটনার ৬৭.৪ শতাংশ। পাশাপাশি পারিবারিক ঝগড়া, প্রত্যাখ্যান, প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষার দাবি থেকেও এমন সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের চেষ্টার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এ ধরনের আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে চলমান তীব্র উত্তেজনা ও ভাঙনের ইঙ্গিত বহন করে।
ভুক্তভোগীদের সামাজিক প্রোফাইলও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ ভুক্তভোগীর বয়স ছিল ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। তাঁদের প্রায় ৭৪.৪ শতাংশ বিবাহিত এবং বেশিরভাগই নিম্ন আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আসা শ্রমিক, পোশাকশ্রমিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতের উপার্জনকারী। আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর আঘাত হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও ৫৮ শতাংশ ঘটনায় কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর পেছনে সামাজিক কলঙ্কের ভয়, পারিবারিক চাপ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যেহেতু বৈবাহিক সঙ্গী এই বাস্তবতা বড় ভূমিকা রেখেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ৬৩.৬ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়, যেখানে আইনি সহায়তা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত সীমিত। প্রায় ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ভুক্তভোগীদের আজীবন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি বহন করতে হয়েছে। অন্তত দুটি ঘটনায় মৃত্যুর তথ্যও পাওয়া গেছে।
এই গবেষণার ফলাফল একটি প্রায় অদৃশ্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরনকে উন্মোচিত করে, যা অবিলম্বে আইনি, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যগত মনোযোগ দাবি করে। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা মনে করি, এই সহিংসতা বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো ও লিঙ্গগত সম্পর্কের গভীর কাঠামোগত সংকটের প্রতিফলন। অর্থনৈতিক চাপ, অপূর্ণ বৈবাহিক প্রত্যাশা, বহুবিবাহ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ঘাটতি দাম্পত্য উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সামনে আসে, সহিংসতার আলোচনায় পুরুষ কোথায়।
বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের কথা শুনলে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন, কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও চান না। পরিসংখ্যানের বিচারে ঘটনাগুলো সংখ্যায় কম মনে হতে পারে, কিন্তু এর সামাজিক বার্তা ভয়াবহ। দাম্পত্য সম্পর্কে অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও টানাপোড়েন মিলিয়ে এক নীরব সংকট তৈরি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পুরুষ ভুক্তভোগীরা লজ্জা ও সামাজিক প্রত্যাশার চাপে মুখ খুলতে পারেন না। আমাদের সমাজে পুরুষ মানেই শক্ত, ব্যথা বা লজ্জা নেই, এই ধারণা তাঁদের নীরব করে রাখে। এর ফল হিসেবে গুরুতর অপরাধও আইনের আওতার বাইরে থেকে যায়। এই নীরবতার মূল্য দিতে হয় পরিবারকে, সন্তানকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।
এই বাস্তবতায় বাংলাদেশকে জেন্ডার-নিউট্রাল গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, দাম্পত্য কাউন্সেলিং এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণকে জাতীয় অগ্রাধিকারে আনতে হবে। দাম্পত্য সহিংসতা নারী বা পুরুষ কাউকেই ছাড়ে না। তাই সমস্যাটি স্বীকার করাই সমাধানের প্রথম ধাপ। সহিংসতা লুকিয়ে নয়, বরং তা স্বীকার করে, বোঝে এবং প্রতিরোধ করেই সমাজকে মানবিক করা সম্ভব।
আমাদের দৃষ্টিতে, এই ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় বহুস্তরের সরকারি প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। প্রথমত, আইনি ও বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। যৌনাঙ্গের ক্ষতির প্রতিটি ঘটনায় বাধ্যতামূলক তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার মামলার জন্য দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পারিবারিক সহিংসতা আইন সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেয়।
দ্বিতীয়ত, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা জোরদার করা জরুরি। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে বৈবাহিক সহিংসতার শিকার পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সংকটকালীন পরামর্শ বিভাগ চালু করতে হবে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের উচ্চঝুঁকিপূর্ণ দাম্পত্য দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পারিবারিক ও বিবাহ পরামর্শ সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
তৃতীয়ত, সামাজিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রটি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এনজিও ও স্থানীয় সরকার যৌথভাবে বিয়ের আগে ও পরে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি চালু করতে পারে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সহিংসতার শিকার পুরুষদের প্রতি সামাজিক কলঙ্ক মোকাবেলার প্রচারণা এবং বহুবিবাহ-সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উপযুক্ত আইনি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
চতুর্থত, দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কভারেজ নিশ্চিত করা জরুরি। যৌনাঙ্গে আঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগীদের লজ্জা ও মানসিক ক্ষতি কমে। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা ও চাঞ্চল্যকর উপস্থাপন পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন অনেক সময় ভুক্তভোগীদের মামলা চালাতে নিরুৎসাহিত করে।
সবশেষে, লিঙ্গ শিক্ষা ও দ্বন্দ্ব সমাধান বিষয়ে জোর দিতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, সম্মতি শিক্ষা এবং সুস্থ সম্পর্ক গঠনের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।
লক্ষণীয় যে, পুরুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গকে লক্ষ্য করে সংঘটিত সহিংসতা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার কারণে প্রায় আলোচনার বাইরে থাকে। এখানে প্রতিযোগিতামূলক অভিযোগ নয়, বরং সকল ধরনের আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলায় সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু পুরুষের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রটি প্রায় উপেক্ষিত। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে পুরুষ ভুক্তভোগীরা নীরবে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে এবং ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার গভীর কারণগুলো যেমন লিঙ্গ বৈষম্য, দুর্বল আইনি সহায়তা এবং তীব্র বৈবাহিক চাপ অমীমাংসিতই থেকে যাবে।
লেখক-
ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ড. আনিসুর রহমান খান, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
পাঠকের মতামত:
- যাকাত দিয়েই দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনা: নতুন উদ্যোগের কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী
- আমরা বিশ্বের উপকার করছি! ইরানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ট্রাম্পের বিতর্কিত দাবি
- কুমিল্লায় কাঁচাবাজার পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী
- মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশে: জ্বালানি বিপর্যয় রুখতে ডা. শফিকের ৩ দফা পরামর্শ
- আল ধাফরা ও ফিফথ ফ্লিটে ইরানের বিধ্বংসী আঘাত; মার্কিন সেনাদের বড় বিপর্যয়
- নারীর সমান অধিকারই হবে আগামীর বাংলাদেশের ভিত্তি: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
- খামেনি পরবর্তী ইরানের হাল ধরবেন কে? দ্রুত ঘোষণার দাবি শীর্ষ দুই আয়াতুল্লাহর
- হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তছনছ মার্কিন ঘাঁটি
- আত্মসমর্পণ নাকি রণকৌশল? ট্রাম্পের দাবি ও ইরানের পাল্টা হামলার রহস্য কী?
- সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে জাদুর মতো কাজ করবে এই ৫টি প্রাকৃতিক পানীয়
- প্রতিবেশীদের ওপর আর হামলা নয়, হঠাৎ নমনীয় সুর ইরানি প্রেসিডেন্টের!
- ইফতারে পুষ্টিকর ও মুখরোচক ভেজিটেবল কাটলেট: সহজ রেসিপি
- তেল সংকটের গুজব নিয়ে সতর্কবার্তা: আতঙ্কে পাম্পে ভিড় না করার আহ্বান প্রতিমন্ত্রীর
- রমজান ও ঈদে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে: ইশরাক হোসেন
- ইফতারে চিনির শরবত নাকি গুড়ের? কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশি নিরাপদ?
- ব্রিটেনে মার্কিন বোমারু বিমান, ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিল লন্ডন
- মার্কিন হামলার হুমকির মাঝেই কাঁপল ইরান: ভূমিকম্প নাকি পরমাণু পরীক্ষা?
- প্রতিবেশী দেশে হামলা করা নিয়ে ইরানের নতুন সিদ্ধান্ত
- ইরান হামলার পর ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষোভ: ওয়াশিংটনের সঙ্গে দূরত্বের দাবি জোরালো
- মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত তীব্রতর: লেবাননে ১২ নিহত, ইরানে নতুন হামলা
- আত্মগোপন থেকে ফিরেই আলভীর বোমা: ইকরার মৃত্যু ও ‘দ্বিতীয় বিয়ে’ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি
- ইফতারে মুখরোচক চিকেন কিমা তাওয়া কাবাব: সহজ ঘরোয়া রেসিপি
- ভোট কারচুপি না হলে প্রতিপক্ষ এত ভোট পেত না: মির্জা আব্বাস
- আপসহীন সংগ্রামের স্বীকৃতি: অদম্য নারী পুরস্কারে ভূষিত প্রয়াত খালেদা জিয়া
- ভাড়া বাসায় চলত জাল নোটের কারবার, গোয়েন্দা জালে ধরা কারিগর
- সৌদি আরবের তেলের খনিতে ইরানের ড্রোন হামলা
- আজ রাতেই ইরানে ইতিহাসের বৃহত্তম বোমাবর্ষণের আলটিমেটাম
- রোববার থেকে দেশে চালু হচ্ছে নতুন নিয়মে তেল বিক্রি
- আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: জেনে নিন কোন দেশের মুদ্রার কত দাম
- তেহরানের আকাশে কালো ধোঁয়া: বিমানবন্দরের ভেতরে জ্বলছে সারিবদ্ধ বিমান
- আপস না করাই আজ নিজের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে: আসিফ মাহমুদ
- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- ১৭ রমজান: যে যুদ্ধে নির্ধারিত হয়েছিল ইসলামের আগামীর বিশ্বজয়
- শনিবারে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের ব্যস্ত সূচি: টিভিতে আজকের খেলা
- মধ্যপ্রাচ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ: বিশ্ব অর্থনীতিতে চরম অস্থিরতার সংকেত
- বিশ্ববাজারে উত্তেজনা থাকলেও দেশের বাজারে কমলো স্বর্ণের দাম
- কোনটি প্রমাণিত হয়েছে?—দুর্নীতি ইস্যুতে মধ্যরাতে হাসনাতের বিস্ফোরক প্রশ্ন
- আজ ৭ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে যেসব এলাকা
- শনিবার ০৭ মার্চ: ৫ ওয়াক্ত নামাজের সঠিক সময় ও গুরুত্ব
- “প্রায় সীমাহীন অস্ত্র মজুত” দাবি, তবু উৎপাদন বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের
- বাহরাইনে ইসরায়েলি দূতাবাসে ইরানের ড্রোন হামলা
- ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট: আজ মিলছে ১৬ মার্চের আসন
- মৃত্যুপুরী তেহরান: মহামারির চেয়েও ভয়ংকর নীরবতা
- সংহতির বার্তা নাকি কৌশলী কূটনীতি? প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমিরাতের প্রেসিডেন্টের বিশেষ আলাপ
- অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টা বাংলার নতুন মীরজাফর: মো. তাহের
- বিক্ষোভ দমন ও নিষেধাজ্ঞা: বিতর্ক সঙ্গী করেই ইরানের সামরিক কমান্ডে আহমদ বাহিদি
- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- বাজার অস্থিরতায় বাজুসের বড় সিদ্ধান্ত: কমেছে স্বর্ণ ও রুপার দাম
- রাজধানীতে আজ কোথায় কী? এক নজরে দেখে নিন কর্মসূচির তালিকা
- আজকের নামাজের সময়সূচি: ৬ মার্চ ২০২৬
- বাজার অস্থিরতায় বাজুসের বড় সিদ্ধান্ত: কমেছে স্বর্ণ ও রুপার দাম
- বিশ্ববাজারে উত্তেজনা থাকলেও দেশের বাজারে কমলো স্বর্ণের দাম
- ইরান যুদ্ধ, পরিচয়ের রাজনীতি এবং বৈশ্বিক সংকটের নতুন সমীকরণ
- স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড: ভরিতে বাড়ল ৩ হাজার ২৬৬ টাকা
- টানা ছয় দফা বৃদ্ধির পর স্বর্ণের দামে বড় স্বস্তি, নতুন দর কার্যকর আজ
- রোববার থেকে দেশে চালু হচ্ছে নতুন নিয়মে তেল বিক্রি
- স্বর্ণের বাজারে নজিরবিহীন অস্থিরতা; এক বছরে দাম বাড়ল ৬৪ শতাংশ
- ক্ষমতার লড়াইয়ে ইরান: খামেনির আসনে বসতে আইআরজিসি’র চাপ
- মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাবে স্বর্ণের বাজারে আগুন: এক লাফে বাড়ল ৩ হাজার টাকা
- শহীদ হলেন আয়াতুল্লাহ খামেনি
- ২ মার্চ ডিএসই: আজকের শেয়ারবাজার বিশ্লেষণ
- নতুন বেতন কাঠামো ও পে স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে যা জানা গেল
- ইফতারের প্রশান্তি কেড়ে নিচ্ছে মাথাব্যথা? জেনে নিন মুক্তির পূর্ণাঙ্গ গাইড
- রামাদান মাসে কোরানের হাফেজ দের নিয়ে মোস্তফা হাকিম ব্লাড ব্যাংকের সেহেরি আয়োজন
- খামেনি কি বেঁচে আছেন? সাহারা মরুভূমিতে থাকার ছবির আসল সত্য ফাঁস


.jpg)




-100x66.jpg)