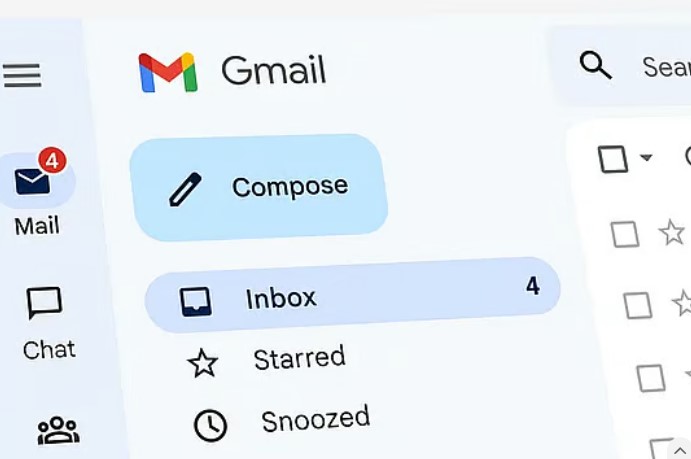বিশেষ প্রতিবেদন
মাহাথির মোহাম্মদ ও মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক রূপান্তর: নীতি, সংস্কার ও উত্তরাধিকার

মো. অহিদুজ্জামান
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

বিশ শতকের শেষভাগে মালয়েশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তরের কৃতিত্ব প্রায়ই মাহাথির মোহাম্মদের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সাহসী নীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৮১ থেকে ২০০৩ এবং পরে আবার ২০১৮ থেকে ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম ২২ বছরের শাসনামলে মাহাথির মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে আধুনিকীকরণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। একটি পণ্যনির্ভর পশ্চাৎপদ অর্থনীতি থেকে এটিকে রূপান্তরিত করেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে গতিশীল উদীয়মান শিল্প অর্থনীতির একটিতে।
তিনি জাতীয় উন্নয়নের জন্য উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি হাতে নেন। এর মধ্যে ছিল Look East Policy, Vision 2020 এবং বিশাল অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ। তিনি প্রচলিত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে দ্বিধা করেননি। ১৯৯৭ সালের এশীয় আর্থিক সংকটে আইএমএফ-এর সহায়তা প্রত্যাখ্যান এবং পুঁজি নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মাহাথির মূলধারার অর্থনীতিতে ইসলামী নীতিমালা যেমন ইসলামী ব্যাংকিং ও সুকুক বন্ড সংযুক্ত করেন। উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেন এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ তৈরি করেন উন্নয়নের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।
আশির দশকের শুরু: শিল্পায়ন উদ্যোগ ও “লুক ইস্ট” নীতি
১৯৮১ সালে মাহাথির ক্ষমতায় আসার সময় মালয়েশিয়া তীব্র বাজেট ঘাটতি এবং রাবার, টিন ও পাম তেল রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির চাপে ভুগছিল। শিল্পায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি একটি বৃহৎ শিল্পায়ন কর্মসূচি হাতে নেন এবং ১৯৮২ সালে প্রবর্তন করেন “Look East Policy”। এর উদ্দেশ্য ছিল জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মনৈতিকতা ও শিল্প দক্ষতাকে অনুসরণ করা।
এই নীতির আওতায় হাজার হাজার মালয়েশিয়ান শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীকে জাপানে পাঠানো হয় এবং জাপানি বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয় মালয়েশিয়ায়। আশা করা হয়েছিল যে পূর্ব এশীয় দক্ষতা ও শৃঙ্খলা মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত হবে। লুক ইস্ট নীতির ৪০তম বার্ষিকীতে মাহাথির উল্লেখ করেন যে ১৯৮২ সালের পর থেকে ২৬,০০০-এরও বেশি মালয়েশিয়ান জাপানে পড়াশোনা করেছে এবং প্রায় ১,৫০০ জাপানি কোম্পানি মালয়েশিয়ায় কার্যক্রম চালাচ্ছে, যেখানে চার লক্ষাধিক মানুষ কর্মরত।
এই নীতি প্রাথমিকভাবে মালয়েশিয়ার কৌশলগত ঝোঁককে পশ্চিমা নির্ভরতা থেকে সরিয়ে পূর্ব এশীয় মডেলের দিকে নিয়ে যায়। এতে যেমন অর্থনৈতিক বাস্তববাদ প্রতিফলিত হয়, তেমনি উন্নয়নে অধিক জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য মাহাথিরের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট হয়।
মাহাথিরের প্রথম দিককার বছরগুলোতে জাতীয় শিল্প অগ্রদূত তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার প্রথম জাতীয় গাড়ি কোম্পানি Proton (মিতসুবিশির প্রযুক্তিগত সহায়তায়), যার লক্ষ্য ছিল দেশীয় অটোমোবাইল শিল্প গড়ে তোলা। ইস্পাত ও সিমেন্টের মতো ভারী শিল্পগুলোকে উৎসাহিত করা হয় রাষ্ট্রায়ত্ত Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM) এর মাধ্যমে, যা প্রায়ই স্বল্পসুদে জাপানি ঋণ ব্যবহার করে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হতো।
এই পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য ছিল দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করা এবং শিল্পপণ্য আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো। রাজনৈতিকভাবে এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল: আধুনিক শিল্পে বুমিপুত্রা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জাতীয় গর্বের প্রতীক তৈরি করা (যেমন মালয়েশিয়ায় তৈরি গাড়ি), যা জাতিগত অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক হতো। তবে এই রাষ্ট্রনেতৃত্বাধীন শিল্পায়ন উদ্যোগ ব্যয়বহুল ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও দেখা দেয়। যেমন, Perwaja Steel প্রকল্প পরবর্তীতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। তবুও, এই নীতি মালয়েশিয়ার শিল্প অর্থনীতির প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে।
অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিদেশি বিনিয়োগের উত্থান (মধ্য আশির দশক–নব্বইয়ের দশক)
মধ্য আশির দশকে বৈশ্বিক মন্দা এবং পণ্যের দামের পতন মালয়েশিয়াকে কঠোরভাবে আঘাত করে। ১৯৮৫ সালে দেশটি মন্দার কবলে পড়ে। এই পরিস্থিতি মাহাথিরকে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে। ১৯৮৬ সালের পর তাঁর সরকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে বাজারমুখী নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থমন্ত্রী দাইম যায়নুদ্দিনের নেতৃত্বে সরকার কৃচ্ছ্রসাধন, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের মতো পদক্ষেপ নেয়।
এর আগেই ১৯৮৩ সালে মাহাথির “Malaysia Incorporated” ধারণা উত্থাপন করেছিলেন, যেখানে সরকার ও বেসরকারি ব্যবসাকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কল্পনা করা হয়। নব্বইয়ের দশকে এই ধারণা গতি পায়। অনেক সরকারি দপ্তর করপোরেট রূপে রূপান্তরিত হয় বা বেসরকারীকরণ করা হয়। Telekom Malaysia, Tenaga Nasional, এমনকি Malaysia Airlines-কেও আংশিক বা সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষতা বাড়ানো, সরকারের আর্থিক বোঝা হ্রাস করা এবং একই সঙ্গে মালয় উদ্যোক্তাদের একটি করপোরেট শ্রেণি তৈরি করা।
মাহাথিরের অবসর গ্রহণের সময় ২০০৩ সালে দেখা যায়, ১৯৮১ সালের তুলনায় শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়ে ৯০৬-এ দাঁড়িয়েছে এবং বাজার মূলধন ৫৫ বিলিয়ন রিঙ্গিত থেকে বেড়ে ৬৪০ বিলিয়ন রিঙ্গিতে পৌঁছেছে। এটি প্রমাণ করে তাঁর শাসনামলে বেসরকারি খাত কতটা সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।
বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণও ছিল এই নীতির আরেকটি মূল লক্ষ্য। ১৯৮৬ সালে সরকার Promotion of Investments Act চালু করে, যেখানে রপ্তানিমুখী উৎপাদনকারীদের জন্য কর প্রণোদনা দেওয়া হয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করা বুমিপুত্রা মালিকানার কিছু শর্ত শিথিল করা হয়। এর ফলে উচ্চমূল্যের রপ্তানিমুখী শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।
সময়ও ছিল অনুকূল। ১৯৮৫ সালের Plaza Accord-এর পর জাপানি ইয়েনের মান বাড়তে শুরু করে। ফলে অনেক জাপানি কোম্পানি (পরে কোরিয়ান ও তাইওয়ানিজ কোম্পানিও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উৎপাদন স্থানান্তর করতে থাকে। মালয়েশিয়ার নতুন উদার বিনিয়োগ পরিবেশ এই ঢেউয়ের প্রধান সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়। ফলে মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলে সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী কারখানার প্রসার ঘটে। পূর্ব এশিয়া থেকে মূলধন ও প্রযুক্তির প্রবাহ মালয়েশিয়াকে নব্বইয়ের দশকে এক দশকব্যাপী উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তরের পথে এগিয়ে দেয়। ফলে নব্বইয়ের শুরুর দিকেই মালয়েশিয়া এক প্রধান ইলেকট্রনিক্স রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়।
রাজনৈতিকভাবে এ নীতি ছিল মাহাথিরের এক বাস্তববাদী রূপান্তর। পূর্বের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি এটি ছিল Vision 2020-এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বৈদেশিক মূলধন ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস। নব্বইয়ের দশকে মালয়েশিয়া নিয়মিতভাবে ৮–১০ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং কৃষি ও খনিজের বাইরেও অর্থনীতিকে দৃঢ়ভাবে বহুমুখীকরণ করে। মাহাথির নিজেও বলেছিলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে নব্বইয়ের দশকে মালয়েশিয়া বিশ্বের শীর্ষ ২০ বাণিজ্যিক দেশের একটিতে পরিণত হয়।
প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় মালয়েশিয়া বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের শর্তে একীভূত হতে সক্ষম হয়েছিল। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানালেও সরকার-সংযুক্ত কোম্পানি ও নীতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এর ফলে প্রবৃদ্ধির সুফল মালয়েশিয়ার জনগণ ভোগ করতে পেরেছিল।
ভিশন ২০২০ ও উচ্চাভিলাষী আধুনিকায়ন কর্মসূচি
১৯৯১ সালে আত্মবিশ্বাসের জোয়ারে ভেসে মাহাথির ঘোষণা করেন Vision 2020। এটি ছিল এক সাহসী জাতীয় কর্মসূচি, যার লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করা। এই দীর্ঘমেয়াদি ভিশন শুধু অর্থনীতি নয়, আরও বিস্তৃত একটি কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে নয়টি চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন থেকে শুরু করে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা পর্যন্ত।
অর্থনৈতিকভাবে ভিশন ২০২০ প্রতি বছর প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ওপর জোর দেয়। রাজনৈতিকভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত ভেদাভেদ অতিক্রম করে সকল মালয়েশিয়ানকে সমৃদ্ধি ও আধুনিকতার যৌথ লক্ষ্যের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করা। এটি New Economic Policy (১৯৭০–১৯৯০)-এর পরবর্তী ধাপ হিসেবে প্রণীত হয়েছিল। NEP মূলত দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পদের পুনর্বিন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছিল। আর Vision 2020 সেই ধাপ অতিক্রম করে এক সমন্বিত আধুনিক উন্নয়ন কৌশল প্রস্তাব করে। একই বছর মাহাথির National Development Policy চালু করেন, যা NEP-এর উত্তরসূরি হলেও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণে বেশি জোর দেয়।
নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক বুম ও অবকাঠামো উন্নয়ন
নব্বইয়ের দশকের প্রথম ও মধ্যভাগে মালয়েশিয়া এক অর্থনৈতিক বুমের সাক্ষী হয়। এই সময় মাহাথির সরকার দেশকে আধুনিকায়নের জন্য বিশাল অবকাঠামো ও নগর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। মহাসড়ক, আকাশচুম্বী ভবন, বিমানবন্দর, এমনকি নতুন শহরও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় গড়ে ওঠে।
একটি ঐতিহাসিক প্রকল্প ছিল North–South Expressway। এটি ৮৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক, যা থাইল্যান্ড সীমান্ত থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করে। ১৯৯৪ সালে এটি সম্পন্ন হয় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সংযোগ বৃদ্ধি পায়। রাজধানী কুয়ালালামপুরের আকাশরেখা পাল্টে যায় Petronas Twin Towers নির্মাণের মাধ্যমে। ৪৫২ মিটার উচ্চতার এই ভবন দুটি ১৯৯৮ সালে সম্পন্ন হলে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনে পরিণত হয়। এতে জাতীয় তেল কোম্পানি পেট্রোনাসের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়। এটি মালয়েশিয়ার আধুনিক আকাঙ্ক্ষা ও দ্রুত উন্নয়নের প্রতীক হয়ে ওঠে।
সরকার নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর KLIA নির্মাণ করে। এটি ১৯৯৮ সালে চালু হয় এবং দ্রুতই বিশ্বমানের বিমানকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। এর পাশাপাশি নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয় নতুন প্রশাসনিক রাজধানী Putrajaya-এর নির্মাণ। ১৯৯৬ সালে কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়। পরে এটিকে ফেডারেল টেরিটরি ঘোষণা করা হয়। সুপরিকল্পিত এই শহরে বিশাল সরকারি ভবন, আধুনিক অবকাঠামো, বাগান ও স্মার্ট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি মাহাথিরের কল্পিত আধুনিক ও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিফলন।
আরেকটি দূরদর্শী প্রকল্প ছিল Multimedia Super Corridor (MSC)। ১৯৯৬ সালে চালু হওয়া এই উচ্চপ্রযুক্তি অঞ্চল কুয়ালালামপুর থেকে নতুন বিমানবন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাইবারজায়া শহর। MSC-কে মালয়েশিয়ার “সিলিকন ভ্যালি” হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলা। মাহাথির নিজেই বৈশ্বিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এমনকি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের নেতৃস্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা প্যানেলও গঠন করেন। ২০০০ সালের মধ্যে বিল গেটসের মতো প্রযুক্তি বিশ্বনেতারা MSC-কে পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রযুক্তি উদ্যোগ হিসেবে আখ্যা দেন।

কুয়ালালামপুরে অবস্থিত পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার, যা ১৯৯৮ সালে সম্পন্ন হয়, সে সময় বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন হিসেবে খ্যাতি পায়। মাহাথির মোহাম্মদের উন্নয়ন নীতির অধীনে এগুলো শুধু আকাশচুম্বী স্থাপত্যই নয়, বরং মালয়েশিয়ার দ্রুত আধুনিকায়নের গর্বিত প্রতীক হয়ে ওঠে।
নব্বইয়ের দশকে মাহাথির সরকারের রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুধু এই টুইন টাওয়ারই নয়, নতুন মহাসড়ক, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নতুন প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রাজায়া নির্মাণ করা হয়। এসব বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প মালয়েশিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং বিশ্বমঞ্চে দেশটির সক্ষমতা তুলে ধরে।
এই প্রকল্পগুলো ছিল ব্যয়বহুল এবং অনেক সময় সমালোচিতও হয়েছে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এগুলো মালয়েশিয়ার ভৌত ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামোকে উন্নত করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে। এসব অবদানের জন্য মাহাথির “বাপা পেমোডেনান” বা “Father of Modernisation” উপাধি অর্জন করেন।
এ ধরনের বৃহৎ রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন আধুনিকীকরণের পেছনে দুটি প্রধান যুক্তি ছিল। অর্থনৈতিকভাবে মাহাথির বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বমানের অবকাঠামো ও প্রতীকী প্রকল্প বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং মালয়েশিয়াকে নবশিল্পায়িত দেশের কাতারে উন্নীত করবে। সত্যিই, ২০০৩ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া বিশ্বের ১৭তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক জাতিতে পরিণত হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ও সেবা খাত গড়ে তোলে।
ইসলামী অর্থনীতি ও নীতিমালার সংযুক্তি
পশ্চিমা ধাঁচের শিল্প আধুনিকায়নের পাশাপাশি মাহাথিরের মালয়েশিয়া ধীরে ধীরে ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিগুলোকে আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে। এতে দেশের মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় এবং মাহাথিরের আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র গড়ার ধারণাও প্রকাশ পায়। আশির দশকে মাহাথিরের সরকার ইসলামীকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের চাহিদা পূরণ করা, একই সঙ্গে ইসলামী বিরোধী দলের প্রভাবও হ্রাস করা। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক Bank Islam Malaysia Berhad। মাহাথির এটিকে আখ্যা দেন “একটি বৃহত্তর ইসলামী অর্থনীতির প্রথম ধাপ” হিসেবে। এর পরের বছর চালু হয় দেশের প্রথম তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান, যা শরীয়াহ-সম্মত আর্থিক সেবা প্রদান শুরু করে। এই প্রাথমিক উদ্যোগগুলো মালয়েশিয়াকে আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম অগ্রদূত করে তোলে।
নব্বইয়ের দশক জুড়ে সরকার প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী আর্থিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে থাকে। ১৯৯০ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হয়, যখন Shell MDS বিশ্বের প্রথম সুকুক বা ইসলামী বন্ড মালয়েশিয়ায় ইস্যু করে। এতে ১২৫ মিলিয়ন রিঙ্গিত সংগ্রহ করা হয় এবং শরীয়াহ-সম্মত মূলধনবাজারের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। নব্বইয়ের শেষভাগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ কমিশনে বিশেষ শরীয়াহ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়, যাতে ইসলামী ব্যাংকিং ও মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একই সময়ে ইসলামী আন্তঃব্যাংক অর্থবাজার চালু করা হয়, যাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো তারল্য ব্যবস্থাপনা করতে পারে। মাহাথির এসব উদ্যোগকে সমর্থন করেন, কারণ এগুলো তাঁর কল্পিত অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, ইসলাম উন্নয়নের অন্তরায় নয়। মুসলমানরা আধুনিক কাঠামোর মধ্যেও সফল হতে পারে এবং তিনি নীতির মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।
ইসলামী অর্থনীতি সম্প্রসারণের রাজনৈতিক যুক্তি ছিল বহুমুখী। একদিকে এটি মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয়-অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে। তারা যাতে বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ করতে পারে, সে সুযোগ তৈরি হ। অন্যদিকে মালয়েশিয়াকে একটি বৈশ্বিক ইসলামী আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করত, যা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মূলধন আকর্ষণ করত।
এই কৌশলের দীর্ঘমেয়াদি সুফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় সুকুক ইস্যুকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একই সঙ্গে দেশটি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ইসলামী ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলে। বর্তমানে মালয়েশিয়ার প্রায় ৪৫ শতাংশ অর্থায়ন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে হয়। দেশটি ধারাবাহিকভাবে ইসলামী অর্থনীতি উন্নয়ন সূচকে শীর্ষে থাকে।
১৯৯৭–৯৮ এশিয়ান আর্থিক সংকট: আইএমএফকে অস্বীকার করে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ
নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে মাহাথিরের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। এটি ছিল এশিয়ান আর্থিক সংকট। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন আঞ্চলিক মুদ্রার অস্থিরতা দেখা দেয়, মালয়েশিয়াও প্রতিবেশী দেশগুলোর মতোই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিঙ্গিতের মান দ্রুত পতন ঘটে, শেয়ারবাজার প্রায় অর্ধেক ধসে পড়ে এবং বিপুল মূলধন দেশ থেকে বেরিয়ে যায়। ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে মালয়েশিয়ার জিডিপি প্রবলভাবে সংকুচিত হচ্ছিল এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অত্যন্ত কমে গিয়েছিল।
অনেক পর্যবেক্ষক ধারণা করেছিলেন মালয়েশিয়াও থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো আইএমএফের সহায়তা চাইবে এবং কঠোর মিতব্যয়ী নীতি গ্রহণ করবে। সত্যিই, প্রথমদিকে উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বে সরকার সুদের হার বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয় কমানোর মতো আইএমএফ-ধাঁচের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মাহাথির ক্রমশ এসব পদক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করছিলেন এগুলো মন্দাকে আরও গভীর করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্ত্রণ বিদেশি ঋণদাতাদের হাতে চলে যাচ্ছে।
১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি মাহাথির নাটকীয়ভাবে আনোয়ারকে সরিয়ে দেন এবং একেবারে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মালয়েশিয়া আইএমএফের সহায়তা নেবে না, বরং নিজস্বভাবে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।
১৯৯৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া রিঙ্গিতের বিনিময় হার মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৩.৮০ নির্ধারণ করে এবং বিদেশে রিঙ্গিত লেনদেন নিষিদ্ধ করে। এর ফলে জল্পনাকারীদের মূলধন পালানোর পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগের ওপর এক বছরের জন্য উত্তোলন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় (পরে তা উত্তোলনের ওপর কর ধার্য করে পরিবর্তন করা হয়)। একই সময়ে আইএমএফের নির্দেশনার বিপরীতে সুদের হার কমানো হয়, যাতে ব্যাংক ঋণ বাড়াতে পারে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল হয়। মাহাথির স্পষ্ট করে বলেন যে আইএমএফের সহায়তা প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক নীতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং কঠোর মিতব্যয়ী পদক্ষেপ এড়ানো। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ায় আইএমএফ-নির্ধারিত নীতির কারণে মন্দা আরও গভীর হয়েছে এবং সেখানে ব্যাপক বেকারত্ব ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। মালয়েশিয়া সেই পথ এড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।
মাহাথিরের এই নীতি শুরুতে সমালোচিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় ফিরবে না। কিন্তু বাস্তবে দ্রুত স্থিতিশীলতা আসে। নির্ধারিত বিনিময় হার রিঙ্গিতের পতন থামিয়ে দেয়। ব্যবসার জন্য নিশ্চয়তা তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে সহজ করার দিকে মনোযোগ দিতে পারে। মূলধনের দেশত্যাগ বন্ধ হওয়ায় রিজার্ভ রক্ষা পায় এবং নতুন করে জল্পনামূলক আক্রমণ প্রতিরোধ হয়।
১৯৯৮ সালে অর্থনীতি ৭.৪ শতাংশ সংকুচিত হলেও ১৯৯৯ সালে প্রবৃদ্ধি ফিরে আসে ৬.১ শতাংশে। তা-ও আইএমএফ ঋণ ছাড়াই। এই সাফল্য মাহাথিরের অবস্থানকে অনেকের চোখে বৈধতা দেয়। পরে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকও স্বীকার করে যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অস্থায়ী পুঁজি নিয়ন্ত্রণ বৈধ নীতি হতে পারে। পল ক্রুগম্যানের মতো অর্থনীতিবিদও মন্তব্য করেন যে মালয়েশিয়ার বিকল্প প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিকে গভীর ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে এবং তা পরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার আইএমএফ কর্মসূচি এতটাই কঠোর ছিল যে ১৯৯৮ সালে অর্থনীতি ১৩ শতাংশের বেশি সংকুচিত হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মালয়েশিয়া আইএমএফের শর্ত এড়িয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকেও রক্ষা পায়।
রাজনৈতিকভাবে সংকট শুরুর ১৪ মাস পর পুঁজি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা নেতৃত্বের এক দৃঢ় প্রকাশ ছিল। এটি মন্ত্রিসভার প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আনোয়ার ইব্রাহিমকে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করা, যিনি এসব নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। বিতর্ক সত্ত্বেও ফলাফল স্পষ্ট ছিল। মালয়েশিয়া অধিকাংশ প্রতিবেশীর তুলনায় দ্রুত সংকট থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো আইএমএফ ঋণ বা শর্ত ছাড়াই এবং মৌলিক শিল্প অক্ষত রেখেই। এই ঘটনাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে মাহাথির ফর্মুলা। বৈশ্বিক প্রচলিত নীতিকে অগ্রাহ্য করার সাহস এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সংহতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
বেসরকারীকরণ ও রাষ্ট্র-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান: রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে ভারসাম্য
মাহাথিরের অর্থনৈতিক কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রীয় দিকনির্দেশনা ও বেসরকারি খাতের দক্ষতার বাস্তবসম্মত সমন্বয়। এর প্রতিফলন ঘটে তাঁর বেসরকারীকরণ কর্মসূচি এবং রাষ্ট্র-সংযুক্ত কোম্পানি বা GLC (Government-Linked Companies) গঠনের মাধ্যমে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে মালয়েশিয়ায় টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, মহাসড়ক থেকে শুরু করে এয়ারলাইন্স পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়।
সরকারের দাবি ছিল যে “বেসরকারি খাত-নির্ভর প্রবৃদ্ধি” সেবার মান উন্নত করবে এবং সরকারি আর্থিক বোঝা হ্রাস করবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ মানে এই নয় যে রাষ্ট্র পুরোপুরি ব্যবসা থেকে সরে গেছে। বরং প্রায়ই দেখা গেছে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে করপোরেট রূপ দেওয়া হয়েছে, আংশিক শেয়ার বাজারে ছাড়া হয়েছে, কিন্তু সরকার বা বুমিপুত্রা ট্রাস্ট সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধরে রেখেছে। এর ফলে রাষ্ট্র-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান ঘটে, যেখানে সরকার হয় শেয়ারহোল্ডার হিসেবে বা রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করত।
Petronas (তেল), Tenaga Nasional (বিদ্যুৎ), Telekom Malaysia এবং POS Malaysia-এর মতো কোম্পানিগুলো করপোরেট কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তবে এসব খাতে সরকার প্রধান অংশীদার বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে রয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্বভৌম সম্পদ তহবিল Khazanah Nasional, যা এসব বিনিয়োগ সরকারের পক্ষে পরিচালনা করে।
বেসরকারীকরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল অদক্ষ ও লোকসানী সরকারি সংস্থাগুলোকে বাজারের শৃঙ্খলার আওতায় আনা। এর ফলে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল। পাশাপাশি বিক্রির অর্থ দিয়ে সরকারের ঋণ কমানো সম্ভব হবে, যা আশির দশকে জিডিপির শতভাগেরও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাহাথিরের সংস্কারের পর বাজেট ঘাটতি হ্রাস পায় এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সরকার উদ্বৃত্ত বাজেট চালাতে সক্ষম হয়। বেসরকারি খাতের জিডিপিতে অংশও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।
রাজনৈতিকভাবে বেসরকারীকরণ ছিল একটি কৌশল। এর মাধ্যমে New Economic Policy-এর লক্ষ্য অর্থাৎ বুমিপুত্রা ব্যবসায়ী শ্রেণি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অনেক বেসরকারীকৃত চুক্তি বা লাইসেন্স শাসক দলের ঘনিষ্ঠ মালয় ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়। এতে রাজনীতি ও ব্যবসা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। মহাসড়ক নির্মাণ ছিল এর একটি উদাহরণ। বেসরকারি ঠিকাদাররা দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক টোল চুক্তি পেত, প্রয়োজনে সরকারি সাহায্যও পেত। এর ফলে এক শ্রেণির “কর্পোরেট মালয়” ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যারা সরকারি সুবিধার মাধ্যমে উপকৃত হতো। সমালোচকরা একে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বলে অভিহিত করেন। অর্থনীতিবিদ জোমো কে এস মন্তব্য করেছিলেন যে মাহাথির আমলে অনেক সময় “privatization” আসলে “piratization” ছিল। জনগণের সম্পদ সস্তায় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হতো এবং সংকটকালে রাষ্ট্র উচ্চমূল্যে আবার তা কিনে নিত।
তবুও মাহাথিরের বেসরকারীকরণ ও রাষ্ট্র-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান কৌশলের সামগ্রিক প্রভাব মূলত ইতিবাচক ছিল। এর ফলে মালয়েশিয়ায় আধুনিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, দক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সম্প্রসারিত পরিবহন অবকাঠামো গড়ে ওঠে। Petronas-এর মতো কিছু প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং সরকারকে বিপুল রাজস্ব প্রদান করে।
Malaysia Incorporated নীতি, যা সরকার ও ব্যবসার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা তৈরি করেছিল, জাপানের keiretsu মডেলের অনুকরণে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে বৃহৎ প্রকল্পে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। যদিও এতে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং দুর্নীতি দেখা দেয়, তবুও সরকারকে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বেসরকারি খাতকে কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় মালয়েশিয়া একটি তুলনামূলক ভালো ভারসাম্য অর্জন করে। ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েতনামের মতো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির চেয়ে এটি বেশি বাজারভিত্তিক, আর ফিলিপাইনের মতো ল্যাসে-ফেয়ার মডেলের চেয়ে বেশি রাষ্ট্র-সমন্বিত। এই মধ্যপন্থা মালয়েশিয়াকে অবকাঠামোতে কম বিনিয়োগের সমস্যা থেকে রক্ষা করে এবং একই সঙ্গে পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অদক্ষতাও এড়াতে সাহায্য করে। এটিই মাহাথির যুগে টেকসই প্রবৃদ্ধির অন্যতম মূল রহস্য।
দ্বিতীয় মেয়াদ (২০১৮–২০২০): সংস্কার, কৃচ্ছ্রসাধন ও যৌথ সমৃদ্ধি
৯২ বছর বয়সে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতায় ফিরে আসেন মাহাথির। এতে তিনি মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনায় আবারও প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পান। তবে প্রেক্ষাপট ছিল একেবারেই ভিন্ন। এ সময় তিনি একটি মধ্যম আয়ের এবং বহুমুখীকৃত অর্থনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে পান, যা নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সরকারি ঋণ ছিল এক ট্রিলিয়ন রিঙ্গিতেরও বেশি (দায়সহ)। পাশাপাশি ছিল 1MDB দুর্নীতির কেলেঙ্কারির প্রভাব এবং প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়া ও বৈষম্যের উদ্বেগ।
একটি সংস্কারবাদী জোট Pakatan Harapan নেতৃত্ব দিয়ে মাহাথির দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দলকে পরাজিত করে। ক্ষমতায় এসে তিনি প্রথমেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসনের দিকে মনোযোগ দেন। 1MDB কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এর মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে Council of Eminent Persons গঠন করেন।
দ্বিতীয় দফায় মাহাথির ব্যয়সংকোচন ও অগ্রাধিকারের ওপর জোর দেন। এটি ছিল নব্বইয়ের দশকের তাঁর বিলাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রায় বিপরীত। তিনি যুক্তি দেন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো জরুরি। তাই পূর্ববর্তী সরকারের শুরু করা একাধিক মেগা প্রকল্প বাতিল বা পুনর্বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুয়ালালামপুর–সিঙ্গাপুর হাই-স্পিড রেল প্রকল্প বাতিল করা হয়। মাহাথির যুক্তি দেন এটি “লাভজনক নয়, আমাদের বিপুল অর্থ ব্যয় হবে, কিন্তু এর থেকে আয় হবে না।” আরেকটি বড় প্রকল্প, চীন-সমর্থিত ইস্ট কোস্ট রেল লিংক, স্থগিত করে পরে কম খরচে পুনঃআলোচনা করা হয়।
দেশীয়ভাবে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করে বহুল সমালোচিত GST (Goods and Services Tax) বাতিল করে। এর পরিবর্তে চালু করা হয় সহজতর সেলস ট্যাক্স। যদিও এতে সরকারি আয় স্বল্পমেয়াদে হ্রাস পায়, তবুও এটি জনগণের কাছে জনপ্রিয় হয় এবং ভোগ ব্যয় বাড়াতে সহায়ক হয়।
যৌথ সমৃদ্ধি ভিশন ২০৩০
মাহাথিরের সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় মেয়াদের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ ছিল ২০১৯ সালের শেষ দিকে Shared Prosperity Vision 2030 (SPV 2030) চালু করা। স্বীকার করা হয়েছিল যে Vision 2020-এর উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়নি, বিশেষ করে সমবণ্টনের ক্ষেত্রে। তাই নতুন এই রোডম্যাপ তৈরি করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মালয়েশিয়ানকে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান প্রদান এবং দেশটিকে আবারও “নতুন এশিয়ান টাইগার” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং নতুন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্র চিহ্নিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মাহাথির বলেন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারকে “ক্যানসারের মতো অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে” দূর করতে হবে।
SPV 2030 মূলত অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও সুশাসন সংস্কারকে একত্রিত করে। এতে অতীতের অতিরিক্ততা ও বৈষম্য থেকে শিক্ষা নেওয়া হয়। এটি ছিল মাহাথিরের বিদায়ী ভিশন যাতে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে আশি ও নব্বইয়ের দশকে যে সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছিলেন তা টেকসই হবে এবং আরও সমভাবে বণ্টিত হবে।
২০২০ সালের মার্চে রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং একই সঙ্গে কোভিড-১৯ মহামারির সূচনার কারণে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হয়। মাত্র ২১ মাসে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ফলাফল অর্জিত না হলেও এটি প্রমাণ করে স্বল্প সময়ে পরিবর্তন আনা কতটা কঠিন। তবে প্রতীকীভাবে তাঁর প্রত্যাবর্তন উন্নয়ন দর্শনের স্থায়ী প্রভাবকে তুলে ধরে। তিনি মালয়েশিয়াকে আর্থিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক নেতৃত্বের দিকে পুনরায় মনোযোগী করেন। তাঁর মতে, উত্তরসূরীরা যে শৃঙ্খলাবদ্ধ উন্নয়নের পথ থেকে সরে গিয়েছিল তা সংশোধন করার চেষ্টা করেন তিনি।
মাহাথির মোহাম্মদের মোট ২৪ বছরের নেতৃত্বে মালয়েশিয়া এক অসাধারণ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। একটি স্বল্প আয়ের পণ্য রপ্তানিকারক দেশ থেকে এটি পরিণত হয় এক বহুমুখী, উচ্চ-মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে। ১৯৮০ সালে মাথাপিছু জিডিপি যেখানে প্রায় ১,৮০০ ডলার ছিল, তা ২০০০ সালের শুরুর দিকে ৯,০০০ ডলারেরও বেশি হয়ে যায়। দারিদ্র্যের হার নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। শতাব্দীর শুরুতে মালয়েশিয়া শুধু রাবার ও পাম তেল নয়, মাইক্রোচিপ ও গাড়িও উৎপাদন করছিল। জনগণ উন্নত দেশের মানসম্মত অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে। মাহাথিরের শাসনামল মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূদৃশ্যকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে। এজন্য তিনি উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে খ্যাতি পান। দেশীয়ভাবে তিনি “Father of Modernisation” নামে পরিচিত হন। গুরুত্বপূর্ণ হলো, মাহাথির সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও কখনো কখনো কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তবে এই স্থিতিশীলতাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছিল।মাহাথির মোহাম্মদের অধীনে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক রূপান্তরের রহস্য ছিল দূরদর্শী পরিকল্পনা, রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ ও অভিযোজিত বাস্তববাদের সমন্বয়ে। তিনি একদিকে বৃহৎ ধারণা যেমন জাতীয় ভিশন, অবকাঠামো বিনিয়োগ ও সামাজিক প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়েছেন, অন্যদিকে নীতিতে নমনীয়তা দেখিয়ে কখনো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, কখনো বাজারমুখী সংস্কার গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজনে প্রচলিত বৈশ্বিক নীতি ভেঙে গিয়েছেন, আবার প্রয়োজনে বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আমন্ত্রণ করেছেন।
এই দ্বৈত কৌশল—একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও বৈশ্বিক, প্রচলিত ও অপ্রচলিত—মালয়েশিয়ার অনন্য প্রেক্ষাপটে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং দেশটি একদিকে উৎপাদনশীল শিল্পশক্তি, অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতির বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।
আজ মাহাথির যখন ২০২৫ সালে শতবর্ষে পা রাখছেন, সমালোচকরাও স্বীকার করেন যে তিনি মালয়েশিয়াকে রূপান্তরিত, আধুনিকায়িত, শিল্পায়িত এবং শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকার জটিল হলেও এটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান পাঠ, যেখানে অর্থনৈতিক কৌশল ও রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ে জাতি গঠনের দিশা খুঁজে পাওয়া যায়।
ভোটের কাগজে বীজ, মাটিতে পড়লেই জন্মাবে সবজি
লিফলেট থেকে গাছ জন্মাবে শুনতে অবাক লাগলেও বিষয়টি মোটেই কল্পকাহিনি নয়। আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির কল্যাণে এমন কাগজ ইতোমধ্যে বাস্তবতা পেয়েছে, যা ব্যবহারের পর মাটিতে ফেললে বা পুঁতে দিলে সেখান থেকে গাছ গজায়। এই বিশেষ ধরনের কাগজ পরিচিত ‘বন-কাগজ’ বা ‘সিড পেপার’ নামে।
এবার এই ধারণার অভিনব প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–এর চেয়ারম্যান তারেক রহমান–সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও প্রার্থী প্রচারণায় ব্যবহার করছেন বীজযুক্ত এই বিশেষ লিফলেট। প্রচারণার কাগজ মাটিতে পড়েই যেন সবজির চারা হয়ে ওঠে এমন ধারণা থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
দলীয় নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের লক্ষ্য কেবল ভোটারদের কাছে বার্তা পৌঁছানো নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন এবং ‘জিরো ওয়েস্ট’ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। প্রচারণা শেষে যেখানে সাধারণ লিফলেট আবর্জনায় পরিণত হয়, সেখানে বন-কাগজ মাটিতে মিশে গিয়ে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়।
বিশ্বে পরিচিত ধারণা, বাংলাদেশে নতুন প্রয়োগ
যদিও দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এটি নতুন, তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বীজযুক্ত কাগজ একেবারেই অপরিচিত নয়। পরিবেশ রক্ষার অংশ হিসেবে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন, সামাজিক সচেতনতা ও পরিবেশ আন্দোলনে সিড পেপার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পোস্টার, আমন্ত্রণপত্র এমনকি ব্যবসায়িক কার্ডেও এই কাগজের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।
কীভাবে তৈরি হয় বন-কাগজ
বন-কাগজ তৈরির প্রক্রিয়াটিও পরিবেশবান্ধব। ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করে প্রথমে ছোট টুকরো করা হয়। এরপর প্রায় ৪২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে কাগজকে সম্পূর্ণ গলিয়ে নেওয়া হয়। এই গলিত কাগজ থেকে তৈরি হয় মণ্ড। নির্দিষ্ট ফ্রেমে সেই মণ্ড ঢেলে বিশেষ কৌশলে এর সঙ্গে বীজ যুক্ত করা হয়, যাতে কাগজ শুকানোর সময় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট না হয়। শেষে শুকিয়ে তৈরি হয় লিফলেট বা পোস্টার।
কীভাবে গাছ জন্মায় এই কাগজ থেকে
বন-কাগজের ভেতরে থাকা বীজ মাটির সংস্পর্শে এলে এবং পর্যাপ্ত আর্দ্রতা পেলে ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়। পুরো লিফলেট অথবা ছোট টুকরো করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায়। মাটি শুষ্ক হলে হালকা পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিলেই যথেষ্ট। উপযুক্ত পরিবেশে একটি বন-কাগজ থেকেই ধীরে ধীরে চারা গজিয়ে গাছে পরিণত হয়। এই কাগজ এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে, অর্থাৎ তৈরি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মাটিতে ফেললে গাছ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।
কোন বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে
এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় পাঁচ ধরনের দেশি সবজির বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো বেগুন, টমেটো, মরিচ, লালশাক ও ডাঁটাশাক। এসব সবজি সহজে জন্মায় এবং ঘরোয়া পরিবেশে পরিচর্যাও তুলনামূলক কম লাগে। তাই কেউ চাইলে বারান্দা বা ছাদের টবে এই লিফলেট পুঁতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সবজির চারা পেতে পারেন। এক মাসের মধ্যেই মিলতে পারে নিজ হাতে ফলানো সবজি।
খরচ বেশি, সুফল দীর্ঘমেয়াদি
সাধারণ কাগজের তুলনায় বন-কাগজের খরচ কিছুটা বেশি। প্রতিটি সিড পেপার লিফলেট তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৮ টাকা। তবে উদ্যোক্তারা মনে করেন, পরিবেশ দূষণ কমানো, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং বর্জ্যহীন প্রচারণার সুফল বিবেচনায় এই ব্যয় যুক্তিসংগত। পরিবেশবিদদের মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
রাজনীতির কাগজ যদি মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে ওঠে তাহলে সেটিই হয়তো হবে প্রচারণার সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা।
সবাই যেদিকে যায় সেদিকে সে নেই: ভাইরাল পেঙ্গুইনের একাকী যাত্রার নেপথ্য কাহিনী

মোঃ আশিকুজ্জামান
নিজস্ব প্রতিবেদক
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি একাকী পেঙ্গুইন তার দল ছেড়ে বিশাল বরফাবৃত পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটি আসলে কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয় বরং এটি ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জার্মান চলচ্চিত্র নির্মাতা ভার্নার হারজগের বিখ্যাত ডকুমেন্টারি 'এনকাউন্টারস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' থেকে নেওয়া একটি অংশ। ভিডিওর সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে দেখা যায় এন্টার্কটিকার একদল অ্যাডেলি পেঙ্গুইন তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সমুদ্রের খাবারের সন্ধানে এগোচ্ছে ঠিক তখনই একটি পেঙ্গুইন হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এবং দল ছেড়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে অর্থাৎ জনমানবহীন ও প্রাণহীন বিশাল এক পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করে। পরিচালক হারজগ এই একাকী পথচলাকে একটি 'ডেথ মার্চ' বা মৃত্যুর পথে যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কারণ পাহাড়ের সেই প্রতিকূল পরিবেশে কোনো খাবারের অস্তিত্ব নেই এবং এই পথচলা পেঙ্গুইনটির নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে। বিজ্ঞানীরাও এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে এমনকি পেঙ্গুইনটিকে জোর করে তার দলের কাছে ফিরিয়ে আনলেও সে আবারও একই জেদ নিয়ে পাহাড়ের দিকেই হাঁটতে শুরু করবে।
২০২৬ সালে এসে এই ভিডিওটি নতুন করে ভাইরাল হওয়ার পেছনে কাজ করছে এক গভীর আবেগীয় ও প্রতীকী কারণ। বর্তমান সময়ের মানুষ যারা তীব্র মানসিক চাপ বা 'বার্নআউট'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা এই পেঙ্গুইনটির একাকী ও লক্ষ্যহীন পথচলার মাঝে নিজেদের জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছেন। অনেকে সামাজিক প্রথা বা গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মতো চলার এক প্রতীকী সাহস হিসেবে একে দেখছেন যদিও সেই পথটি শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি 'হোপকোর' বা অনুপ্রেরণামূলক ক্যাটাগরিতে শেয়ার হচ্ছে যেখানে অনেকেই লিখছেন যে সে হয়তো নিজের গন্তব্য পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে নিজের ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার সাহস যুগিয়েছে। এই চর্চা আরও গতি পায় যখন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়ে একটি পোস্ট করেন তবে সেই পোস্টে গ্রিনল্যান্ড ও পেঙ্গুইনের অবস্থান নিয়ে ভৌগোলিক ভুল থাকায় তা ইন্টারনেটে হাস্যরসের সৃষ্টি করে।
মানুষ এই ঘটনাকে দার্শনিক বা বীরত্বপূর্ণ রূপ দিলেও বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অবশ্য বেশ নিস্পৃহ ও সরাসরি। তাঁদের মতে এই পেঙ্গুইনটির আচরণে কোনো মহান উদ্দেশ্য বা সাহসিকতা নেই বরং এটি মূলত একটি স্নায়বিক বিভ্রান্তি বা 'ডিসঅরিয়েন্টেশন'। পেঙ্গুইনরা সাধারণত সমুদ্রের দিক নির্ণয় করার জন্য প্রকৃতির কিছু নির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করে থাকে কিন্তু কোনো কারণে এই পেঙ্গুইনটির মস্তিষ্ক সেই সংকেত বুঝতে ভুল করেছিল অথবা কোনো স্নায়বিক সমস্যার কারণে সে সঠিক দিক হারিয়ে ফেলেছিল। তবে বিজ্ঞানের এই নিরস ব্যাখ্যার চেয়ে মানুষের কাছে এটি এখন আর কেবল একটি পাখির ভুল হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি একাকিত্ব, মানসিক অবসাদ এবং প্রথা ভাঙার এক গভীর আবেগীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে যা ২০ বছর আগের একটি ডকুমেন্টারি দৃশ্যকে আজ ইন্টারনেটের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে রূপান্তর করেছে।
যে দেশে মা ও দাদির সাথে সুর মিলিয়ে কান্না না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় বিয়ে
বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিয়ে মানেই উৎসব ও নাচের আয়োজন হলেও চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টুজিয়া সম্প্রদায়ের রীতি একদম ভিন্ন। এখানে বিয়ের আগে কনের কান্না করাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য হিসেবে দেখা হয়। কিং রাজবংশের শেষ যুগ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথাটি বর্তমানে আধুনিক শহরগুলোতে কমে গেলেও গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় এখনও টিকে আছে। এটি কেবল চোখের জল নয় বরং একটি সংগীতময় প্রকাশ যাকে ক্রাই সং বলা হয়। কনে এই গানের মাধ্যমে তার পরিবার ও মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং নতুন জীবনে প্রবেশের আবেগ প্রকাশ করে।
বিয়ের অন্তত এক মাস আগে থেকেই কনেকে প্রতিদিন কান্নার এই প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। প্রথা অনুযায়ী কনে প্রতিদিন রাতে একটি বিশেষ ঘরে বসে এক ঘণ্টা করে কাঁদে। দশ দিন পর তার সাথে যোগ দেন মা এবং আরও দশ দিন পর দাদি বা নানি সহ পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক নারীরা এই কান্নার আসরে সামিল হন। অনেক ক্ষেত্রে কনের বান্ধবীরাও একত্রিত হয়ে কাঁদে এবং গান গায় যা টেন সিস্টার গ্যাদারিং নামে পরিচিত। এই দীর্ঘমেয়াদী কান্নার প্রক্রিয়াটি জুও তাং বা হলে বসে থাকা হিসেবে টুজিয়া সমাজে সমাদৃত।
প্রাচীনকালে এই কান্নার পেছনে একটি সামাজিক বিদ্রোহের দিকও ছিল। তখন মেয়েদের বিয়ে সাধারণত ঘটক বা মা-বাবার পছন্দে হতো বলে কনে কান্নার মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরত। এমনকি প্রথা অনুযায়ী কনে যদি যথেষ্ট পরিমাণ না কাঁদতে পারত তবে তাকে অশিক্ষিত বা নিচু পরিবারের মেয়ে হিসেবে সামাজিকভাবে সমালোচনা করা হতো। অনেক সময় কনের মা তাকে পর্যাপ্ত কান্নার জন্য শাস্তিও দিতেন। কান্নার গানের লিরিক্সে অনেক সময় ঘটককে তিরস্কার করার বিষয়টিও উঠে আসত যা এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদের প্রতীক ছিল।
বর্তমানে টুজিয়া সম্প্রদায়ের এই প্রথাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর হিসেবে দেখা হয়। কান্নার মাধ্যমে কনে তার ফেলে আসা জীবনের সব স্মৃতি ও দুঃখকে বিদায় জানিয়ে নতুন জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। গ্রামীণ ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ মনে করে এই রীতি কনের সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। আধুনিক জীবনের প্রভাবে অনেক কিছু বদলে গেলেও টুজিয়াদের এই ক্রাইং ম্যারেজ আজও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সূত্র: ডেইলি চায়না
এক চড়, দশ হাজার টাকা, আর চিরকালের নত মেরুদণ্ড
ব্রিটিশ শাসনামলে একদিন এক ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা রাগের বশে এক তরুণ ভারতীয় যুবকের গালে সপাটে চড় বসান। মুহূর্তের মধ্যেই যা ঘটল, তা উপনিবেশিক অহংকারের ইতিহাসে বিরল। কোনো দ্বিধা না করে সেই তরুণ পূর্ণ শক্তিতে পাল্টা চড় মারল। আঘাতে ইংরেজ কর্মকর্তা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বিস্ময়, অপমান আর অবিশ্বাস একসঙ্গে তাকে গ্রাস করল। কীভাবে এক “সাধারণ” ভারতীয় যুবক সাহস পেল এমন এক সামরিক কর্মকর্তার গায়ে হাত তুলতে, যে সাম্রাজ্যের সূর্য নাকি কখনো অস্ত যেত না।
ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা ছুটে গেলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের কাছে। দাবি একটাই, কঠোর শাস্তি। কিন্তু প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে কমান্ডার শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওই যুবককে শাস্তি নয়, পুরস্কৃত করতে হবে। পুরস্কার হিসেবে তাকে দিতে হবে দশ হাজার রুপি। শুনে ইংরেজ কর্মকর্তা বিস্ফোরিত হলেন। এটি কেবল ব্যক্তিগত অপমান নয়, ব্রিটিশ রাণীর অপমান, আর তার জবাবে পুরস্কার। কিন্তু আদেশ আদেশই। আপত্তির কোনো সুযোগ নেই।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্মকর্তা সেই ভারতীয় যুবকের হাতে দশ হাজার রুপি তুলে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। যুবক টাকা নিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলে গেল একদিন নিজের দেশেই এক ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার হাতে অপমানিত হওয়ার কথা। সে সময় দশ হাজার রুপি ছিল অকল্পনীয় সম্পদ। সে অর্থ কাজে লাগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয়ে উঠল ধনী, সমাজে সম্মানিত, প্রভাবশালী। একসময়ের সাধারণ মানুষ এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি।
বছর কেটে গেল। একদিন সেই একই ঊর্ধ্বতন কমান্ডার আবার তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাকে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন, ওই ভারতীয়কে কি মনে আছে। কর্মকর্তার চোখে তৎক্ষণাৎ পুরোনো অপমান জ্বলে উঠল। কমান্ডার তখন বললেন, সময় এসেছে। যাও, তাকে খুঁজে বের করো এবং সবার সামনে আবার গালে চড় মারো।
ভয়ে কাঁপতে লাগল কর্মকর্তা। সে বলল, তখন সে গরিব ছিল, তবু প্রতিশোধ নিয়েছিল। এখন সে ধনী, প্রভাবশালী। এবার সে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কমান্ডার কঠোর স্বরে বললেন, এটিও আদেশ।
আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। কর্মকর্তা গেলেন। সবার সামনে সেই ভারতীয়কে চড় মারলেন। কিন্তু এবার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া নেই। লোকটি চোখ তুলেও তাকাল না। নীরবে অপমান সহ্য করল।
হতবাক কর্মকর্তা ফিরে এসে কমান্ডারকে সব বললেন। তখন কমান্ডার ধীরে, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, প্রথমবার ওই যুবকের কাছে ছিল শুধু তার সম্মান। সেটাই ছিল তার সবকিছু। তাই সে প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু আজ সে আর সম্মান রক্ষা করল না, কারণ এখন তার কাছে এমন কিছু আছে, যা সে সম্মানের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে, তার সম্পদ। যেদিন সে ওই দশ হাজার রুপি গ্রহণ করেছিল, সেদিনই সে নিজের মর্যাদা বিক্রি করে দিয়েছিল। আর যে মানুষ নিজের আত্মসম্মান বিক্রি করে, তার মেরুদণ্ড চিরতরে নুয়ে যায়।
এই গল্প কেবল অতীতের কোনো উপনিবেশিক উপাখ্যান নয়। এটি আজকের জন্য এক নির্মম আয়না। আমরা কতবার সত্যকে চেপে গেছি সুবিধার জন্য। কতবার না জেনে কাউকে কলঙ্কিত করেছি। কতবার অবস্থান, উপহার কিংবা লোভের কাছে মাথা নত করেছি। প্রতিবারই হয়তো আমরা আমাদের আত্মসম্মানের এক একটি অংশ বিক্রি করেছি।
এখনই সময় নিজেকে প্রশ্ন করার। আমরা কি আমাদের হৃদয় ও বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করছি। ক্ষমা চাইবার সময় এখনই, যাতে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষত থাকে। পদ, উপহার কিংবা লোভের কাছে কখনো নত না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই মানুষের আসল পরিচয়। প্রশ্ন একটাই, আমরা কি সেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব।
(অনূদিত)
কেন ১ জানুয়ারি নতুন বছর? জানুন এর পেছনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস
পৃথিবীজুড়ে আতশবাজি আর উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, বছরের শুরুর এই দিনটি সবসময় ১ জানুয়ারি ছিল না। প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে বছরের শুরু হতো ১ মার্চ থেকে এবং বছরে মাস ছিল মাত্র ১০টি। যার রেশ আজও রয়ে গেছে আমাদের ক্যালেন্ডারে; ল্যাটিন শব্দ 'Septem' মানে ৭, সেই হিসেবে সেপ্টেম্বর ছিল সপ্তম মাস এবং 'Decem' মানে ১০ অনুযায়ী ডিসেম্বর ছিল দশম মাস। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের অসামঞ্জস্য দূর করতেই শুরু হয় সংস্কার।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের পরামর্শে ‘জুলিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন। সিজারই প্রথম জানুয়ারির ১ তারিখকে বছরের শুরু হিসেবে ঘোষণা করেন। এই মাসের নামকরণ করা হয়েছিল রোমান দেবতা ‘জানুস’-এর নামানুসারে। জানুসের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর দুটি মুখ—একটি পেছনের দিকে (অতীত দেখার জন্য) এবং অন্যটি সামনের দিকে (ভবিষ্যৎ দেখার জন্য)। নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে এই মাসটিকেই বছরের সূচনার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়।
রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে ইউরোপের অনেক দেশ ধর্মীয় কারণে ১ জানুয়ারিকে বছরের শুরু হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা ২৫ ডিসেম্বর বা ২৫ মার্চকে বছরের শুরু হিসেবে পালন করত। তবে ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ক্যালেন্ডারের ভুল সংশোধন করে ‘গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন এবং পুনরায় ১ জানুয়ারিকে বছরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং বর্তমানের সার্বজনীন ক্যালেন্ডারে রূপ নেয়।
বর্তমানে ১ জানুয়ারি কেবল একটি তারিখ পরিবর্তনের দিন নয়, বরং বিশ্বজুড়ে প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগের একটি সাধারণ মানদণ্ড। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রোমান দেবতা জানুসের সেই শিক্ষা—অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকাতে। হাজার বছরের সংস্কার আর বিবর্তন পেরিয়ে আজ এই দিনটি বিশ্বের বৃহত্তম ও সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।
সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস
গাছ কাটলে গাছের কি সত্যিই ব্যথা লাগে? বিজ্ঞান কী বলে
গাছের কি ব্যথা লাগে-এই প্রশ্নটি অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। উদ্ভিদের শরীরে কোনো ব্যথা অনুভবকারী রিসেপ্টর, স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক নেই। ফলে প্রাণিজগতের সদস্য হিসেবে মানুষ বা পশু যেভাবে ব্যথা অনুভব করে, উদ্ভিদ সেই অর্থে ব্যথা অনুভব করতে সক্ষম নয়। তাই একটি গাজর মাটি থেকে তুলে নেওয়া, ঝোপঝাড় ছাঁটা বা একটি আপেল কামড়ে খাওয়া কোনোভাবেই ‘উদ্ভিদ নির্যাতন’ হিসেবে বিবেচিত হয় না।
তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, উদ্ভিদ সম্পূর্ণ সংবেদনশূন্য নয়। তারা শারীরিক উদ্দীপনা, স্পর্শ বা ক্ষতির উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারে যদিও সেটি ব্যথা নয়, বরং জৈব-রাসায়নিক ও কোষীয় প্রতিক্রিয়া।
কিছু উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে। যেমন ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ নামের উদ্ভিদটি অর্ধ সেকেন্ডের মধ্যেই পাতা বন্ধ করে শিকার ধরে ফেলতে পারে। আবার লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ পেলেই পাতা গুটিয়ে নেয়, যা সম্ভাব্য তৃণভোজী প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখার একটি প্রতিরক্ষামূলক কৌশল বলে মনে করা হয়। এই উদ্ভিদগুলোর আচরণে স্পষ্টতই একধরনের সংবেদনশীল ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়।
তবে আরও বিস্ময়কর তথ্য এসেছে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে। দেখা গেছে, সাধারণ সরিষা জাতের একটি উদ্ভিদ যা গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত পাতায় পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে কোষীয় স্তরে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে পারে। এই সংকেত এক পাতা থেকে আরেক পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদকে সতর্ক করে দেয় যেন সে দ্রুত রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে। ফলে শুঁয়োপোকা বা এফিডের মতো ক্ষতিকর পোকা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
এই বৈদ্যুতিক সংকেত শুনে অনেকের মনে হতে পারে, উদ্ভিদ বুঝি ব্যথা পাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে বলছেন, এই সংকেত কোনোভাবেই প্রাণীর ব্যথার সংকেতের মতো নয়। এখানে কোনো অনুভূত যন্ত্রণা নেই, নেই সচেতন কষ্টবোধ। এটি নিছক একটি প্রতিরক্ষামূলক সংকেত ব্যবস্থা, যা উদ্ভিদের টিকে থাকার কৌশলের অংশ।
উদ্ভিদ আলো, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের প্রবাহ এমনকি ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের আক্রমণও শনাক্ত করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভূতির ফল নয়, বরং কোটি কোটি বছরের বিবর্তনে গড়ে ওঠা জৈবিক অভিযোজন। উদ্ভিদের জীবনধারা ‘কষ্ট বনাম সুখ’ দিয়ে পরিচালিত নয়; বরং এটি পরিচালিত হয় টিকে থাকা বা বিলুপ্তির সরল বাস্তবতায়।
সুতরাং, উদ্ভিদের এই অসাধারণ সক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করলেও, তাদের মানুষের মতো ব্যথা অনুভবকারী জীব হিসেবে কল্পনা করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। উদ্ভিদ অনুভব করে না—তারা প্রতিক্রিয়া জানায়।
সূত্র: ব্রিটানিকা
অলিম্পিক স্বর্ণপদক কি সত্যিই খাঁটি সোনা, জানুন ইতিহাস
অলিম্পিকের মঞ্চে সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে গলায় স্বর্ণপদক পরার মুহূর্তটি যেকোনো ক্রীড়াবিদের কাছে অমূল্য। তবে আবেগের দিক থেকে যতটাই মূল্যবান হোক না কেন, বাস্তব অর্থমূল্যের বিচারে অলিম্পিক স্বর্ণপদক রুপার পদকের চেয়ে খুব বেশি দামী নয়। এর কারণ হলো, অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণপদক আসলে সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি নয়।
অলিম্পিক গেমস–এর বিধিমালা অনুযায়ী, স্বর্ণপদকে কমপক্ষে ৯২.৫ শতাংশ রুপা থাকতে হয় এবং তার ওপরে মাত্র প্রায় ছয় গ্রাম খাঁটি সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। একইভাবে রুপার পদকও ৯২.৫ শতাংশ রুপা দিয়ে তৈরি হয়। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ পদক বানানো হয় তামা ও বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে। ফলে স্বর্ণ ও রুপার পদকের উপাদানগত পার্থক্য খুবই সীমিত।
পদক প্রদানের এই রীতি আদতে খুব প্রাচীন নয়। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয় ১৮৯৬ সালে গ্রিসের এথেন্সে। তবে সে সময়কার পদকগুলো আজকের পরিচিত স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ কাঠামোর মতো ছিল না। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসরে বিজয়ীদের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়নি।
প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস আরও পেছনে গেলে দেখা যায়, প্রায় ২ হাজার ৮০০ বছর আগে, খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে শুরু হওয়া প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের মাথায় পরানো হতো বিজয়ের মুকুট। এসব মুকুট সাধারণত স্থানীয় উদ্ভিদ যেমন লরেল পাতা বা জলপাই শাখা দিয়ে তৈরি করা হতো। তখন পদকের ধারণাই ছিল না।
১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো পদক প্রদান শুরু হলেও সেখানে মাত্র দুটি পদক দেওয়া হতো। প্রথম স্থান অধিকারী পেতেন রুপার পদক এবং দ্বিতীয় স্থান পাওয়া প্রতিযোগী পেতেন তামার পদক। তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের জন্য কোনো পুরস্কারই নির্ধারিত ছিল না।
এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। সে আসরে কিছু খেলায় প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তখনই স্বর্ণ, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকের ধারণা চালু হয়। তবে সেবার পদকগুলো ছিল আয়তাকার, যা অলিম্পিক ইতিহাসে একমাত্র ব্যতিক্রম। সেই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে পদকের পরিবর্তে ট্রফি বা শিল্পকর্মও দেওয়া হয়েছিল।
১৯০৪ সালের পর থেকে স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ পদকের রীতি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১২ সালের অলিম্পিকে দেওয়া স্বর্ণপদক সত্যিকার অর্থেই খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯১৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় খাঁটি সোনার পদক দেওয়া আর সম্ভব হয়নি।
বর্তমানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পদকের ধাতব গঠন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও, আয়োজক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে পদকে বিশেষ উপাদান যোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন, ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে পদকে জেড পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।
একই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে প্রতিটি পদকের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক আইফেল টাওয়ার–এর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এর মাধ্যমে অলিম্পিক পদক কেবল একটি পুরস্কার নয়, বরং আয়োজক শহরের ইতিহাস ও পরিচয়ের প্রতীক হিসেবেও নতুন মাত্রা পেয়েছে।
সূত্র: ব্রিটানিকা
ইন্টারনেট ছাড়াই চলবে গুগল ম্যাপস: জেনে নিন অফলাইন ব্যবহারের নিয়ম
অচেনা কোনো শহর বা নতুন কোনো গন্তব্যে যাওয়ার পথে বর্তমানে গুগল ম্যাপস আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবে অনেক সময় নেটওয়ার্কের দুর্বলতা কিংবা ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝপথে বিপাকে পড়তে হয়। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা বা বিদেশ ভ্রমণের সময় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবহারকারীদের এই ভোগান্তি দূর করতে গুগল ম্যাপসে রয়েছে ‘অফলাইন’ সুবিধা যা সক্রিয় থাকলে কোনো ধরনের ইন্টারনেট ডাটা ছাড়াই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন মোড ব্যবহারের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর। এটি ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীকে প্রথমে স্মার্টফোনের গুগল ম্যাপস অ্যাপে প্রবেশ করে প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে। সেখানে থাকা 'অফলাইন ম্যাপস' অপশনে গিয়ে ‘সিলেক্ট ইয়োর ওউন ম্যাপ’ নির্বাচন করতে হবে। এরপর যে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহরের মানচিত্র ভবিষ্যতে অফলাইনে ব্যবহারের প্রয়োজন তা জুম ইন বা আউট করে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে ডাউনলোড বাটনে প্রেস করলেই সেই এলাকার মানচিত্রটি ফোনের মেমোরিতে জমা হয়ে যাবে। একবার সফলভাবে ডাউনলোড হয়ে গেলে পরবর্তী যেকোনো সময় ইন্টারনেট ছাড়াই ওই এলাকার পথঘাট দেখা যাবে।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন সংস্করণে গাড়ি চালানোর দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুবিধা থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় রাস্তার রিয়েল-টাইম ট্রাফিক পরিস্থিতি বা জ্যামের খবর জানা সম্ভব হয় না। এছাড়া বিকল্প রুট এবং গণপরিবহনের সঠিক সময়সূচিও এই মোডে দেখা যাবে না। তবে ইন্টারনেট ছাড়াই স্মার্টফোনের জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সবসময় সক্রিয় থাকে যা ডাউনলোড করা মানচিত্রের ওপর ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান ও গন্তব্যের দূরত্ব নিখুঁতভাবে দেখাতে পারে।
ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এই ফিচারটি আশীর্বাদস্বরূপ কারণ বিদেশের মাটিতে দামী ইন্টারন্যাশনাল রোমিং বা লোকাল সিম কার্ডের ডাটা খরচ না করেই তারা মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। ভ্রমণের আগেই প্রয়োজনীয় শহরের ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখলে স্মার্টফোনটি অনেকটা পুরোনো আমলের পকেট ম্যাপের মতোই কার্যকর হয়ে ওঠে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অফলাইন নেভিগেশনের এই সুবিধা কেবল ডেটাই সাশ্রয় করে না বরং জরুরি মুহূর্তে পথ হারানোর ভয় থেকেও ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত রাখে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
জিমেইল স্টোরেজ ফুল? টাকা খরচ না করে জায়গা খালি করার ৫ উপায়
বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগাযোগে জিমেইল একটি অপরিহার্য মাধ্যম। তবে গুগলের নির্ধারিত ১৫ জিবি স্টোরেজ দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যবহারকারীরা বিপাকে পড়েন। স্টোরেজ পূর্ণ থাকলে গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইলগুলো প্রাপকের কাছে না পৌঁছে ফিরে আসে অথবা অনেক ক্ষেত্রে নতুন মেইল আসাও বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে গুগল অতিরিক্ত স্টোরেজের জন্য অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার প্রস্তাব দিলেও সামান্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে কোনো খরচ ছাড়াই এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব।
জিমেইলের জায়গা খালি করার জন্য প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ট্র্যাশ এবং স্প্যাম ফোল্ডারের দিকে। সাধারণত মুছে ফেলা ই-মেইলগুলো সরাসরি ডিলিট না হয়ে ট্র্যাশ ফোল্ডারে ৩০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে যা অযথাই স্টোরেজ দখল করে রাখে। নিয়মিত এই ফোল্ডারগুলো ম্যানুয়ালি খালি করার মাধ্যমে অনেকটা জায়গা তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার করা যায়। এছাড়া ই-মেইলের বড় অ্যাটাচমেন্টগুলো স্টোরেজ পূর্ণ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। জিমেইলের সার্চ বক্সে বিশেষ কোড ব্যবহার করে ১০ মেগাবাইটের বেশি সাইজের ই-মেইলগুলো চিহ্নিত করে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো ডিলিট করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা অপ্রয়োজনীয় নিউজলেটার জিমেইলের প্রমোশন ট্যাবে জমে থেকে ইনবক্সকে ভারী করে তোলে। নিয়মিতভাবে এই ধরনের নিউজলেটারগুলো আনসাবস্ক্রাইব করলে ভবিষ্যৎ স্টোরেজ অপচয় রোধ করা যায়। এছাড়া গুগলের ‘ওয়ান স্টোরেজ ম্যানেজার’ টুলটি ব্যবহার করে এক নজরে ড্রাইভ, ফটোস এবং জিমেইলের বড় ফাইলগুলো দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। বড় সাইজের ছবি বা ভিডিও সরাসরি মেইলে না পাঠিয়ে গুগল ড্রাইভের লিংক শেয়ার করাও স্টোরেজ সাশ্রয়ের একটি আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জিমেইলের স্টোরেজ পূর্ণ হওয়া মানেই টাকা খরচ করে নতুন মেমোরি কেনা নয় বরং ডিজিটাল হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাই এর মূল সমাধান। নিয়মিত ইনবক্স পরিষ্কার রাখা এবং ক্লাউড স্টোরেজের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা বছরের পর বছর কোনো চার্জ ছাড়াই জিমেইলের নিরবচ্ছিন্ন সেবা উপভোগ করতে পারবেন। এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে কেবল স্টোরেজই বাঁচবে না বরং জিমেইলের গতি ও কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পাবে।
পাঠকের মতামত:
- চাঁদাবাজবিরোধী আন্দোলন এখন সময়ের দাবি : ডা. শফিক
- বইমেলার পর্দা উঠবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে: দেবেন একুশে পদক
- ৫২ বছরের অপেক্ষা শেষ: আবারও চাঁদে যাচ্ছে মানুষ
- ক্রিকেট থেকে বিতাড়িত মঞ্জুরুল: জাহানারার অভিযোগে বড় অ্যাকশন!
- ইফতারের পরই মাথাব্যথা? জেনে নিন মুক্তির ৫টি সহজ উপায়
- তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সইবে না চীন: ঢাকার বৈঠকে কড়া বার্তা
- ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত করতে বড় অভিযান শুরু
- তারেক রহমান সরকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহী ভারত : প্রণয় ভার্মা
- দায়িত্ব শেষে চিরচেনা আঙ্গিনায় ড. ইউনূস: ফিরলেন কর্মস্থলে
- তিন স্তরের যাচাই শেষে ফ্যামিলি কার্ড: জেনে নিন আবেদনের সব নিয়ম
- ১৮-এর আগেই হাতে আসবে এনআইডি: ইসির নতুন বয়সের ঘোষণা
- ফুল দেবেন না, এখন কাজের সময়, কথা কম কাজ বেশি : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী
- পুলিশে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর: আদাবর ইস্যুতে কঠোর বার্তা
- থার্ড টার্মিনাল দ্রুত চালুর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : বিমানমন্ত্রী
- ২২ ফেব্রুয়ারি শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- ২২ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরপতনের শেয়ার
- ২২ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরবৃদ্ধিকারী শেয়ার
- এত চাপ সত্ত্বেও ইরান কেন ‘নতি স্বীকার’ করছে না: ট্রাম্প
- দলীয় পরিচয়ে চাঁদাবাজিতে ছাড় নয়: ববি হাজ্জাজ
- গণহত্যার বিচার শুরু: কাঠগড়ায় সালমান-আনিসুল
- জিহ্বায় জল আনা স্বাদ: ইফতারে জাদুকরী ফ্রুট কাস্টার্ড রেসিপি
- সচিবালয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূতের চমক: প্রধানমন্ত্রীর হাতে যুবরাজের বিশেষ বার্তা
- সমুদ্র থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইরান
- আজ বিরিয়ানি কোন মসজিদে? সব খবর মিলবে এক ক্লিকেই বিরিয়ানি দিবে অ্যাপে
- ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থভাবে রোজা: সেহরি ও ইফতারের পূর্ণাঙ্গ গাইড
- আজ কিছু মোবাইল সংযোগে সাময়িক নেটওয়ার্ক বিঘ্ন
- দিল্লিতে বড় হামলার ছক: তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশিসহ গ্রেপ্তার ৮
- আজকের টাকার রেট কত? দেখে নিন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার
- লেবুর বাজারে স্বস্তির হাওয়া: হালিপ্রতি দাম কমল প্রায় অর্ধেক
- সৌদি সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা: রমজানে ওমরাহ পালনকারীদের জন্য একগুচ্ছ বার্তা
- হাসনাত-পাটওয়ারীদের পথেই জামায়াত আমির: ইনকিলাব স্ট্যাটাসে নেটদুনিয়ায় তোলপাড়
- টিভির পর্দায় আজকের খেলা: ভারত-বাংলাদেশ ফাইনাল থেকে নর্দান লন্ডন ডার্বি
- আফগান সীমান্তে পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের হানা: টিটিপি ও আইএস আস্তানায় বড় আক্রমণ
- আজ রাজধানীর যেসব এলাকা ও শপিংমল বন্ধ থাকবে
- আবারও বাড়ল স্বর্ণ-রুপার দাম: নতুন দরে নাকাল সাধারণ ক্রেতারা
- ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বৃষ্টির হানা: রাতের তাপমাত্রা কমার নতুন আভাস
- আজ ৪ রমজান: জেনে নিন আজকের ৫ ওয়াক্ত নামাজের সঠিক সময়সূচি
- সকালে বের হওয়ার আগে জেনে নিন আজ রাজধানীতে কোথায় কী কর্মসূচি
- অস্বাভাবিক ব্যয়ের কবলে নতুন দুই মেট্রো রেল: খরচের অঙ্ক আগের চেয়েও দ্বিগুণ
- ববি হাজ্জাজের মাস্টারপ্ল্যান: শিক্ষাক্রমে আসছে তৃতীয় ভাষা
- জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
- ঢাকাসহ ৬ বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর
- ১০ থেকে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ বিল কমবে; কেবল নিয়মিত এই একটি কাজ করলেই
- তাঁবুতে ইফতার ও স্বজন হারানোর হাহাকার: ধ্বংসস্তূপের মাঝে গাজার রমজান
- সিলেটে ৩টি বইয়ের প্রকাশনা উৎসব: প্রধান অতিথি শাবিপ্রবি উপাচার্য ড. সরওয়ার উদ্দিন
- জান দেবো কিন্তু জুলাই দেবো না: ব্যারিস্টার আরমান
- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ
- আগামীকাল ৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
- ভয়ভীতিমুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশ গড়ার অঙ্গীকার করলেন জহির উদ্দিন স্বপন
- অস্থায়ী শুল্কের কবলে বিশ্ব: ১৫০ দিনের জন্য নতুন কর নীতি কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্র
- হু হু করে কমল সোনার দাম
- আবারও বাড়ল স্বর্ণ-রুপার দাম: নতুন দরে নাকাল সাধারণ ক্রেতারা
- চাকরির টাকায় সংসার না চললে ছেড়ে দিন, দুর্নীতির কোনো ক্ষমা নেই: আইনমন্ত্রী
- প্রাথমিকে রোজার ছুটি নিয়ে নতুন তথ্য জানাল অধিদপ্তর
- অগ্নিমূল্য স্বর্ণের বাজার, ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম বাড়লো ২২১৬ টাকা
- বিশ্ববাজারের প্রভাব পড়ল দেশের স্বর্ণবাজারে: আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম
- ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশের অংশবিশেষ
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক হলেন এহসানুল হক মিলন
- আজকের বাজারে স্বর্ণের দর কত? জেনে নিন বাজুসের নতুন মূল্যতালিকা
- মঙ্গলবার টানা ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না যেসব এলাকায়
- আজ বিকেলেই শুরু হচ্ছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ: বাংলাদেশ থেকে কি দেখা যাবে?
- বাজুসের নতুন সিদ্ধান্ত: আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে স্বর্ণের হ্রাসকৃত মূল্য
- আকাশছোঁয়া স্বর্ণের বাজারে কিছুটা স্বস্তি: আজ থেকেই দাম কমছে
- স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রী: কুমিল্লা বরুড়াবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে চান জাকারিয়া তাহের
- স্বর্ণের বাজারে টানা দরপতন: দুই দফায় কমল প্রায় সাড়ে ৫ হাজার টাকা