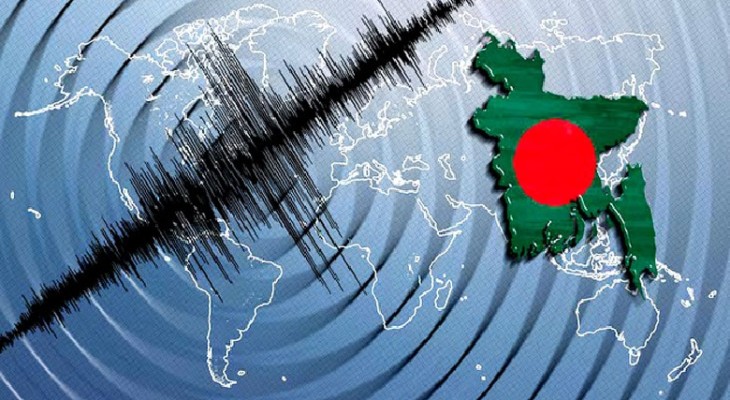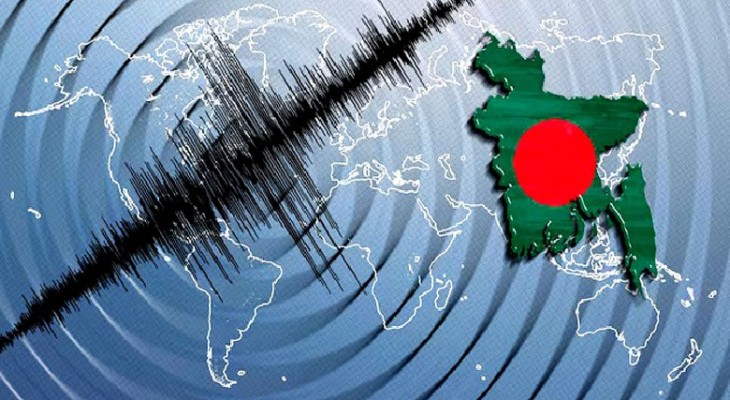জলবায়ু পরিবর্তন
ড্রোনে ফিরছে বন: দাবানলে পুড়ে যাওয়া কানাডায় গাছ লাগাচ্ছে প্রযুক্তি

উত্তর কানাডার কোয়েবেক প্রদেশের পুড়ে যাওয়া বনভূমির আকাশে উড়ছে বিশাল এক ড্রোন। নিচে সে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশেষ প্রযুক্তির ‘বীজ ক্যাপসুল’, যার ভেতরে শুধু বীজ নয়, রয়েছে পানি, পুষ্টি ও জীবাণুর সংমিশ্রণ প্রতিষেধক—সব মিলিয়ে বন পুনরুদ্ধারে এক অভিনব বৈপ্লবিক প্রয়াস।
২০২৩ সালের গ্রীষ্মে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল এই অঞ্চল। চলতি বছর দ্বিতীয়বারের মতো শুরু হয়েছে ড্রোন-নির্ভর এই পুনরায় বনায়ন প্রকল্প। নেতৃত্ব দিচ্ছে কানাডাভিত্তিক পরিবেশপ্রযুক্তি সংস্থা Flash Forest, যারা গত পাঁচ বছর ধরে বেছে বেছে নতুন পুড়ে যাওয়া বনাঞ্চলগুলোতে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আসছে।
কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্যামেরন জোনস বলেন, “আমরা এমন সব বনাঞ্চলে ড্রোন পাঠাই, যেগুলো সাম্প্রতিক সময়েই পুড়েছে। পুরোনো বনভূমিতে সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে আগাছা বা গুল্ম জন্মে, যা নতুন গাছের বৃদ্ধিতে বাঁধা দেয়।”
প্রতিটি ড্রোন দৈনিক ৫০,০০০ বীজযুক্ত ক্যাপসুল ছিটাতে সক্ষম, যা এক দিনে বিশাল এলাকা জুড়ে পুনরায় গাছ রোপণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
এই প্রকল্পে কাজ করছেন ভূ-তথ্য বিশ্লেষক ও ড্রোন অপারেটর ওউয়েন লুকাস। তাঁর ভাষায়, “আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে আগে থেকেই ভৌগলিক ও জলবায়ু-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করি। এরপর নির্ধারিত অঞ্চলেই বীজ ফেলি, যাতে গাছ গজানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে।”
ড্রোন ছিটানো এই বীজগুলো সাধারণ বীজ নয়। এগুলো কৃত্রিম ক্যাপসুলে সুরক্ষিত, যার ভেতরে রয়েছে পানি, প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, এবং গাছের বেড়ে ওঠায় সহায়ক ছত্রাক বা ফাঙ্গাস। এই প্রযুক্তি বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়।
দাবানলের প্রকোপে ২০২৩ সালে কানাডা জুড়ে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ হেক্টর বনভূমি পুড়ে যায়—দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড। চলতি বছরও ইতোমধ্যে ৪.২ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি বনভূমি আগুনে ছারখার হয়েছে।
ফ্ল্যাশ ফরেস্ট শুধু কোয়েবেকেই নয়, আলবার্টা ও যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতেও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বনায়নের কাজ করছে। তবে এখনই কিছু চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট হয়ে উঠছে—বিশেষত বীজ সংকট। গাছের উপযোগী বীজ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন ফরেস্ট ইকোলজি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ম্যাক্সেন্স মার্টিন।
“বোরিয়াল (উত্তরাঞ্চলীয়) অরণ্যের গাছগুলো সাধারণত দাবানলে অভিযোজিত,” বলেন তিনি। “কিন্তু এখনকার জলবায়ু পরিস্থিতিতে যেভাবে অল্পবয়সী বনও ধ্বংস হচ্ছে, সেখানে পুনরায় বনায়নের একমাত্র উপায় দ্রুত বীজ রোপণ।”
স্থানীয় আদিবাসী ক্রী (Cree) সম্প্রদায়-এর নেত্রী অ্যাঞ্জেল মিয়ানস্কুম বলেন, “আমাদের বন হারিয়ে যাওয়াটা খুবই দুঃখজনক। তবে এই নতুন প্রযুক্তি আশার আলো দেখাচ্ছে।” উল্লেখযোগ্য যে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো, কারণ তারা বসবাস করে বনভূমির গভীরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে।
তবে প্রযুক্তির কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে—অনেক সময় ছিটানো বীজ নষ্ট হয়ে যায় বা অনুপযুক্ত স্থানে পড়ে যায়। আর এখন সবচেয়ে বড় সংকট হলো মানসম্পন্ন বীজের স্বল্পতা, যা এ উদ্যোগকে টেকসই করতে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করেই কানাডা এখন চাইছে হারানো বন ফিরিয়ে আনতে—তাও আবার ড্রোন আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায়। প্রকৃতির ক্ষত মেরামত করতে প্রযুক্তির এই উদ্যোগ হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের রোল মডেল।
-এম জামান, নিজস্ব প্রতিবেদক
আসছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ: হাড়কাঁপানো শীতের পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া অফিস
সারা দেশে পৌষের মাঝামাঝি সময়ে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। যদিও আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে এখন পর্যন্ত শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়নি, তবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে যাওয়ায় এবং দিনের বেলা সূর্যের দেখা না মেলায় কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে, সোমবার ভোরে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে দেশের সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ঢাকায় সর্বনিম্ন ১৩.৮ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পার্থক্য ছিল মাত্র ১.৭ ডিগ্রি, যার ফলে রাজধানীবাসী হাড়কাঁপানো শীতের কবলে পড়েছেন।
আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা জানিয়েছেন, আগামী ১ থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা খুব একটা না কমলেও ৬ জানুয়ারি থেকে পারদ নামতে শুরু করবে। এরপর ৮ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি) এই শৈত্যপ্রবাহের নাম দিয়েছে ‘কনকন’। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারির মধ্যে এই শৈত্যপ্রবাহের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ দেখা যাবে, বিশেষ করে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রিতে নেমে আসতে পারে।
কুয়াশার তীব্রতার কারণে মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এই সময়ে মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে, যার ফলে বিমান, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেটসহ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে শীতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকবে। তবে বরিশাল ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব তুলনামূলক কম হতে পারে। শীতের এই বৈরী পরিস্থিতিতে শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।
২১০০ সালের মধ্যে ২০ কোটি মানুষ ঘরহারা হতে পারে, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ চিত্র
বিশ্বজুড়ে গরম বেড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায় তবে অধিকাংশ বাসযোগ্য এলাকায় পরিস্থিতি এখনো মানুষের জন্য জীবনযাপন অসহনীয় নয়। বিশেষ করে শুষ্ক অঞ্চলে গরম হলেও শরীর ঘাম দিয়ে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কপালে ভাঁজ ফেলছে এমন কিছু জায়গা যেখানে গরমের সঙ্গে আর্দ্রতাও বেশি থাকে। মধ্যপ্রাচ্য পাকিস্তান ও ভারতের কিছু এলাকায় গরমে সামুদ্রিক আর্দ্রতা যুক্ত হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে। সেখানে ঘাম দ্রুত বাষ্পীভূত হয় না তাই শরীর ঠাণ্ডা হয় না এবং দীর্ঘ সময় থাকলে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।
গবেষকরা ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার ব্যবহার করে এই ঝুঁকি মাপেন। যদি ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় তবে শরীর যথেষ্ট তাপ বের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ২০২৪ সালের মে মাসে দিল্লিতে তাপমাত্রা ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালে অনেক মানুষ তাপদাহে মারা গিয়েছিলেন। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক গরম এবং আর্দ্রতা আরও বেশি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গালফ কোস্ট ও মরুভূমি এলাকায় যেখানে কৃষিকাজে জল স্প্রে করা হয় সেসব অঞ্চলেও গরম ও আর্দ্রতার ঝুঁকি বাড়ছে।
জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলছেন যখন আমরা কয়লা তেল বা গ্যাস জ্বালাই তখন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় যা বায়ুমণ্ডলে জমে সূর্যের তাপ ধরে রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু গরমের সমস্যা নয় বরং এটি আগুন খরা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও বন্যার ঝুঁকি বাড়ায়। একুশ শতকের শেষ নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রায় ২০ কোটি মানুষ বাসস্থান হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি ও অর্থনীতিও মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে।
খারাপ খবর হলো যতক্ষণ আমরা কার্বন জ্বালাব তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে। তবে ভালো খবর হলো আমরা সোলার ও উইন্ড পাওয়ারের মতো পরিচ্ছন্ন শক্তি ব্যবহার করে কার্বন নির্গমন কমাতে পারি। গত ১৫ বছরে পরিষ্কার শক্তি আরও সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য হয়েছে এবং প্রায় সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সম্মত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করেই এই পৃথিবী বাসযোগ্য রাখা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
তথ্যসূত্র : এনডিটিভি
২৫০ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ কি বড় ভূমিকম্পের দ্বারপ্রান্তে?
বাংলাদেশ আবারও একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত এই সকালের কম্পন খুব বেশি ক্ষতি না করলেও বিশেষজ্ঞদের মতে এটি মোটেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং উপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক সিসমিক সক্রিয়তার অংশ। আজকের ভূমিকম্প বাংলাদেশের দীর্ঘ ভূমিকম্প-ইতিহাসকে নতুনভাবে সামনে এনেছে এবং দেখিয়েছে যে দেশটি এখনো বড় ধরনের কম্পনের ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়।
দেশের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান এমন যে বাংলাদেশের নিচ দিয়ে তিনটি টেকটোনিক প্লেটের চাপের রেখা চলে গেছে। এই কারণে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ নানা সময়ে বড় কম্পনের অভিঘাত সহ্য করেছে। ১৭৬২ সালের আরাকান ভূমিকম্প যার মাত্রা প্রায় ৮ দশমিক ৮ ধরা হয়, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার উপকূলের বৃহৎ ভূমি পরিবর্তন ঘটায়। উপকূলের অনেক অংশ নিচে নেমে যায় এবং কোথাও কোথাও নতুন চর ও দ্বীপ সৃষ্টি হয়। এই ভূমিকম্প এখনো বাংলাদেশের ভূ-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূ-পরিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত।
১৮৯৭ সালের শিলং ভূমিকম্প ছিল আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা। প্রায় ৮ দশমিক ১ মাত্রার এই ভূমিকম্পে সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং রংপুরসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বহু ভবন ধসে পড়ে, রেললাইন বেঁকে যায় এবং জমিতে দীর্ঘ ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ভূমিকম্প বাংলাদেশের ভূমিকম্প-ঝুঁকির কেন্দ্রীয়তা স্পষ্ট করে দেয়।
এরপর ১৯১৮ এবং ১৯২৩ সালে নেত্রকোনা অঞ্চলে ঘটে দুটি বড় ভূমিকম্প। এই দুই ঘটনার ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি, ধর্মীয় স্থাপন এবং স্থানীয় স্থাপনা ধসের মুখে পড়ে। উপকেন্দ্র ছিল নেত্রকোনা ময়মনসিংহ অঞ্চল। উভয় ঘটনায় প্রাণহানি হওয়ায় কেন্দ্রীয় বাংলাদেশের ভূমিকম্প-সংবেদনশীলতা আবারও সামনে আসে।
উপনিবেশিক যুগের আরেক বড় ঘটনা ১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প। প্রায় ৮ দশমিক ৬ মাত্রার এই কম্পনের উপকেন্দ্র ছিল ভারতের অরুণাচল সীমান্ত, তবে এর ধাক্কা বাংলাদেশেও শক্তভাবে অনুভূত হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বহু স্থাপনায় ফাটল দেখা দেয়।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মাঝারি মাত্রার একাধিক ভূমিকম্প ঘটে। ১৯৮৮ সালের সিলেট ভূমিকম্পে বহু ভবনে ফাটল ও ধসের ঘটনা ঘটে। ১৯৮৯ সালে খুলনা অঞ্চলে এবং ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি, স্থাপনা ও পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে এবং প্রাণহানি হয়। ১৯৯৯ সালে মহেশখালী দ্বীপে ভূমিকম্পে অন্তত ছয়জন নিহত হন। ২০০৩ সালে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুভূত কম্পন আবারও পাহাড়ধসসহ নানা ক্ষতি তৈরি করে।
সাম্প্রতিক সময়েও সিসমিক সক্রিয়তা বাংলাদেশের জন্য নতুন চিন্তার কারণ। ২০১৬ সালে মণিপুর ভূমিকম্প, ২০১৭ সালে ত্রিপুরার ভূমিকম্প এবং ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ধারাবাহিক ছোট মাঝারি ভূমিকম্প দেশের প্রস্তুতিহীনতার বিষয়টি সামনে আনে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের আশপাশে ২ মাত্রার বেশি শক্তির একশটিরও বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে অঞ্চলটি এখন অত্যন্ত সক্রিয় এবং বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি বিদ্যমান।
আজকের ভূমিকম্পও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। কম গভীরতার কারণে কম্পনটি বহু এলাকায় তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ঘনবসতি, দুর্বল ভবন, নরম পলিমাটি এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন বাংলাদেশের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে অল্প শক্তির ভূমিকম্পও বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় বিপদের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় এমন ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং ছোট কম্পনগুলো দেখাচ্ছে ভূতলের নিচে টেনশন জমছে যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ভূমিকম্পের ইঙ্গিত হতে পারে।
বাংলাদেশের দীর্ঘ ইতিহাস, সাম্প্রতিক সিসমিক প্যাটার্ন এবং আজকের ভূমিকম্প মিলিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। দেশটি ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে কখনোই নিরাপদ ছিল না এবং এখনো নয়। উন্নত ও ভূমিকম্প সহনশীল নির্মাণ, কড়া বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি যুক্ত করা এবং জনগণকে সচেতন করা এখন সময়ের দাবি।
আজকের ভূমিকম্প আমাদের কী শিক্ষা দিচ্ছে: একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
আজকের ভূমিকম্প বাংলাদেশের মানুষকে আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে ভূমিকম্প এদেশে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় বরং একটি স্থায়ী বাস্তবতা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত কম্পনটি স্বল্প সময়ের হলেও এটি মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং অনেকে ভবন থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই ভূমিকম্প ভবিষ্যতের আরও বড় সম্ভাব্য বিপদের সতর্ক সংকেত হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।
বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এবং এটি বহুদিনের বাস্তবতা
বাংলাদেশ এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখানে পৃথিবীর তিনটি বড় টেকটোনিক প্লেট পরস্পরের সংযোগস্থলে রয়েছে। ইন্ডিয়ান প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মা মাইক্রো প্লেটের সংঘর্ষপ্রবণ অবস্থান বাংলাদেশকে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। বিশেষ করে ইন্ডো বার্মা সাবডাকশন জোনে দীর্ঘদিন ধরে টেকটোনিক চাপ জমে আছে যা বড় মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা বলছে এই অঞ্চলে শক্তি সঞ্চয়ের প্রকৃতি বিবেচনায় ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা রয়েছে।
ছোট বা মাঝারি মাত্রার কম্পন ঘন ঘন অনুভূত হওয়া এই অঞ্চলের সক্রিয়তার একটি স্বাভাবিক ইঙ্গিত। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ফল্ট লাইনগুলো সক্রিয় রয়েছে এবং সিসমিক গতিবিধির ধারাবাহিকতা বজায় আছে। তাই বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির দিক থেকে একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বাস্তব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
ঘনবসতি এবং দুর্বল অবকাঠামো আমাদের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে
বাংলাদেশের বড় শহরগুলো, বিশেষ করে ঢাকা, বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ নগর কেন্দ্র। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, অনুমোদনহীন নির্মাণ এবং নরম পলিমাটির ওপর অসংখ্য ভবন নির্মাণ বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উন্নত দেশের মতো এখানে ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনশীলভাবে নির্মাণ করা হয়নি। ফলে একই মাত্রার ভূমিকম্প বিদেশে কম ক্ষতি করলেও বাংলাদেশে অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।
এর পাশাপাশি গ্যাসলাইন, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, সেতু এবং উড়ালসড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোও বড় ভূমিকম্প প্রতিরোধে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত নয়। মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলেও পাইপলাইন বিস্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস বা সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো গৌণ বিপর্যয় ঘটতে পারে। ফলস্বরূপ মৃত্যুহার এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত বাড়তে পারে।
ছোট ছোট কম্পন বড় ভূমিকম্পের শক্তি কমিয়ে দেয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল
বাংলাদেশে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে ছোট ছোট ভূমিকম্প হলে নাকি ভূগর্ভের চাপ মুক্ত হয়ে যায় এবং বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কমে যায়। ভূতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন এই ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার গবেষণা বলছে ছোট ভূমিকম্প বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দূর করে না বরং সক্রিয় ফল্ট লাইনের চলমান ভূ-চাপের একটি সাধারণ ইঙ্গিত।
ইতিহাস বলছে যেসব অঞ্চলে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছে তারও আগে অনেক জায়গায় ছোট কম্পন দেখা গিয়েছে। তাই ছোট ভূমিকম্পকে নিরাপত্তার লক্ষণ হিসেবে দেখা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বরং এগুলো ভূগর্ভে সিসমিক শক্তির সক্রিয়তার একটি সতর্ক সংকেত যা মানুষকে আরও সচেতন ও প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।
নির্দিষ্ট সময় ধরে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়
প্রতি ভূমিকম্পের পরই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে অমুক সময়ে বা নির্দিষ্ট ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বড় ভূমিকম্প হবে। এসব দাবি মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। কিন্তু পৃথিবীর কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্থা এখনো নির্দিষ্ট দিন, সময় বা ঘণ্টা ধরে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়নি। ভূমিকম্প একটি অত্যন্ত জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং এর সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা এখনো বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে।
কেবল ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, সম্ভাব্য মাত্রা এবং সিসমিক সক্রিয়তার ধরণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় ধরে ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী শুধুই গুজব এবং আতঙ্ক ছড়ানোর একটি পদ্ধতি। তাই ভূমিকম্প সংক্রান্ত তথ্য জানতে সর্বদা বৈজ্ঞানিক উৎসের ওপর নির্ভর করা এবং গুজবকে প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত জরুরি।
আজকের ভূমিকম্প ছিল সতর্ক সংকেত
আজকের ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাস্তব এবং যেকোনো সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে। ভূ-অবস্থান, সক্রিয় ফল্ট লাইন, ঘনবসতি, দুর্বল ভবন এবং প্রস্তুতিহীনতা বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা। ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তবে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব যদি বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, নগর পরিকল্পনায় ভূমিকম্প ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জনগণকে বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক প্রস্তুতি শেখানো হয়।
ভূমিকম্পের প্রধান কারণ গুলো কি কি
সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভূতত্ত্ববিদরা। তাদের মতে, ভূমিকম্পের প্রধান কারণ হলো পৃথিবীর নিচের স্তরে টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত নড়াচড়া। তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, শিলাস্তরে ফাটল সৃষ্টি হওয়া, ভূমিধস এবং মানুষের বিভিন্ন কার্যক্রমও এই ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।
টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়াই বড় কারণ
বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যায়, পৃথিবীর ভূত্বক বিশাল কয়েকটি টেকটোনিক প্লেট নিয়ে গঠিত, যেগুলো সবসময় নীরবে নড়াচড়া করে। যখন এই প্লেটগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়, দূরে সরে যায় বা ঘর্ষণ তৈরি করে, তখন শিলাস্তরে প্রচণ্ড চাপ জমা হয়। কোনো এক পর্যায়ে এই চাপ হঠাৎ মুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর কম্পন তৈরি করে যাকে আমরা ভূমিকম্প বলে জানি।
দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলকে ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা পুরো অঞ্চলে শিলাস্তরের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করছে।
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও সৃষ্টি করে কম্পন
বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে ভূমিকম্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আগ্নেয়গিরির ভেতরে গলিত লাভা ও গ্যাস যখন জোরে বের হয়ে আসে, তখন ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে। এটিকে আগ্নেয় কম্পন বলা হয়।
শিলাস্তরে ফাটল ও শিলাচ্যুতি
ভূপৃষ্ঠের গভীরে শিলাস্তরের ভেতর ছোট বা বড় ফাটল তৈরি হলে সেখানে একধরনের শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। এই শক্তি যখন হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে, তখন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, এই ধরনের ভূমিকম্প কখনও খুবই তীব্র হতে পারে কারণ এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে জমা হওয়া চাপ একসঙ্গে মুক্ত করে।
ভূমিধসে সৃষ্টি হতে পারে ভূমিকম্পের মতো ঝাঁকুনি
বৃহৎ আকারের ভূমিধসে ভূমি দ্রুত নিচে নেমে যেতে থাকে, যার ফলে সৃষ্ট কম্পন মানুষের কাছে ভূমিকম্পের মতো অনুভূত হয়। পাহাড়ি বা ভঙ্গুর মাটির অঞ্চলে এই ঝুঁকি বাড়ে।
মানবসৃষ্ট কারণেও বাড়ছে ভূমিকম্প
যেখানে পৃথিবী কোটি কোটি বছর ধরে স্বাভাবিকভাবে ভূমিকম্প সৃষ্টি করছে, সেখানে সাম্প্রতিক যুগে মানুষের কার্যকলাপও এই ঝুঁকিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
খনি বিস্ফোরণ
গভীর খনিতে বিস্ফোরণ চালালে মাটির নিচের স্থিতি নষ্ট হয়ে কম্পন তৈরি হতে পারে।
হাইড্রোলিক ফ্র্যাকচারিং বা ফ্র্যাকিং
প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে ব্যবহৃত এই পদ্ধতিতে উচ্চচাপে তরল ঢুকিয়ে শিলাস্তর ভাঙা হয়। এর ফলে ছোট থেকে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প দেখা দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চীনে এই ধরনের ভূমিকম্প বেশ কয়েকবার নথিবদ্ধ হয়েছে।
পারমাণবিক পরীক্ষা
ভূগর্ভে পরিচালিত পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে শক্তিশালী কম্পন সৃষ্টি হয়, যা আশপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্পের মতো প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা
দুর্যোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাকৃতিক কারণগুলো মানবনিয়ন্ত্রিত নয়, তবে মানবসৃষ্ট ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব। একইসঙ্গে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভবন নির্মাণবিধি কঠোরভাবে মানা হলে ভূমিকম্পে প্রাণহানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যাবে।
পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা: ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধের কারণ

সাদিক আহমেদ প্রান্ত
পরিবেশ কর্মী ও কলাম লেখক
এক সময় বাংলাদেশের নদীগুলো ছিল জীবনের উৎস। কৃষকরা নদীর পানি ব্যবহার করে জমিতে সেচ দিতেন, খাল-বিল ছিল মাছ ও কৃষির আশ্রয়স্থল। চারদিকে ছিল অফুরন্ত পানির সরবরাহ, আর পানির সংকট তখন কারো কল্পনাতেও আসেনি। কিন্তু আজ সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বিশুদ্ধ পানির অভাব এখন এক বৈশ্বিক সংকট, যা ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।
জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দশকে পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হবে মিঠা পানির সংকট। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানির অভাবে ভুগবে। বর্তমানে বিশ্বের ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানির সেবা থেকে বঞ্চিত, এবং ২০২২ সালে ৭৮৩ মিলিয়ন মানুষ ভুগেছে অপুষ্টিতে। অন্যদিকে ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯৮০ কোটিতে, যা পানি ও খাদ্য উভয়ের ওপর ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করবে।
পানি আজ কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এটি এখন এক ভূরাজনৈতিক ইস্যু। একবিংশ শতাব্দীতে দেশগুলোর মধ্যে পানি সংকট নিয়ে টানাপোড়েন বাড়ছে, যা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়। মিশর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে নীলনদকে কেন্দ্র করে বিরোধ, ভারত ও পাকিস্তানের সিন্ধু চুক্তি নিয়ে উত্তেজনা, কিংবা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পানি বণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের দীর্ঘ আলোচনাই প্রমাণ করছে যে ভবিষ্যতের সংঘাতের কেন্দ্রে থাকবে পানি। অতীতে যুদ্ধ হয়েছে তেল ও ভূমির জন্য, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে পানির জন্য। বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবার্তা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব সম্ভাবনা।
পানির সংকট কেবল পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈষম্যের প্রশ্নেও পরিণত হয়েছে। ২০১১ সালে চিলির কোকিম্বো অঞ্চলে পানি সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ করা হলে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী মারাত্মক সংকটে পড়ে। আবার ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরে “ডে জিরো” ঘোষণা করা হয়, যখন প্রতিজন নাগরিককে দিনে মাত্র ৫০ লিটার পানি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলো দেখায় যে পুঁজিবাদী বিশ্বে পানি এখন বাজারে বিক্রি হওয়া এক পণ্য, যার মূল্য নির্ধারিত হয় মুনাফার ভিত্তিতে, মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয়।
জলবায়ু পরিবর্তন একসঙ্গে প্রভাব ফেলছে পানির প্রাপ্যতা ও খাদ্য উৎপাদনে। হিমবাহ গলে যাচ্ছে, নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটিকে বিষাক্ত করছে, ফলে ফসলের উৎপাদন কমছে এবং খাদ্য ঘাটতি বাড়ছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, জলাশয় দখল ও অতিরিক্ত পাম্পিংয়ের ফলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নামছে। এর ফলে কৃষি, মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য সবকিছুই হুমকির মুখে পড়ছে।
পানির অভাব সরাসরি প্রভাব ফেলছে খাদ্য নিরাপত্তায়। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়, অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়, আর দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবেই পানি সংকট ও খাদ্য সংকট এখন একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো আছে। মানবজাতি ইতিমধ্যেই এমন অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা পানি ও খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। হাইড্রোপনিক ও ভার্টিক্যাল ফার্মিং শহুরে কৃষিতে এক নতুন দিগন্ত খুলেছে। এতে প্রচলিত কৃষির তুলনায় ৯০ শতাংশ পানি সাশ্রয় হয় এবং ফলন ১০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ড্রিপ সেচ প্রযুক্তি ফসলের শিকড়ে সরাসরি পানি পৌঁছে দিয়ে অপচয় কমায় ও উৎপাদন বাড়ায়। বায়োটেকনোলজির অগ্রগতিতে তৈরি হয়েছে এমন ফসল, যা খরা, লবণাক্ততা বা অতিরিক্ত তাপমাত্রার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য তৈরি করা হয়েছে ‘ড্রট-রেসিস্ট্যান্ট’ ধান ও গমের জাত, যা স্বল্প পানিতে উৎপাদন সম্ভব করছে।
পানিশোধনের ক্ষেত্রেও এসেছে নতুনত্ব। রিভার্স অসমোসিস, লাইফস্ট্র, এবং ইলেক্ট্রোডায়ালাইসিস প্রযুক্তি দূষিত পানিকে বিশুদ্ধ করছে। যদিও এসব প্রযুক্তি এখনো ব্যয়বহুল, কিন্তু সহযোগিতা ও ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে এগুলোকে সুলভ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, ইসরাইল তার ব্যবহৃত বৃষ্টির ৮৫ শতাংশ পানি পুনর্ব্যবহার করে, যা বিশ্বে অন্যতম সেরা উদাহরণ।
যত উন্নত প্রযুক্তিই উদ্ভাবিত হোক, যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে পানির অপচয় বন্ধ না করা যায়, তবে কোনো প্রযুক্তিই টেকসই সমাধান দিতে পারবে না। প্রতিটি ফোঁটা পানি অপচয় মানে একটি প্রাণের জন্য হুমকি। এখনই প্রয়োজন সচেতনতা ও মনোভাবের পরিবর্তন।
বিশ্বের সীমান্তনদীগুলোর পানি বণ্টন এখন এক জটিল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা। জাতিসংঘের উচিত আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করে নিশ্চিত করা যে কোনো দেশ একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে অন্য দেশের পানি প্রবাহ বন্ধ করতে না পারে। একই সঙ্গে দরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর। বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃষি উদ্ভাবন যেন কেবল ধনী দেশ বা কোম্পানির একচেটিয়া সম্পদ না হয়, বরং তা বৈশ্বিক মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়।
বিশ্ব দ্রুত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে, যেখানে পানি ও খাদ্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নির্ভর করবে আজ আমরা কীভাবে এই সম্পদ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ন্যায্যভাবে বণ্টন করি তার ওপর। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সম্মিলিত প্রয়াস, সঙ্গে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই আসন্ন সংকট মোকাবিলার একমাত্র কার্যকর পথ।
আমাদের যুদ্ধ হোক অস্ত্রের নয়, সচেতনতার, সংযমের ও মানবিকতার। যখন আমরা অবহেলায় পানি নষ্ট করি, তখন পৃথিবীর কোথাও কেউ তৃষ্ণায় কাতরায়।
লেখক: সাদিক আহমেদ প্রান্ত,পরিবেশ কর্মী ও কলাম লেখক,কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
যোগাযোগ: [email protected]
ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকা এবং আশেপাশের এলাকায় বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এ কারণে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।
সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকার আকাশ আংশিকভাবে থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এ সময়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
বাতাস দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে।
সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৫ শতাংশ। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হবে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৫টা ২১ মিনিটে, এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৪ মিনিটে।
একই সঙ্গে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১২০ ঘণ্টার সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ জায়গা, খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গা, এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গা আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে।
এ ছাড়া, সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে। আবহাওয়াবিদরা মনে করাচ্ছেন, নাগরিকরা হঠাৎ বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত থাকলে দুর্ভোগ এড়ানো সম্ভব।
‘আর ফেরার উপায় নেই’: জলবায়ু সংকটে পৃথিবীর ইকোসিস্টেম বিপন্ন
বৈশ্বিক উষ্ণতা যে আগের সব পূর্বাভাসকে অতিক্রম করে ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে, তার এক কঠোর প্রমাণ এখন সামনে। বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরগুলো (Coral Reefs) প্রায় অপরিবর্তনীয় মৃত্যুযাত্রায় পৌঁছে গেছে—যা বিজ্ঞানীদের ভাষায় পৃথিবীর প্রথম ‘জলবায়ুজনিত ইকোসিস্টেম ধসের টিপিং পয়েন্ট’। সোমবার প্রকাশিত গ্লোবাল টিপিং পয়েন্টস রিপোর্টে এ সতর্কবার্তা দিয়েছেন ১৬০ জন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী।
এই প্রতিবেদনটি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ইকোসিস্টেম কোন পর্যায়ে পৌঁছালে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়—তা নিরূপণ করেছে বৈজ্ঞানিকভাবে। এবারের এই অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ প্রকাশিত হলো এমন এক সময়, যখন ব্রাজিলের আমাজন বনাঞ্চলের কিনারায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩০ (COP30)।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি প্রাক-শিল্প যুগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বেড়ে যায়, তবে বিশ্বের বৃহত্তম রেইনফরেস্ট আমাজনও ধসের মুখে পড়বে। এর আগের হিসাব অনুযায়ী, এই সীমা কিছুটা বেশি ধরা হয়েছিল, যা এখন কমিয়ে আনতে হয়েছে বননিধনের গতি ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে।
আরও উদ্বেগজনক হলো, বৈশ্বিক উষ্ণতা অব্যাহত থাকলে বিপর্যস্ত হতে পারে পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র স্রোত অ্যাটলান্টিক মেরিডিওনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন (AMOC)—যা উত্তর ইউরোপের শীতকালকে সহনীয় রাখে। এর ধস বিশ্ব আবহাওয়ার ভারসাম্যকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে।
ব্রিটেনের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞানী এবং প্রতিবেদনের প্রধান লেখক টিম লেন্টন বলেন, “পরিবেশে পরিবর্তন এখন দ্রুত ও ভয়াবহ গতিতে ঘটছে—বিশেষ করে জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে। আমরা আসলে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি।”
আশার কিছু আলোও আছে
তবে হতাশার মাঝেও কিছু আশার ইঙ্গিত দেখছেন গবেষকরা। টিম লেন্টন বলেন, “আমরা এখনো সম্পূর্ণ অসহায় নই। আমাদের হাতে পরিবর্তনের সুযোগ আছে।” তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের পরিমাণ প্রথমবারের মতো কয়লাচালিত বিদ্যুতের চেয়ে বেশি হয়েছে—যা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।
এই সাফল্যকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীরা নভেম্বরের কপ৩০ সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন দ্রুত কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়।
জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই প্রাক-শিল্প যুগের চেয়ে ১.৩ থেকে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রকৃতিতে পরিবর্তন যেভাবে দ্রুত ঘটছে, তা তাদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ।
উষ্ণতম বছর ও প্রবাল মৃত্যুযাত্রা
গত দুই বছর পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণ বছর হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে সাগরে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ, যা পৃথিবীর ৮৪ শতাংশ প্রবাল প্রাচীরকে ব্লিচিং (রঙ হারিয়ে ফেলা) ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ এই প্রবাল প্রাচীরই সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশের আশ্রয়স্থল।
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রবালগুলোকে বাঁচাতে হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আবারও ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে—যা সম্ভব হবে কেবল বৈশ্বিক জলবায়ু উদ্যোগে বিপ্লব ঘটলে।
অস্ট্রেলিয়ার সিএসআইআরও (CSIRO) জলবায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী পেপ কানাডেল বলেন, “নতুন প্রতিবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে, প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের পরিসর ও তীব্রতা বাড়ছে।”
বর্তমান নীতিমালা অনুসারে, পৃথিবী এই শতাব্দীর শেষে প্রায় ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধির পথে রয়েছে—যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য এক অশনিসংকেত।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে শুধু প্রবাল প্রাচীর বা আমাজন নয়—পৃথিবীর বহু প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই ধ্বংসের অপ্রতিরোধ্য পথে এগোবে। সময় ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু আশার আলো এখনো নিভে যায়নি—শুধু দরকার বিশ্বনেতাদের সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও মানবজাতির সম্মিলিত উদ্যোগ।
-এম জামান
ইউরোপের পরিবেশ সংকট: অগ্রগতি সত্ত্বেও সতর্কবার্তা ইইএ’র
ইউরোপ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশ রক্ষা ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ক্ষতি মোকাবিলায় মহাদেশটিকে আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে—সোমবার প্রকাশিত ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি (ইইএ)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে এমনই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিন দশকে ইউরোপ উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ও বায়ুদূষণ কমাতে সক্ষম হলেও সামগ্রিকভাবে মহাদেশটির পরিবেশের অবস্থা ‘ভালো নয়’। ১৯৯০ সালের তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমেছে ৩৭ শতাংশ, যা যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের মতো বড় দূষণকারীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং ২০০৫ সাল থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্বিগুণ বৃদ্ধির ফলে এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।
তবুও ইইএ মনে করে, ইউরোপীয় দেশগুলোকে ইউরোপীয় গ্রিন ডিলের অধীনে ইতোমধ্যেই গৃহীত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা আরও জোরালোভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ মহাদেশটির প্রকৃতি ক্রমেই অবনতি ও অতিরিক্ত শোষণের শিকার হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ৮১ শতাংশ সুরক্ষিত আবাসস্থল খারাপ বা খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে, ৬০-৭০ শতাংশ মাটি দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৬২ শতাংশ জলাশয় স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নেই।
জল এখন ক্রমশ বিরল হয়ে পড়ছে এবং কৃষি, পানি সরবরাহ ও জ্বালানি খাতে দক্ষ শাসনব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পানি পুনঃব্যবহার ও জনসচেতনতা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পানি সাশ্রয় করা সম্ভব বলে মনে করে ইইএ। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি নয় বরং পরোক্ষভাবে অবকাঠামো ও ইকোসিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে তুলছে।
প্রতিবেদনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, ইউরোপের অধিকাংশ ভবন প্রচণ্ড গরম সহ্য করার মতোভাবে নির্মিত নয় এবং মহাদেশের ১৯ শতাংশ মানুষ নিজের ঘর আরামদায়ক তাপমাত্রায় রাখতে সক্ষম নয়। যদিও তাপপ্রবাহের প্রকোপ বাড়ছে, ইইএ’র ৩৮টি সদস্য দেশের মধ্যে মাত্র ২১টি দেশে গরম মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।
ক্রমবর্ধমান আর্থিক ক্ষতি
১৯৮০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপে তাপপ্রবাহ, বন্যা, ভূমিধস ও দাবানলের মতো চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনায় ২ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রাও বেড়েছে কয়েকগুণ—২০২০ থেকে ২০২৩ সময়কালে বার্ষিক গড় ক্ষতি ২০১০-২০১৯ সময়কালের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি। শুধু ২০২৩ সালে স্লোভেনিয়ার বন্যার ক্ষতি দেশটির জিডিপির ১৬ শতাংশের সমান।
ইইএ-এর টেকসই উন্নয়ন ইউনিটের প্রধান ক্যাথরিন গ্যানজলেবেন সতর্ক করে বলেন, “মানব টিকে থাকার জন্য উচ্চমানের প্রকৃতি অপরিহার্য। এখনই যদি পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, ভবিষ্যতে খরচ ও ক্ষতি আরও বেশি হবে।”
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দূষণ প্রতিরোধ মানুষের মৃত্যু ও রোগের সংখ্যা কমায়। সূক্ষ্ম ধূলিকণার কারণে হওয়া অকাল মৃত্যুর হার ২০০৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪৫ শতাংশ কমেছে, যা এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।
-এম জামান
পাঠকের মতামত:
- একই দিনে ধুরন্ধর ২ ও টক্সিক: মুখোমুখি লড়াইয়ে বড় ক্ষতির শঙ্কা
- ৬ সিটি পেল নতুন ৬ প্রশাসক: দায়িত্বে বিএনপির একঝাঁক হেভিওয়েট নেতা
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দিন: নতুন দিগন্তের সূচনা
- ভোটের সময় হলো বলে! সিটি নির্বাচন নিয়ে বড় আপডেট দিলেন ফখরুল
- টাকার বিপরীতে ডলারের দাপট: এক নজরে আজকের মুদ্রার রেট
- এখতিয়ারবহির্ভূত সড়ক ইজারা দিয়েছে কুমিল্লা জেলা পরিষদ
- সব রেকর্ড ভাঙল স্বর্ণ! আজ থেকে নতুন রেট কার্যকর
- ১৮ মাসের নীরবতা ভেঙে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ: মুকসুদপুরে উত্তেজনা
- হাসনাত আব্দুল্লাহ কই? লীগ তো দোকান খোলা শুরু করছে: নাসীরুদ্দীন
- ববি হাজ্জাজের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ খেলাফত মজলিস
- আড়ালে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে? ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ
- জেন-জি’র মিছিলে উত্তাল তেহরান: স্বৈরাচারবিরোধী স্লোগানে কাঁপছে ইরান
- বৃষ্টি আসছে ৪ বিভাগে: আবহাওয়া দপ্তরের ৫ দিনের বড় সতর্কবার্তা
- আজ সোমবার রাজধানীর যেসব এলাকায় মার্কেট বন্ধ: জেনে নিন তালিকা
- যানজট এড়াতে জেনে নিন আজকের রাজপথের সব কর্মসূচি
- আজ ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
- আজ টানা ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে যেসব এলাকা
- পবিত্র রমজানের ৫ম দিন; জেনে নিন আজকের নামাজের সময়সূচি
- চাঁদাবাজবিরোধী আন্দোলন এখন সময়ের দাবি : ডা. শফিক
- বইমেলার পর্দা উঠবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে: দেবেন একুশে পদক
- ৫২ বছরের অপেক্ষা শেষ: আবারও চাঁদে যাচ্ছে মানুষ
- ক্রিকেট থেকে বিতাড়িত মঞ্জুরুল: জাহানারার অভিযোগে বড় অ্যাকশন!
- ইফতারের পরই মাথাব্যথা? জেনে নিন মুক্তির ৫টি সহজ উপায়
- তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সইবে না চীন: ঢাকার বৈঠকে কড়া বার্তা
- ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত করতে বড় অভিযান শুরু
- তারেক রহমান সরকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহী ভারত : প্রণয় ভার্মা
- দায়িত্ব শেষে চিরচেনা আঙ্গিনায় ড. ইউনূস: ফিরলেন কর্মস্থলে
- তিন স্তরের যাচাই শেষে ফ্যামিলি কার্ড: জেনে নিন আবেদনের সব নিয়ম
- ১৮-এর আগেই হাতে আসবে এনআইডি: ইসির নতুন বয়সের ঘোষণা
- ফুল দেবেন না, এখন কাজের সময়, কথা কম কাজ বেশি : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী
- পুলিশে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর: আদাবর ইস্যুতে কঠোর বার্তা
- থার্ড টার্মিনাল দ্রুত চালুর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : বিমানমন্ত্রী
- ২২ ফেব্রুয়ারি শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- ২২ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরপতনের শেয়ার
- ২২ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরবৃদ্ধিকারী শেয়ার
- এত চাপ সত্ত্বেও ইরান কেন ‘নতি স্বীকার’ করছে না: ট্রাম্প
- দলীয় পরিচয়ে চাঁদাবাজিতে ছাড় নয়: ববি হাজ্জাজ
- গণহত্যার বিচার শুরু: কাঠগড়ায় সালমান-আনিসুল
- জিহ্বায় জল আনা স্বাদ: ইফতারে জাদুকরী ফ্রুট কাস্টার্ড রেসিপি
- সচিবালয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূতের চমক: প্রধানমন্ত্রীর হাতে যুবরাজের বিশেষ বার্তা
- সমুদ্র থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইরান
- আজ বিরিয়ানি কোন মসজিদে? সব খবর মিলবে এক ক্লিকেই বিরিয়ানি দিবে অ্যাপে
- ডায়াবেটিস নিয়েও সুস্থভাবে রোজা: সেহরি ও ইফতারের পূর্ণাঙ্গ গাইড
- আজ কিছু মোবাইল সংযোগে সাময়িক নেটওয়ার্ক বিঘ্ন
- দিল্লিতে বড় হামলার ছক: তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশিসহ গ্রেপ্তার ৮
- আজকের টাকার রেট কত? দেখে নিন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার
- লেবুর বাজারে স্বস্তির হাওয়া: হালিপ্রতি দাম কমল প্রায় অর্ধেক
- সৌদি সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা: রমজানে ওমরাহ পালনকারীদের জন্য একগুচ্ছ বার্তা
- হাসনাত-পাটওয়ারীদের পথেই জামায়াত আমির: ইনকিলাব স্ট্যাটাসে নেটদুনিয়ায় তোলপাড়
- টিভির পর্দায় আজকের খেলা: ভারত-বাংলাদেশ ফাইনাল থেকে নর্দান লন্ডন ডার্বি
- হু হু করে কমল সোনার দাম
- আবারও বাড়ল স্বর্ণ-রুপার দাম: নতুন দরে নাকাল সাধারণ ক্রেতারা
- চাকরির টাকায় সংসার না চললে ছেড়ে দিন, দুর্নীতির কোনো ক্ষমা নেই: আইনমন্ত্রী
- প্রাথমিকে রোজার ছুটি নিয়ে নতুন তথ্য জানাল অধিদপ্তর
- অগ্নিমূল্য স্বর্ণের বাজার, ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম বাড়লো ২২১৬ টাকা
- ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশের অংশবিশেষ
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক হলেন এহসানুল হক মিলন
- আজকের বাজারে স্বর্ণের দর কত? জেনে নিন বাজুসের নতুন মূল্যতালিকা
- মঙ্গলবার টানা ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না যেসব এলাকায়
- বাজুসের নতুন সিদ্ধান্ত: আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে স্বর্ণের হ্রাসকৃত মূল্য
- নতুন মন্ত্রিসভায় শপথের আমন্ত্রণ পেলেন যাঁরা
- আকাশছোঁয়া স্বর্ণের বাজারে কিছুটা স্বস্তি: আজ থেকেই দাম কমছে
- তিন স্তরের যাচাই শেষে ফ্যামিলি কার্ড: জেনে নিন আবেদনের সব নিয়ম
- স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রী: কুমিল্লা বরুড়াবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে চান জাকারিয়া তাহের
- তালসরায় গাউসিয়া কমিটির মানবিক উদ্যোগ: দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ