বিশেষ প্রতিবেদন
ভারতের পণ্যে উচ্চ শুল্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য সুবর্ণ সুযোগ নাকি সীমিত সম্ভাবনা?
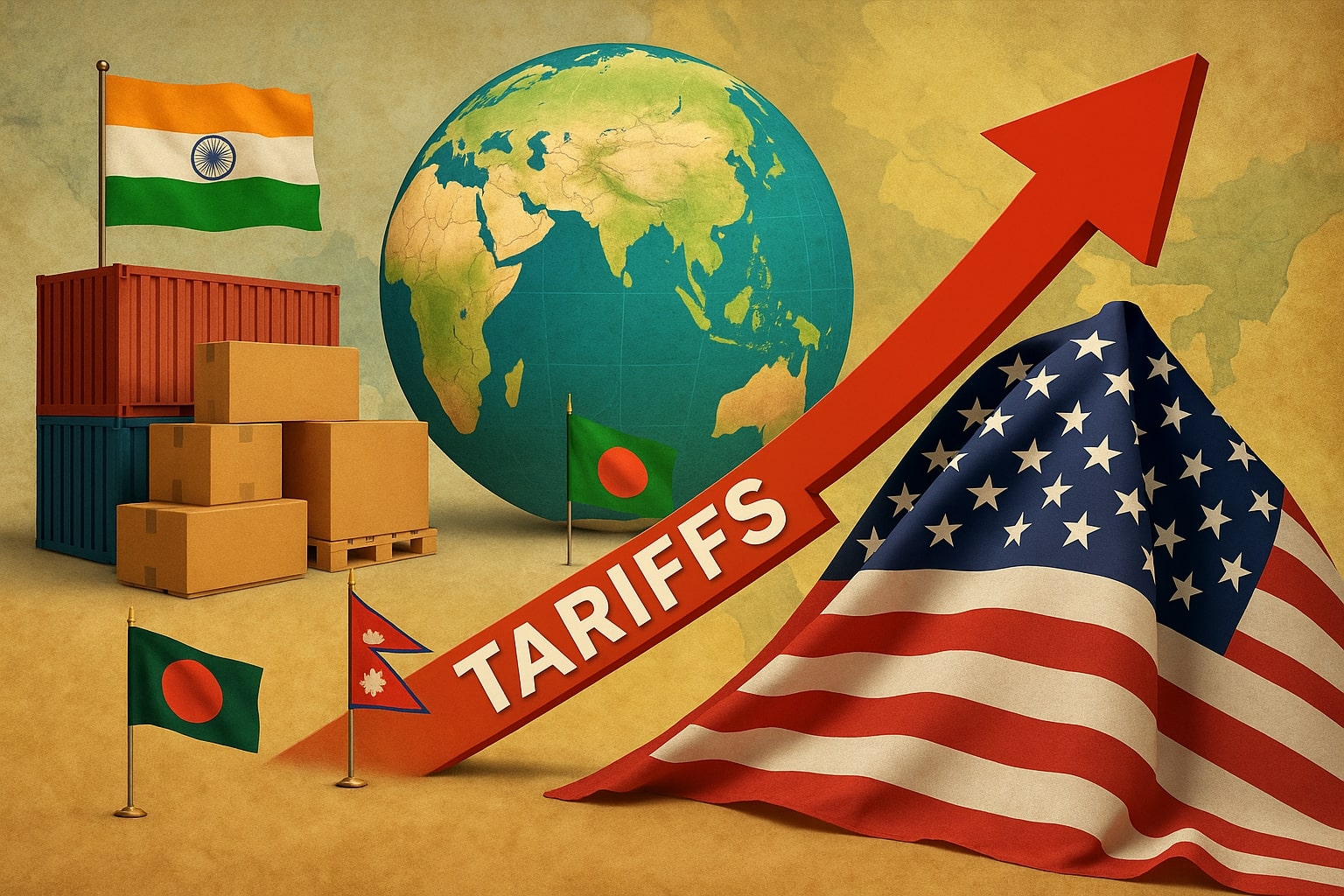
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পাল্টা শুল্ক নীতির কারণে ভারতীয় পণ্যে উচ্চ কর আরোপ হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার রপ্তানি প্রতিযোগিতার মানচিত্র বদলে যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, যেটি ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ তিন পোশাক রপ্তানিকারকের মধ্যে রয়েছে, এই পরিবর্তনের ফলে উল্লেখযোগ্য সুযোগ পেতে পারে। তবে অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করছেন, এই সুযোগ স্থায়ী নাও হতে পারে যদি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা দ্রুত গড়ে তোলা না হয়।
দুই সপ্তাহ আগেও যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক নীতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বাজার-অংশ দখলের পরিকল্পনা করছিল ভারতের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ধারণা ছিল, এই দেশগুলোর পণ্যে বেশি শুল্ক আরোপ হবে, অথচ ভারতীয় পণ্যে তুলনামূলক কম শুল্ক বসবে। কিন্তু ৩১ জুলাইয়ের ঘোষণায় চিত্র পাল্টে যায়। ওইদিন যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশের পণ্যে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করলেও ভারতীয় পণ্যে শুল্ক ধরা হয় ২৫ শতাংশ। এর মাত্র এক সপ্তাহ পর, রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানির ‘শাস্তি’ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর ঘোষণা দেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় পণ্যে মোট শুল্ক দাঁড়াচ্ছে ৫০ শতাংশে।
যদিও এই অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে ২১ দিন পর, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য পাল্টা শুল্ক ইতোমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে। ভারতীয় রপ্তানিকারকের জন্য এটি বড় ধাক্কা, আর বাংলাদেশের জন্য এটি সম্ভাবনার জানালা খুলে দিয়েছে।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য লাভের খাতসমূহ
শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা কিছু খাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবেন। রপ্তানি সম্ভাবনা বেশি এমন খাতগুলো হলো:
তৈরি পোশাক (RMG) – যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের গড় শুল্ক ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে, যেখানে বাংলাদেশের গড় শুল্ক হবে ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ। এতে নিট ও ওভেন পোশাকে অর্ডার সরতে পারে।
হোম টেক্সটাইল – ভারত গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ২৯৩ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি করেছে, বাংলাদেশ মাত্র ১৫ কোটি ডলার। উচ্চমূল্যের পণ্যে অর্ডার সরার সম্ভাবনা বেশি।
কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য – উচ্চ শুল্কের কারণে ভারতীয় কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যে দাম বাড়বে, যা বাংলাদেশের জন্য সুযোগ তৈরি করবে।
চামড়াজাত পণ্য – ভারতীয় পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি এই খাতে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াবে।
হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি – মূল্য প্রতিযোগিতায় ভারত পিছিয়ে পড়বে, ফলে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা বাড়তে পারে।
আসবাব – ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১১৫ কোটি ডলারের আসবাব রপ্তানি করেছে, বাংলাদেশ মাত্র ১ কোটি ৯৭ লাখ ডলার। হাতিলসহ কয়েকটি ব্র্যান্ড সক্ষমতা বাড়ালে বাজার দখলের সুযোগ রয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের সতর্কতা
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, ট্রাম্পের এই শুল্কনীতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির পরিপন্থী। রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ইরান থেকে জ্বালানি তেল কিনলে অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি বাংলাদেশের জন্যও উদ্বেগজনক, কারণ বাংলাদেশ রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে। এছাড়া অন্য দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে রপ্তানি করলে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসতে পারে।
তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে অস্থিতিশীল করেছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল শুল্কনীতির কারণে বিদেশি ক্রেতারা তড়িঘড়ি ব্যবসা স্থানান্তর করবে এমনটি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তাই বাজার পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
সম্ভাব্য কৌশল
সম্ভাব্য বাজার কৌশলগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। সর্বপ্রথম, দ্রুত সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিশেষ করে পোশাক, হোম টেক্সটাইল এবং আসবাবপত্র খাতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানের গুণমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। এর মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন, দক্ষ জনবল প্রশিক্ষণ এবং গুণগত মান যাচাইয়ের আন্তর্জাতিক সনদপ্রাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এছাড়া, সরকারি নীতি সহায়তা রপ্তানি প্রবৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি। কাঁচামাল আমদানিতে বন্ড সুবিধা নিশ্চিত করা, রপ্তানি প্রণোদনার হার বৃদ্ধি, এবং বন্দর ও লজিস্টিক অবকাঠামো উন্নয়ন এই খাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে কাস্টমস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।
বাজার গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও বজায় রাখা অপরিহার্য। পাশাপাশি বাজার প্রবণতা ও চাহিদার পরিবর্তন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং শুল্ক নীতির যেকোনো পরিবর্তন দ্রুত শনাক্ত করে তার ভিত্তিতে রপ্তানি কৌশল হালনাগাদ করতে হবে।
বৈচিত্র্যকরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধুমাত্র তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভর না করে চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি, এবং হোম ডেকর পণ্যের মতো অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। এর ফলে একদিকে বাজারের ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে।
সবশেষে, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের সাথে স্থায়ী সরবরাহ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। এতে শুধু অর্ডারের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না, বরং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। স্থায়ী ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরির জন্য নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি, মানসম্মত পণ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নীতি বজায় রাখা হবে মূল চাবিকাঠি।
আজকের টাকার রেট কত? দেখে নিন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের কোটি মানুষ আছেন প্রবাসে। বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, দেশের মুদ্রা বাজারে ডলার কেনার দাম ধরা হচ্ছে ১২২.৩০ টাকা। বিক্রির দাম ১২২.৩০ টাকা। গড় বিনিময় হার ১২২.৩০ টাকা।
ইউরো কেনার ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৪ টাকা ৯৬ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে দাম ধরা হয়েছে ১৪৫ টাকা ০১ পয়সা। মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে। (১৯ ফেব্রুয়ারি সমন্বয়কৃত দাম অনুসারে)*
আজকের বাজার দর অনুযায়ী, ইউএস ডলার কেনা হচ্ছে ১২২.৩০ টাকায় এবং বিক্রি হচ্ছে ১২২.৩০ টাকায়।
পাউন্ড কেনার রেট ১৬৫.৯২ টাকা এবং বিক্রির রেট ১৬৫.৯৮ টাকা।
ইউরো কেনা হচ্ছে ১৪৪.৯৬ টাকায় এবং বিক্রি হচ্ছে ১৪৫.০১ টাকায়।
জাপানি ইয়েন কেনা ও বিক্রি উভয়ই হচ্ছে ০.৮০ টাকায়।
অস্ট্রেলিয়ান ডলার কেনা হচ্ছে ৮৬.৬৩ টাকায় এবং বিক্রি হচ্ছে ৮৬.৬৮ টাকায়।
সিঙ্গাপুর ডলার কেনা হচ্ছে ৯৬.৮৯ টাকায় এবং বিক্রি হচ্ছে ৯৬.৮৮ টাকায়।
কানাডিয়ান ডলার কেনা হচ্ছে ৮৯.৬৮ টাকায় এবং বিক্রি হচ্ছে ৮৯.৬৯ টাকায়।
ইন্ডিয়ান রুপি কেনা ও বিক্রি উভয়ই হচ্ছে ১.৩৫ টাকায় এবং সৌদি রিয়েল কেনা হচ্ছে ৩২.৬১ টাকায় ও বিক্রি হচ্ছে ৩২.৫০ টাকায়।
/আশিক
আজকের বাজারে স্বর্ণের দর কত? জেনে নিন বাজুসের নতুন মূল্যতালিকা
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) সর্বশেষ গত বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কমিয়েছে। ওইদিন ভরিতে ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে নতুন দামে ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫৫৮ টাকা। নতুন এই দাম ওই দিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। আজ শনিবারও (২১ ফেব্রুয়ারি) দেশের বাজারে একই দামে স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম কমায় স্বর্ণের দামে এই সমন্বয় করা হয়েছে। নতুন নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী, এখন থেকে ২২ ক্যারেট প্রতি ভরি স্বর্ণ ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫৫৮ টাকা, ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৫৩ টাকা, ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ৭৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৭১ হাজার ১১১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, স্বর্ণের এই বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যোগ করতে হবে। তবে অলঙ্কারের ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির হারে ভিন্নতা হতে পারে। এদিকে, স্বর্ণের দাম কমলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বাজারে ২২ ক্যারেটের রুপার ভরি ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা, ২১ ক্যারেট ৬ হাজার ৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট ৫ হাজার ১৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপা ৩ হাজার ৯০৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
/আশিক
আবারও স্বর্ণের বাজারে বড় উত্থান
আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের মূল্য আবারও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে স্বর্ণে ঝুঁকছেন বলে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা Reuters জানিয়েছে।
বাংলাদেশ সময় শুক্রবার বিকাল ৩টা ৪১ মিনিটে স্পট মার্কেটে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ০ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৫ হাজার ৩২ দশমিক ৪৯ ডলারে পৌঁছায়। একই সময়ে এপ্রিল ডেলিভারির জন্য মার্কিন গোল্ড ফিউচারস ১ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ হাজার ৫২ দশমিক ৭০ ডলারে লেনদেন হয়েছে। ফিউচারস বাজারে তুলনামূলক বেশি উত্থান বিনিয়োগকারীদের আগাম প্রত্যাশার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের অস্থিরতা বিনিয়োগকারীদের ‘সেফ হ্যাভেন’ সম্পদে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে। ঐতিহাসিকভাবে সংকটকালীন সময়ে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
বিনিয়োগ ব্যাংক Goldman Sachs জানিয়েছে, তাদের মৌলিক পূর্বাভাস অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর স্বর্ণ ক্রয় কার্যক্রম পুনরায় জোরদার হলে এবং যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য সুদহার হ্রাসের পরিবেশে বিনিয়োগকারীরা বিকল্প সম্পদে ঝুঁকলে চলতি বছরে স্বর্ণের দাম ধীরে ধীরে আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে সুদহার কমার প্রত্যাশা ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে স্বর্ণের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
বাজার পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সাম্প্রতিক অস্থিরতার পাশাপাশি বৈশ্বিক মুদ্রানীতি, ডলার সূচকের গতিপ্রকৃতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা স্বর্ণবাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে স্বর্ণের দামে আরও ঊর্ধ্বগতি দেখা যেতে পারে।
-রাফসান
হু হু করে কমল সোনার দাম
দেশের স্বর্ণবাজারে আবারও মূল্য সমন্বয়ের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি ভরিতে ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমিয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫৫৮ টাকা। বুধবার সকালে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘোষিত এই মূল্য আজ শুক্রবার থেকে কার্যকর থাকবে।
বাজুসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণ বা পিওর গোল্ডের দর হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দামের ওঠানামা, ডলার বিনিময় হার এবং দেশীয় সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই এই সমন্বয় করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
নতুন তালিকা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৫৩ টাকা। ১৮ ক্যারেটের ক্ষেত্রে প্রতি ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ৭৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ১১১ টাকা। এখানে এক ভরি সমান ১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম হিসেবে গণনা করা হয়েছে।
তবে নির্ধারিত দামের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত হবে। ফলে গহনার চূড়ান্ত বিক্রয়মূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। ডিজাইন, কারুকাজ ও মানভেদে মজুরির হার ভিন্ন হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ মূল্য সমন্বয়ে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪ টাকা, যা সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়। সে সময়ও ভরিতে ২ হাজার ২১৬ টাকা কমানো হয়েছিল। চলতি বছর এখন পর্যন্ত মোট ৩০ বার স্বর্ণের মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ দফা দাম বৃদ্ধি এবং ১২ দফা হ্রাস করা হয়েছে। গত ২০২৫ সালে রেকর্ডসংখ্যক ৯৩ বার মূল্য পরিবর্তন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৬৪ বার দাম বেড়েছিল এবং ২৯ বার কমেছিল।
স্বর্ণের বাজারে ওঠানামা চললেও রুপার দামে আপাতত কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। বর্তমানে ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি বিক্রি হচ্ছে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকায়। ২১ ক্যারেট রুপার দাম ৬ হাজার ৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ৫ হাজার ১৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপা ৩ হাজার ৯০৭ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। চলতি বছরে রুপার দাম ১৭ বার সমন্বয় করা হয়েছে, যার মধ্যে ১০ বার বেড়েছে এবং ৭ বার কমেছে। গত বছর মোট ১৩ বার সমন্বয় করা হয়েছিল, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাম বেড়েছিল।
-রাফসান
বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার: ২০ ফেব্রুয়ারি
বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। আমদানি-রপ্তানি, প্রবাসী আয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের বিনিময় হার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার হালনাগাদ বিনিময় হার প্রকাশিত হয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন ডলার প্রতি ১২২ টাকা ৪২ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে। ইউরোপীয় অঞ্চলের একক মুদ্রা ইউরোর দর দাঁড়িয়েছে ১৪৩ টাকা ৯৬ পয়সা। যুক্তরাজ্যের মুদ্রা ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ১৬৪ টাকা ৬২ পয়সা।
অস্ট্রেলিয়ান ডলার প্রতি ৮৬ টাকা এবং কানাডিয়ান ডলার ৮৯ টাকা ৩৯ পয়সায় বিনিময় হচ্ছে। এশীয় মুদ্রাগুলোর মধ্যে জাপানি ইয়েনের মূল্য ৭৯ পয়সা, চীনা ইউয়ান রেনমিনবি ১৭ টাকা ৭৪ পয়সা এবং সিঙ্গাপুর ডলার ৯৬ টাকা ৪৪ পয়সায় নির্ধারিত হয়েছে।
ভারতীয় রুপি ১ টাকা ৩৫ পয়সা এবং শ্রীলঙ্কান রুপি ২ টাকা ৫২ পয়সায় বিনিময় হচ্ছে। মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের দর ৩১ টাকা ২৯ পয়সা। মধ্যপ্রাচ্যের মুদ্রাগুলোর মধ্যে সৌদি রিয়াল ৩২ টাকা ৬৩ পয়সা এবং কাতারি রিয়াল ৩৩ টাকা ৫৩ পয়সায় লেনদেন হচ্ছে। ওমানি রিয়াল ৩১৮ টাকা ৩৯ পয়সা এবং কুয়েতি দিনার সর্বোচ্চ ৩৯৯ টাকা ৮ পয়সায় বিনিময় হচ্ছে।
ইউরোপীয় অঞ্চলের সুইডিশ ক্রোনা প্রতি ১৩ টাকা ৪৭ পয়সায় নির্ধারিত হয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সুদের হার, জ্বালানি বাজার ও রিজার্ভের অবস্থার ওপর নির্ভর করে মুদ্রার দর প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। ফলে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী, ব্যাংকিং খাত ও প্রবাসীদের জন্য প্রতিদিনের আপডেট জানা গুরুত্বপূর্ণ।
উল্লেখ্য, উল্লিখিত হার আন্তর্জাতিক অনলাইন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাজার পরিস্থিতি ও ব্যাংকভেদে বাস্তব লেনদেনে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে এবং যে কোনো সময় বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।
-রাফসান
স্বর্ণের বাজারে টানা উত্থান: বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় খবর
আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বৃহস্পতিবারও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। আগের সেশনে ২ শতাংশের বেশি বৃদ্ধির পর নতুন করে দাম বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদে ঝুঁকছেন। একই সঙ্গে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতির দিকনির্দেশনা মূল্যায়ন করছেন। খবর রয়টার্সের।
স্পট মার্কেটে স্বর্ণের দাম ০ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৫,০১২ দশমিক ৮৩ ডলারে পৌঁছেছে। এপ্রিল ডেলিভারির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ ফিউচারস ০ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,০৩১ দশমিক ২০ ডলার।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়লে স্বর্ণের চাহিদা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। কারণ বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে সরে গিয়ে তুলনামূলক নিরাপদ বিনিয়োগে অর্থ স্থানান্তর করেন।
এদিকে ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ অবস্থানও স্বর্ণবাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। সুদের হার কমার সম্ভাবনা থাকলে স্বর্ণের আকর্ষণ বাড়ে, আর কড়াকড়ি নীতি থাকলে দাম চাপে পড়ে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ও মার্কিন মুদ্রানীতির ইঙ্গিতই এখন স্বর্ণবাজারের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।
/আশিক
রোজার প্রথম দিনেই মুরগি ও সবজির দামে লাগামহীন রাজধানীর বাজার
রোজার প্রথম দিনেই রাজধানীর বাজারে মুরগির মাংসের দাম বেড়েছে। জাতভেদে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কেজিতে ২০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) কারওয়ান বাজার ঘুরে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা গেছে। সেই সঙ্গে গরুর মাংস ৭৮০ থেকে ৮০০ টাকা ও খাশির মাংস ১২০০ থেকে ১২৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হতে দেখা গেছে।
বাজারে দেখা যায়, ব্রয়লার মুরগি ২০০ টাকা, দেশি মুরগি ৭৫০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ থেকে ৩৪০ টাকা ও লাল লেয়ার মুরগি ৩৩০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।
কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেটের সততা মুরগির আড়তের কর্মচারী সুমন সাংবাদিকদের বলেন, সব ধরনের মুরগির দাম বেড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন দাম ২০০ টাকা। দেশি মুরগি ৫৮০ থেকে ৬৮০ টাকা থাকলেও এখন বিক্রি হচ্ছে ৭ ১৫০ টাকায়। আর ২৮০ টাকার লাল মুরগি এখন বিক্রি হচ্ছে ৩৩০ টাকা কেজিতে।
এদিকে বাজারে লেবু ৬০ থেকে ১২০ টাকা হালি, শশা ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি ও বেগুন ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সেই সঙ্গে আলু ২০ টাকা ও পেঁয়াজ ৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হতে দেখা গেছে।
/আশিক
শুল্ক ছাড়ের সুফল নেই: জাহাজ ডুবি ও সিন্ডিকেটে উত্তপ্ত খেজুরের বাজার
সরকার আমদানিতে বড় ধরনের শুল্ক ছাড় দিলেও তার সুফল পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। পবিত্র রমজানের শুরুতে খেজুরের দাম নাগালের মধ্যে থাকার আশা থাকলেও বর্তমানে তা কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। এমনকি গত বছরের তুলনায় এবার খেজুরের দাম আরও বাড়তি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মবিরতি থাকায় জাহাজ বার্থিং পেতে বিলম্ব হয়েছে, যা সাপ্লাই চেইনকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এর পাশাপাশি থাইল্যান্ড উপকূলে ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ইরাকি খেজুরসহ একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ায় বাজারে বড় ধরনের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন আগেও যে ইরাকি খেজুর ১৫০ টাকা কেজি দরে পাইকারি বিক্রি হতো, বর্তমানে সেই খেজুর ১৮০-১৮৫ টাকায় পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। ১০ কেজির কার্টন পাইকারি ২ হাজার ২০০ টাকা থেকে বেড়ে ২ হাজার ৪০০ টাকা হয়েছে।
দেশের মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করে সরকার খেজুরের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে, যা ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তবে শুল্ক কমানোর কারণে দাম কমার কথা থাকলেও অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফালোভী কারসাজির কারণে এর প্রতিফলন বাজারে নেই। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খেজুর আমদানিকারক ও বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, "থাইল্যান্ড উপকূলে প্রায় ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ইরাকি খেজুরবাহী একটি জাহাজ ডুবে গেছে এবং চট্টগ্রাম বন্দরে চার দিনের কর্মবিরতির ফলে সৃষ্ট জাহাজ জটে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে জনপ্রিয় ইরাকি খেজুরের সরবরাহ কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, খুচরা বিক্রেতাদের অধিক মুনাফা করার প্রবণতাই এই অকাল দাম বাড়ার পেছনে বড় কারণ। তবে আমদানিকৃত খেজুরের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে বেশি হলে রমজান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাজার দ্রুতই স্থিতিশীল হয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
সামগ্রিকভাবে বাজারে খেজুরের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সৌদি আরব, তিউনিসিয়া বা আরব আমিরাতের মতো বড় উৎসগুলো থেকে আসা প্রিমিয়াম খেজুরের দাম সেভাবে বাড়েনি। তবে নিম্নবিত্তের জন্য জনপ্রিয় জাতগুলোর দাম এখন আকাশচুম্বী।
বাজারে খেজুরের বর্তমান মূল্য তালিকা
বস্তা খেজুর (বাংলা খেজুর): ২২০ থেকে ২৪০ টাকা কেজি।
জাহিদি খেজুর: ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি।
দাবাস খেজুর: ৫৫০ থেকে ৬০০ টাকা কেজি।
বরই খেজুর: ৪৮০ থেকে ৬৫০ টাকা কেজি।
কালমি খেজুর: ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকা কেজি।
সুক্কারি খেজুর: ৮০০ থেকে ৮৫০ টাকা কেজি।
মাবরুম খেজুর: ৮৫০ থেকে ১,২০০ টাকা কেজি।
মরিয়ম খেজুর: ১,১০০ থেকে ১,৪০০ টাকা কেজি।
মেডজুল খেজুর: ১,২০০ থেকে ১,৮০০ টাকা কেজি।
/আশিক
নবম পে-স্কেল কি পিছিয়ে যাচ্ছে? যা বললেন নতুন অর্থমন্ত্রী
নবম জাতীয় বেতন কমিশন বা পে-স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার মাঝে নতুন বার্তা দিয়েছেন নবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, বর্তমান দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ট্যাক্স-জিডিপি রেশিও বিবেচনা করে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, সুপারিশগুলো না দেখে এখনই কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়; বরং এটি কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য, তা যাচাই করাই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।
এর আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে যথাসময়ে নতুন পে-স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হবে। গত ২১ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়া বেতন কমিশনের প্রতিবেদনে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ১০০ থেকে ১৪৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে সর্বনিম্ন বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতন ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কমিশন চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে আংশিক এবং আগামী ১ জুলাই (২০২৬-২৭ অর্থবছর) থেকে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করার কথা জানিয়েছে।
বর্তমানে দেশের প্রায় ১৪ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং ৯ লাখ পেনশনভোগীর বেতনের জন্য সরকারের ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। কমিশনের নতুন সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের অতিরিক্ত ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তবে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর বক্তব্যে এটি স্পষ্ট যে, দেশের বর্তমান রাজস্ব ঘাটতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাতের কারণে এই বিশাল আর্থিক ব্যয়ভার বহন করার আগে সরকার অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে চায়।
/আশিক
পাঠকের মতামত:
- কুমিল্লা সদর দক্ষিণে গভীর রাতে শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান
- ইতিহাসে প্রথম শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে ভাষা শহীদদের জন্য দোয়া প্রধানমন্ত্রীর
- রোজায় ক্লান্তিবোধ কমবে নিমিষেই: শক্তি ধরে রাখার ৪টি সেরা কৌশল
- রোজায় গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান মিলবে ঘরোয়া এই নিয়মেই
- দুর্নীতি ও ধর্মান্ধতা একুশের চেতনার শত্রু: টিআইবি প্রধান
- সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে: জামায়াত আমির
- গণভোটের হ্যাঁঅটোমেটিক কার্যকর হবে, এটাই জুলাই সনদ: এ্যানি
- আজকের টাকার রেট কত? দেখে নিন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার
- যশোরে তালা ভেঙে আওয়ামী লীগ অফিসে ছবি টাঙালো ছাত্রলীগ
- আজ শনিবার; রাজধানীর যেসব এলাকার মার্কেট ও দোকানপাট বন্ধ
- ১৭ বছর পর ক্ষমতায় এসে এমন আচরণ কাম্য নয়: রুমিন ফারহানা
- জেনে নিন রাজধানীতে আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- আজ রাজধানীতে কোথায় কী কর্মসূচি: জেনে নিন সকালে বের হওয়ার আগে
- আজকের বাজারে স্বর্ণের দর কত? জেনে নিন বাজুসের নতুন মূল্যতালিকা
- একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
- রমজানের তৃতীয় দিনের ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
- প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন, কে কোন দায়িত্বে?
- আবারও স্বর্ণের বাজারে বড় উত্থান
- রমজানে অর্ধশত পরিবারের পাশে সিলেট-চট্টগ্রাম ফ্রেন্ডশিপ ফাউন্ডেশন
- মুরাদনগরে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধে নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা
- শেয়ারবাজারের সাপ্তাহিক পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- যমুনা ছাড়ছেন কবে ড. ইউনূস, কোথায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী
- ঢাকায় ১০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান ইশরাকের
- শেয়ারবাজারে আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন: অর্থ মন্ত্রী আমীর খসরু
- ২১ ফেব্রুয়ারিতে ডিএমপির সড়ক নির্দেশনা, কোন পথ এড়াবেন
- হামলা হলে মার্কিন ঘাঁটি হবে লক্ষ্যবস্তু: ইরান
- "আই হ্যাভ এ প্ল্যান" বাস্তবায়ন শুরু
- হু হু করে কমল সোনার দাম
- বৈদেশিক মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার: ২০ ফেব্রুয়ারি
- বের হওয়ার আগে জেনে নিন আজ যেসব মার্কেট বন্ধ
- এইচএসসি ২০২৬: ফরম পূরণের পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ও নীতিমালা প্রকাশ
- শুক্রবারের পূর্ণ নামাজ সূচি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
- রাজধানীতে আজ আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- রাজধানীতে আজ আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- বাংলাদেশের ম্যাচসহ আজ টিভিতে যেসব খেলা দেখবেন
- এতিমদের মধ্য থেকেই কেউ একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে: শফিকুর রহমান
- ঈদের আগেই ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে কমিটি: দায়িত্বে আছেন যারা
- সড়কে সমঝোতার ভিত্তিতে টাকা তোলা চাঁদা নয়: সড়ক পরিবহন মন্ত্রী
- স্বর্ণের বাজারে টানা উত্থান: বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় খবর
- ইফতারের পর ক্লান্ত লাগে? সতেজ থাকার সহজ উপায়গুলো জেনে নিন
- মহাকাশ বিজয়ে ইরান: সফলভাবে উৎক্ষেপিত হলো জাম-এ-জাম ১
- ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত মন্ত্রিসভা, জনস্বার্থ উপেক্ষিত: নাহিদ ইসলাম
- পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আসছে
- ১৯ ফেব্রুয়ারি শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- রোজার প্রথম দিনেই মুরগি ও সবজির দামে লাগামহীন রাজধানীর বাজার
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরপতনের শেয়ার
- ইফতারে যেসব ভুলের কারণে গ্যাস্ট্রিক ও ওজন বাড়ে
- প্রথম রোজার ইফতারে চমক! ঘরেই তৈরি করুন মুচমুচে ও সুস্বাদু চিকেন পাকোড়া
- দুপুরের নির্জনতা ভেঙে হঠাৎ কেঁপে উঠল সিলেট: বড় কোনো দুর্যোগের পূর্বাভাস?
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরবৃদ্ধিকারী শেয়ার
- বাজুসের নতুন দর! ২ লাখ ১৩ হাজারে মিলবে ১ ভরি সোনা
- হু হু করে কমল সোনার দাম
- রমজানে স্কুল খোলা নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়: বদলে গেল ছুটির পুরো ক্যালেন্ডার
- চাকরির টাকায় সংসার না চললে ছেড়ে দিন, দুর্নীতির কোনো ক্ষমা নেই: আইনমন্ত্রী
- প্রাথমিকে রোজার ছুটি নিয়ে নতুন তথ্য জানাল অধিদপ্তর
- অগ্নিমূল্য স্বর্ণের বাজার, ভরিপ্রতি স্বর্ণের দাম বাড়লো ২২১৬ টাকা
- বিশ্ববাজারের প্রভাব পড়ল দেশের স্বর্ণবাজারে: আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম
- ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দেশের অংশবিশেষ
- কালিগঞ্জে শতবর্ষী মাদ্রাসার জমি জোরপূর্বক বিক্রয়ের অভিযোগ, দখলের পায়তারা
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক হলেন এহসানুল হক মিলন
- মঙ্গলবার টানা ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না যেসব এলাকায়
- আজ বিকেলেই শুরু হচ্ছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ: বাংলাদেশ থেকে কি দেখা যাবে?
- বাজুসের নতুন সিদ্ধান্ত: আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে স্বর্ণের হ্রাসকৃত মূল্য
- আকাশছোঁয়া স্বর্ণের বাজারে কিছুটা স্বস্তি: আজ থেকেই দাম কমছে
- ১৫ ফেব্রুয়ারি শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ














