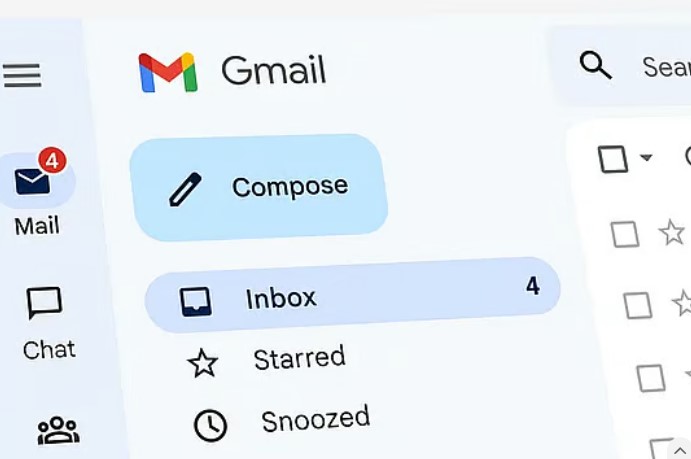ইতিহাস ও দর্শন
ধ্বংসস্তূপ থেকে মহাশক্তি: চীনের পুনর্জন্মের বিস্ময়গাঁথা

ইশরাত ওয়ারা
ডেস্ক রিপোর্টার

৭০ বছর আগেও চীনের এই সমুদ্রপথে প্রতিদিন ভেসে থাকত অসংখ্য মানুষের নিথর দেহ। তারা মরিয়া হয়ে মূল ভূখণ্ড চীন থেকে হংকংয়ের পথে রওনা দিত, একটি ভালো জীবনের আশায়। সেই সময় চীনে মানুষের পেটে দুবেলা খাবার জুটত না, শিক্ষা ছিল একপ্রকার অপরাধ। স্কুলে যেতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হতো। বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল সাধারণ মানুষ। কমিউনিজমের কৃত্রিম পরীক্ষাগারে চীন তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই এক সময় এমন এক রূপান্তর ঘটে যে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।
নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন, চীন একটি ঘুমন্ত দৈত্য। যেদিন সে জেগে উঠবে, গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কথাটি আজ সত্য বলে মনে হয়। ভাবুন একবার, যে দেশের জিডিপি এক সময় তানজানিয়া কিংবা কেনিয়ার চেয়েও কম ছিল, সেই দেশের অর্থনীতি আজ ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আজকের সাংহাই, চংকিং বা শেনজেনের মতো শহরগুলো উন্নয়ন ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপকেও পেছনে ফেলছে। ধারণা করা হয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?
কীভাবে চীন এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে ধনী হয়ে উঠল? চীনের এই জাদুকরী রূপান্তরের পেছনের রহস্য কী? আমাদের দেশে এমন পরিবর্তন কেন ঘটল না? এমনকি জাপানের মতো কর্মঠ জাতিও কেন এই গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি? নিশ্চয়ই চীনের হাতে কোনো জাদুর কাঠি ছিল না। এর পেছনে ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবসম্মত ভিশন এবং জাতীয় স্বপ্ন।
১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর আক্রমণ করে। মাত্র একদিনে দুই লক্ষাধিক চীনা নারী জাপানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত হন, নিহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যাতে চীনের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধ শেষে যখন জাপান পরাজিত হয়, তখন চীনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দীর্ঘ যুদ্ধের ধাক্কায় চীনের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং মেইনল্যান্ড চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট শাসন। কিন্তু যেই আশায় মানুষ কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছিল, সেটিই পরে পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে।
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও জেদং-এর আদর্শ ও নীতিমালা দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অথচ এই চীনই এক সময় ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাচীন চীনের সম্পদ ও জ্ঞান এতই বিস্ময়কর ছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়ও সে সময় চীন ছিল ধনী। বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ আসত চীন থেকে।
চীনের রেশম ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সিল্ক রোডের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। বিশ্বের প্রথম কম্পাস, বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল এই চীনেই। সামরিক শক্তিতেও চীন ছিল বলিষ্ঠ, যার সাক্ষ্য আজও বহন করছে দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না। কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা ছিল অগ্রগামী। চীনের উর্বর মাটিতে কখনো খাদ্যের ঘাটতি পড়েনি। তারাই প্রথম আকুপাংচার ও হারবাল মেডিসিন আবিষ্কার করে, যা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।
তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এত সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্ভর এক দেশ কীভাবে একসময় চরম দারিদ্র্য ও হতাশার গভীরে তলিয়ে গেল? ইতিহাসের এই প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আমাদের আজ নতুন করে ভাবতে শেখায় যে একটি জাতি কেবল সম্পদে নয়, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায়ই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।
শুধু কি জাপানের আগ্রাসন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চীনকে ধ্বংস করেছিল? না, এর পেছনে ছিল আরও গভীর ইতিহাস, যার শিকড় অনেক পুরোনো এবং যেখানে পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তির কূটচালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
সময়টা ১৭৭৩ সাল। তখন চীনে চিং রাজবংশের শাসন চলছে। এদিকে ভারতে ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল, তেমনি তারা চীনের বাজারেও প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু চীনের সম্রাট ইংরেজদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে নানা রাজনৈতিক চাপের পর সীমিত পরিসরে তাদের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণে চা আমদানি শুরু করে, কিন্তু বিনিময়ে তারা চীনকে দিতে শুরু করে আফিম, এক ভয়াবহ নেশাদ্রব্য।
চীনের সভ্যতা ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল এই আফিম দিয়ে। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাল পরিসরে আফিম চাষ করত এবং সেই আফিম চীনে রপ্তানি করত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের তরুণ প্রজন্ম আফিমের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমী মানুষগুলো কাজ বন্ধ করে সারাদিন নেশায় ডুবে থাকত। উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।
চীনের শাসকরা এই অবস্থা দেখে দেশে আফিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ইংরেজরা তা উপেক্ষা করে গোপনে বিক্রি চালিয়ে যায়, কারণ এই ব্যবসায় তারা প্রচুর লাভ করছিল। এক পর্যায়ে চীনের প্রশাসন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের আফিমের গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৮৩৯ সালে শুরু হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ।
যুদ্ধটি টানা চার বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে। তারা হংকং দখল করে নেয়, চীনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বিশাল অংশের ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। এখান থেকেই শুরু হয় চীনের “শতবর্ষের অপমান” বা সেঞ্চুরি অব হিউমিলিয়েশন।
যখন পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তখন চীনের উচিত ছিল বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তার করা। কিন্তু আফিম যুদ্ধের পর চীনের শাসকরা ভয় ও সন্দেহে নিজেদের চারপাশে দেয়াল তুলে দেয়। তারা বিদেশি বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে এবং নিজেদের অর্থনীতি বন্ধ করে ফেলে। এর ফলে তারা দ্রুত আধুনিকায়নের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
পরবর্তী একশ বছর ধরে চীন ক্রমাগত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কখনো রাশিয়া, কখনো জাপান, আবার কখনো যুক্তরাষ্ট্র চীনের ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এইসব যুদ্ধ এবং বিদেশি আগ্রাসনের ফলে চীনের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
অবশেষে আসে ১৯৪৯ সাল। দীর্ঘ যুদ্ধ, আফিম বাণিজ্য, জাপানের দখল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর চীনের সামনে আবার একবার পুনরুত্থানের সুযোগ আসে। মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে, মনে হয় নতুন এক যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই আশার মুহূর্তেই ক্ষমতায় আসেন এমন একজন নেতা, যার সিদ্ধান্ত চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। তিনি ছিলেন চীনের রাষ্ট্রপতি মাও জেদং।
মাও জেদং চীনের অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নতির পথে নিতে কিছু নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে ছিল গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড এবং কালচারাল রেভলিউশন। বড় জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে তিনি ছোট চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই রাখেন। সরকার নির্ধারণ করত কখন চাষ হবে, কী চাষ হবে এবং কতটা উৎপাদন হবে। কৃষকদের কাজ ছিল শুধু শ্রম দেওয়া। উৎপাদিত ফসলের সবটাই দিতে হতো সরকারের কাছে এবং বিনিময়ে তারা পেত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।
এই নীতি খুব দ্রুত ব্যর্থ হয়। কৃষকদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, প্রযুক্তি ছিল পুরোনো এবং উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত কমতে থাকে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেও দুবেলা আহার জুটাতে পারত না। এরই মধ্যে মাও আরেকটি নীতি চালু করেন, যার নাম ছিল ফোর পেস্ট কন্ট্রোল। তিনি চীনের সব চড়ুই, ইঁদুর, মশা ও মাছি নির্মূল করার আদেশ দেন। মাও তখন চীনে প্রায় ঈশ্বরসম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই জনগণ তার নির্দেশ অন্ধভাবে পালন করে। কয়েক বছরের মধ্যে চীনে লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি মারা পড়ে, ফলে পঙ্গপালের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ফসলে হানা দেয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যেখানে প্রায় চার কোটি মানুষ প্রাণ হারায়।
মাও শিল্পায়নের দিকেও জোর দেন। গোটা দেশে স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা হয়, এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঘরে স্টিল তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাবে সেই স্টিলের গুণমান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, ফলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।
১৯৬০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক চার শতাংশে। দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং খাদ্যসংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধারণ মানুষ মাওয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক শীর্ষ নেতা তার নীতির সমালোচনা করেন।
চীনের এই দীর্ঘ পতনের ইতিহাস দেখায়, একটি দেশ কেবল দেশপ্রেম বা শ্রম দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সঠিক নেতৃত্ব, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তিই পারে একটি জাতিকে পুনর্জন্ম দিতে।
হীরক রাজা একবার বলেছিলেন, “পড়াশোনা করে যে, অনাহারে মরে সে।” মাও জেদংও প্রায় একই বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষরা বা বুদ্ধিজীবীরা তার শাসনের জন্য হুমকি। তাই তিনি তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন।
১৯৬৬ সালে চীনে শুরু হয় কালচারাল রেভলিউশন। মাও ঘোষণা দেন, চীনে নতুন এক বিপ্লব ঘটবে যেখানে পুরনো প্রথা, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির স্থান থাকবে না। তখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শহরের শিক্ষিত মানুষদের জোর করে গ্রামে পাঠানো হয় যাতে তারা মাঠে কাজ করে কৃষকদের কাছ থেকে শেখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করা হয়। কেউ যদি পড়াশোনা করতে চাইত, তবে তাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো।
এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল একটাই। যে কেউ মাও-এর চিন্তার বিপরীতে কথা বলবে, তাকে রাষ্ট্রবিরোধী ঘোষণা করা হবে। সেই সময় শিক্ষিত মানুষদের মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। সমাজে ভয়, অরাজকতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকে এসে চীনের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য কার্যত থেমে যায়। দেশের অর্থনীতি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তখন চীনের রাস্তায় মোটরগাড়ি প্রায় দেখা যেত না। যার কাছে একটি সাইকেল ছিল, তাকেই ধনী মনে করা হতো।
মানুষ তখন চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। অন্যদিকে, পাশেই ছিল হংকং, যা তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। হংকং-এ জীবনযাত্রা ছিল বহু গুণ উন্নত। সেখানে কাজের সুযোগ বেশি ছিল, বেতন অনেক বেশি ছিল এবং মানুষ অন্তত দুবেলা খেতে পারত। তাই হংকং চীনের মানুষের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য হয়ে ওঠে।
এই সময় সেনজেন প্রদেশের প্রায় সাত লাখ মানুষ সমুদ্র পেরিয়ে হংকং যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ পৌঁছাতে পারে। কেউ কেউ ফিরে আসে, আর বাকিদের অনেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ে প্রাণ হারায়। সেই উপকূল আজও পরিচিত “কোভ অফ কর্পস” নামে, যার অর্থ মৃতদেহের উপসাগর।
এই সময় কেউ ভাবতেও পারত না যে চীন কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তখন চীনের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে কাজ করছিলেন এক খাটো মানুষ, যার উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। তার নাম দেং জিয়াওপিং। কেউ তখন জানত না যে এই মানুষটিই একদিন চীনকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত করবেন।
দেং জিয়াওপিং একসময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কিন্তু মাও জেদং-এর সমালোচনা করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং রাজধানী বেইজিং থেকে দূরে এক গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি তিন বছর কৃষিকাজ করেন।
১৯৭৬ সালে মাও জেদং-এর মৃত্যুর পর দেং জিয়াওপিং-এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তার সমর্থকেরা তাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনে। তখন চীনের মানুষের একটাই লক্ষ্য ছিল, কীভাবে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা যায়।
দেং জিয়াওপিং-এর আদর্শ ছিল মাও-এর চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাও চেয়েছিলেন জনগণ তাকে ঈশ্বরের মতো মানুক এবং তার প্রতিটি কথা যেন চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য হয়। তিনি বিপ্লব ও কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দেং ছিলেন বাস্তববাদী এবং প্রগতিশীল। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একটি দেশের আসল লক্ষ্য।
মাও-এর মৃত্যুর পর দেং-এর সামনে বড় বাধা ছিল সেই সব নেতারা, যারা এখনও মাও-এর পুরনো আদর্শে বিশ্বাস করতেন। একই সময়ে মাও-এর স্ত্রী জিয়াং ছিং ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন এবং গ্রেফতার হন।
দেং জিয়াওপিং কখনো চীনের রাষ্ট্রপতি বা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হননি, তবুও তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চীনের উন্নতির জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
১৯৭৭ সালে তিনি বেইজিংয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রক্ষণশীল নেতারা, যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার বিরোধিতা করছিলেন। তখন দেং জিয়াওপিং একটি ঐতিহাসিক কথা বলেন যা চীনের ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। তিনি বলেন, “বিড়াল সাদা না কালো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না সে ইঁদুর ধরতে পারে।” অর্থাৎ দেশের উন্নতির জন্য কোনো নীতি কার্যকর হলে সেটা কে তৈরি করেছে বা কোন মতবাদ থেকে এসেছে তা বিবেচ্য নয়। মূল কথা হলো, তা কাজ করছে কি না।
এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে বাস্তবতা-নির্ভর নীতি গ্রহণই হবে চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। তিনি মাও-এর সময় বন্ধ করে দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলো পুনরায় খুলে দেন। আবার শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা।
১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বড় পরিসরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ৩৮ বছর বয়সী প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ পাস করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাই ছিল চীনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন চীনের পুনর্জাগরণের ইতিহাস।
চীনের অর্থনীতিকে নতুন পথে নেওয়ার পরবর্তী ধাপে দেং জিয়াওপিং তিরিশ জনের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেন। দলটি ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের নানা দেশে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে তারা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উৎপাদনশীলতা ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইউরোপের ব্যাপক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়। দেশে তাদের দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে এবং সমাজকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে তারা দেখতে পায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কার্যকর নীতি, উচ্চ দক্ষতা ও আধুনিক অবকাঠামোর মাধ্যমে বহুগুণ এগিয়ে গেছে।
চীনা প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে ধারণা নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোও চীনকে সহায়তায় আগ্রহ দেখায়, কারণ বিশাল বাজার হিসাবে চীন তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। এ সময় দেং জিয়াওপিং নিজেও সিঙ্গাপুর ও জাপান সফর করেন। জাপানে তিনি ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার গতির ট্রেন, রোবোটিক্স ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের আধুনিকতা, এবং নাগরিক জীবনের উচ্চমান দেখে অভিভূত হন। সিঙ্গাপুর ও জাপানের রাস্তা, কারখানা, বসতবাড়ি এবং জীবনযাত্রা তিনি ভিডিও করে দেশে এনে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। জাপানে সাধারণ শ্রমিকের ঘরেও টেলিভিশন ও ফ্রিজ আছে, উন্নত কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, এইসব দৃশ্য দেখে চীনের মানুষ নতুন করে আশা পেতে শুরু করে। দেং বুঝতেন যে দীর্ঘদিনের ভুল নীতিতে মানুষ স্বপ্ন দেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তাই জাতির মনে আশাবাদ সঞ্চার করা ছিল তার প্রথম লক্ষ্য।
তবে ভেতরে ভেতরে অনেকে পরিবর্তন মানতে রাজি ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, ইউরোপ বা জাপানের মতো উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করলে বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির দুই শতাধিক সদস্যকে বেইজিংয়ে ডাকা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দেং জিয়াওপিং। সেখানেই প্রথম তিনি অর্থনীতি উন্মুক্ত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। আফিম যুদ্ধের পর থেকে চীন কার্যত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত করে রেখেছিল। দেং বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর না হলে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।
দেং ভালোভাবেই বুঝতেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার বানানো জরুরি। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে সোভিয়েত প্রভাববলয় থেকে দূরে টানতে আগ্রহী ছিল। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো পিপলস রিপাবলিক অব চায়নাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সে বছরই দেং ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন। শীতল যুদ্ধের দ্বিপাক্ষিক সন্দেহ সত্ত্বেও এই কূটনৈতিক অগ্রগতি ছিল ঐতিহাসিক।
আমেরিকা সফর শেষে দেং চীনের দক্ষিণে যান। হংকংয়ের লাগোয়া মৃতপ্রায় শিল্পকেন্দ্র গুয়াংজৌ ও তার আশপাশে তিনি পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা হাতে নেন। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার নেতা শি ঝোংসুনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার তহবিল দিতে পারবে না, তবে নীতিগত বাধা কমিয়ে উদ্যোগপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। হংকংয়ের নিকটবর্তী শহর শেনজেনকে বেছে নেওয়া হয় অগ্রাধিকারে। হংকংয়ে তৎকালীন নির্মাণ জোয়ারে স্টিলের চাহিদা আকাশছোঁয়া ছিল, কিন্তু উচ্চ মজুরি ও অবকাঠামো ব্যয়ের কারণে সেখানেই উৎপাদন লাভজনক ছিল না। শেনজেনে তুলনামূলক কম মজুরি এবং অতি স্বল্প দূরত্বের সুবিধা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় উদ্যোগীরা হংকংয়ের বিনিয়োগ আনেন, জাহাজ ভাঙা থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ দিয়ে স্টিল উৎপাদন শুরু করেন এবং তা সমুদ্রপথে দ্রুত হংকংয়ে পাঠান। এটাই ছিল চীনে বিদেশি বিনিয়োগের প্রথম সার্থক গল্প।
এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেনজেনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা হয়। পরে মডেলটি অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় প্রসারিত করা হয়। করছাড়, শুল্কসহ নানা প্রণোদনায় বিদেশি পুঁজি প্রবাহ বাড়তে থাকে। ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েনঝৌতে তুলনামূলক কম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে সরকার এসব বেসরকারি উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন দিতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেং সমষ্টিগত মতামত ও দায়িত্ববোধের নীতি চালু করেন। বড় সিদ্ধান্ত আগে আলাপ করতে হবে এবং ভুল হলে যৌথভাবে দায় নিতে হবে।
শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। মাওয়ের আমলে যেখানে স্কুলে পড়তে গেলেও পার্টির অনুমতি লাগত, সেখানে দেং উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু করেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠন করা হয়। নয় বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের মৌলিক শিক্ষা চালু হয়। পরে ধাপে ধাপে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠানো শুরু হয়। অনেকে স্থায়ীভাবে না ফিরলেও দেং-এর বাস্তববাদী যুক্তি ছিল, দশজনের মধ্যে যদি একজনও ফিরে আসে, দেশের লাভই হবে। ধীরে ধীরে বিদেশফেরত তরুণরা দেশে উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন গতি আনে।
১৯৯০–এর দশকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় বড় ব্র্যান্ড যখন উৎপাদন সম্প্রসারণের জায়গা খুঁজছিল, চীন তাদের আমন্ত্রণ জানায়। কম মজুরি, বিস্তৃত জমি, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা একত্রে বিদেশি কারখানা স্থাপনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি শেখা, সরবরাহ শৃঙ্খলা গঠন এবং মান নিয়ন্ত্রণে চীন দ্রুত দক্ষ হয়ে ওঠে। স্থানীয় উদ্যোগীরাও একই শিল্পশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে ক্রমে নিজস্ব ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে থাকে।
ক্রমশ চীন বিশ্ব উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। গবেষণা ও উন্নয়নে বড় বাজেট বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সংযোগ, এবং অবকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগের ফলে উচ্চগতির রেল, উন্নত ইলেকট্রনিক্স, ড্রোন ও রোবোটিক্সসহ বহু ক্ষেত্রে তারা আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। প্রাথমিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে স্মার্টফোন তৈরির বাজার অংশীদারিত্ব পর্যন্ত বহু খাতে চীনের প্রভাব সুদৃঢ় হয়।
সমান্তরালে দারিদ্র্য হ্রাসে তারা ব্যতিক্রমী সাফল্য দেখায়। কৃষি সংস্কার, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ মিলিয়ে কয়েক দশকে শত কোটি মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। শিক্ষা খাতে ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতা বিস্তৃত হয় এবং তরুণদের সাক্ষরতার হার প্রায় সার্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে।
উচ্চগতির রেলের উদাহরণটি দেং-এর স্বপ্ন পূরণের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালে তিনি জাপানে যে বুলেট ট্রেন দেখেছিলেন, ২০০৮ সালে চীন নিজের মাটিতে উচ্চগতির ট্রেন চালু করে। পরবর্তী দশকে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নিজেরাই নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে। আজ দেশের ভেতরে হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চগতির রেলপথ জাতীয় সংযোগ ও উৎপাদনশীলতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
সব মিলিয়ে দেং জিয়াওপিং-এর পদক্ষেপগুলোর সারকথা ছিল বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া, উন্মুক্ততার দিকে অগ্রসর হওয়া, শিক্ষা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং নীতিনির্ধারণে সমষ্টিগত জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই চীন কয়েক দশকে এক অনুন্নত অর্থনীতি থেকে একটি জটিল, প্রযুক্তিনির্ভর ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
ভোটের কাগজে বীজ, মাটিতে পড়লেই জন্মাবে সবজি
লিফলেট থেকে গাছ জন্মাবে শুনতে অবাক লাগলেও বিষয়টি মোটেই কল্পকাহিনি নয়। আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির কল্যাণে এমন কাগজ ইতোমধ্যে বাস্তবতা পেয়েছে, যা ব্যবহারের পর মাটিতে ফেললে বা পুঁতে দিলে সেখান থেকে গাছ গজায়। এই বিশেষ ধরনের কাগজ পরিচিত ‘বন-কাগজ’ বা ‘সিড পেপার’ নামে।
এবার এই ধারণার অভিনব প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–এর চেয়ারম্যান তারেক রহমান–সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও প্রার্থী প্রচারণায় ব্যবহার করছেন বীজযুক্ত এই বিশেষ লিফলেট। প্রচারণার কাগজ মাটিতে পড়েই যেন সবজির চারা হয়ে ওঠে এমন ধারণা থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
দলীয় নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের লক্ষ্য কেবল ভোটারদের কাছে বার্তা পৌঁছানো নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন এবং ‘জিরো ওয়েস্ট’ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। প্রচারণা শেষে যেখানে সাধারণ লিফলেট আবর্জনায় পরিণত হয়, সেখানে বন-কাগজ মাটিতে মিশে গিয়ে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়।
বিশ্বে পরিচিত ধারণা, বাংলাদেশে নতুন প্রয়োগ
যদিও দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এটি নতুন, তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বীজযুক্ত কাগজ একেবারেই অপরিচিত নয়। পরিবেশ রক্ষার অংশ হিসেবে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন, সামাজিক সচেতনতা ও পরিবেশ আন্দোলনে সিড পেপার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পোস্টার, আমন্ত্রণপত্র এমনকি ব্যবসায়িক কার্ডেও এই কাগজের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।
কীভাবে তৈরি হয় বন-কাগজ
বন-কাগজ তৈরির প্রক্রিয়াটিও পরিবেশবান্ধব। ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করে প্রথমে ছোট টুকরো করা হয়। এরপর প্রায় ৪২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে কাগজকে সম্পূর্ণ গলিয়ে নেওয়া হয়। এই গলিত কাগজ থেকে তৈরি হয় মণ্ড। নির্দিষ্ট ফ্রেমে সেই মণ্ড ঢেলে বিশেষ কৌশলে এর সঙ্গে বীজ যুক্ত করা হয়, যাতে কাগজ শুকানোর সময় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট না হয়। শেষে শুকিয়ে তৈরি হয় লিফলেট বা পোস্টার।
কীভাবে গাছ জন্মায় এই কাগজ থেকে
বন-কাগজের ভেতরে থাকা বীজ মাটির সংস্পর্শে এলে এবং পর্যাপ্ত আর্দ্রতা পেলে ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়। পুরো লিফলেট অথবা ছোট টুকরো করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায়। মাটি শুষ্ক হলে হালকা পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিলেই যথেষ্ট। উপযুক্ত পরিবেশে একটি বন-কাগজ থেকেই ধীরে ধীরে চারা গজিয়ে গাছে পরিণত হয়। এই কাগজ এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে, অর্থাৎ তৈরি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মাটিতে ফেললে গাছ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।
কোন বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে
এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় পাঁচ ধরনের দেশি সবজির বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো বেগুন, টমেটো, মরিচ, লালশাক ও ডাঁটাশাক। এসব সবজি সহজে জন্মায় এবং ঘরোয়া পরিবেশে পরিচর্যাও তুলনামূলক কম লাগে। তাই কেউ চাইলে বারান্দা বা ছাদের টবে এই লিফলেট পুঁতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সবজির চারা পেতে পারেন। এক মাসের মধ্যেই মিলতে পারে নিজ হাতে ফলানো সবজি।
খরচ বেশি, সুফল দীর্ঘমেয়াদি
সাধারণ কাগজের তুলনায় বন-কাগজের খরচ কিছুটা বেশি। প্রতিটি সিড পেপার লিফলেট তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৮ টাকা। তবে উদ্যোক্তারা মনে করেন, পরিবেশ দূষণ কমানো, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং বর্জ্যহীন প্রচারণার সুফল বিবেচনায় এই ব্যয় যুক্তিসংগত। পরিবেশবিদদের মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
রাজনীতির কাগজ যদি মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে ওঠে তাহলে সেটিই হয়তো হবে প্রচারণার সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা।
সবাই যেদিকে যায় সেদিকে সে নেই: ভাইরাল পেঙ্গুইনের একাকী যাত্রার নেপথ্য কাহিনী

মোঃ আশিকুজ্জামান
নিজস্ব প্রতিবেদক
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি একাকী পেঙ্গুইন তার দল ছেড়ে বিশাল বরফাবৃত পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটি আসলে কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয় বরং এটি ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জার্মান চলচ্চিত্র নির্মাতা ভার্নার হারজগের বিখ্যাত ডকুমেন্টারি 'এনকাউন্টারস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' থেকে নেওয়া একটি অংশ। ভিডিওর সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে দেখা যায় এন্টার্কটিকার একদল অ্যাডেলি পেঙ্গুইন তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সমুদ্রের খাবারের সন্ধানে এগোচ্ছে ঠিক তখনই একটি পেঙ্গুইন হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এবং দল ছেড়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে অর্থাৎ জনমানবহীন ও প্রাণহীন বিশাল এক পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করে। পরিচালক হারজগ এই একাকী পথচলাকে একটি 'ডেথ মার্চ' বা মৃত্যুর পথে যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কারণ পাহাড়ের সেই প্রতিকূল পরিবেশে কোনো খাবারের অস্তিত্ব নেই এবং এই পথচলা পেঙ্গুইনটির নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে। বিজ্ঞানীরাও এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে এমনকি পেঙ্গুইনটিকে জোর করে তার দলের কাছে ফিরিয়ে আনলেও সে আবারও একই জেদ নিয়ে পাহাড়ের দিকেই হাঁটতে শুরু করবে।
২০২৬ সালে এসে এই ভিডিওটি নতুন করে ভাইরাল হওয়ার পেছনে কাজ করছে এক গভীর আবেগীয় ও প্রতীকী কারণ। বর্তমান সময়ের মানুষ যারা তীব্র মানসিক চাপ বা 'বার্নআউট'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা এই পেঙ্গুইনটির একাকী ও লক্ষ্যহীন পথচলার মাঝে নিজেদের জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছেন। অনেকে সামাজিক প্রথা বা গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মতো চলার এক প্রতীকী সাহস হিসেবে একে দেখছেন যদিও সেই পথটি শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি 'হোপকোর' বা অনুপ্রেরণামূলক ক্যাটাগরিতে শেয়ার হচ্ছে যেখানে অনেকেই লিখছেন যে সে হয়তো নিজের গন্তব্য পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে নিজের ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার সাহস যুগিয়েছে। এই চর্চা আরও গতি পায় যখন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়ে একটি পোস্ট করেন তবে সেই পোস্টে গ্রিনল্যান্ড ও পেঙ্গুইনের অবস্থান নিয়ে ভৌগোলিক ভুল থাকায় তা ইন্টারনেটে হাস্যরসের সৃষ্টি করে।
মানুষ এই ঘটনাকে দার্শনিক বা বীরত্বপূর্ণ রূপ দিলেও বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অবশ্য বেশ নিস্পৃহ ও সরাসরি। তাঁদের মতে এই পেঙ্গুইনটির আচরণে কোনো মহান উদ্দেশ্য বা সাহসিকতা নেই বরং এটি মূলত একটি স্নায়বিক বিভ্রান্তি বা 'ডিসঅরিয়েন্টেশন'। পেঙ্গুইনরা সাধারণত সমুদ্রের দিক নির্ণয় করার জন্য প্রকৃতির কিছু নির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করে থাকে কিন্তু কোনো কারণে এই পেঙ্গুইনটির মস্তিষ্ক সেই সংকেত বুঝতে ভুল করেছিল অথবা কোনো স্নায়বিক সমস্যার কারণে সে সঠিক দিক হারিয়ে ফেলেছিল। তবে বিজ্ঞানের এই নিরস ব্যাখ্যার চেয়ে মানুষের কাছে এটি এখন আর কেবল একটি পাখির ভুল হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি একাকিত্ব, মানসিক অবসাদ এবং প্রথা ভাঙার এক গভীর আবেগীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে যা ২০ বছর আগের একটি ডকুমেন্টারি দৃশ্যকে আজ ইন্টারনেটের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে রূপান্তর করেছে।
যে দেশে মা ও দাদির সাথে সুর মিলিয়ে কান্না না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় বিয়ে
বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিয়ে মানেই উৎসব ও নাচের আয়োজন হলেও চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টুজিয়া সম্প্রদায়ের রীতি একদম ভিন্ন। এখানে বিয়ের আগে কনের কান্না করাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য হিসেবে দেখা হয়। কিং রাজবংশের শেষ যুগ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথাটি বর্তমানে আধুনিক শহরগুলোতে কমে গেলেও গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় এখনও টিকে আছে। এটি কেবল চোখের জল নয় বরং একটি সংগীতময় প্রকাশ যাকে ক্রাই সং বলা হয়। কনে এই গানের মাধ্যমে তার পরিবার ও মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং নতুন জীবনে প্রবেশের আবেগ প্রকাশ করে।
বিয়ের অন্তত এক মাস আগে থেকেই কনেকে প্রতিদিন কান্নার এই প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। প্রথা অনুযায়ী কনে প্রতিদিন রাতে একটি বিশেষ ঘরে বসে এক ঘণ্টা করে কাঁদে। দশ দিন পর তার সাথে যোগ দেন মা এবং আরও দশ দিন পর দাদি বা নানি সহ পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক নারীরা এই কান্নার আসরে সামিল হন। অনেক ক্ষেত্রে কনের বান্ধবীরাও একত্রিত হয়ে কাঁদে এবং গান গায় যা টেন সিস্টার গ্যাদারিং নামে পরিচিত। এই দীর্ঘমেয়াদী কান্নার প্রক্রিয়াটি জুও তাং বা হলে বসে থাকা হিসেবে টুজিয়া সমাজে সমাদৃত।
প্রাচীনকালে এই কান্নার পেছনে একটি সামাজিক বিদ্রোহের দিকও ছিল। তখন মেয়েদের বিয়ে সাধারণত ঘটক বা মা-বাবার পছন্দে হতো বলে কনে কান্নার মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরত। এমনকি প্রথা অনুযায়ী কনে যদি যথেষ্ট পরিমাণ না কাঁদতে পারত তবে তাকে অশিক্ষিত বা নিচু পরিবারের মেয়ে হিসেবে সামাজিকভাবে সমালোচনা করা হতো। অনেক সময় কনের মা তাকে পর্যাপ্ত কান্নার জন্য শাস্তিও দিতেন। কান্নার গানের লিরিক্সে অনেক সময় ঘটককে তিরস্কার করার বিষয়টিও উঠে আসত যা এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদের প্রতীক ছিল।
বর্তমানে টুজিয়া সম্প্রদায়ের এই প্রথাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর হিসেবে দেখা হয়। কান্নার মাধ্যমে কনে তার ফেলে আসা জীবনের সব স্মৃতি ও দুঃখকে বিদায় জানিয়ে নতুন জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। গ্রামীণ ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ মনে করে এই রীতি কনের সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। আধুনিক জীবনের প্রভাবে অনেক কিছু বদলে গেলেও টুজিয়াদের এই ক্রাইং ম্যারেজ আজও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সূত্র: ডেইলি চায়না
এক চড়, দশ হাজার টাকা, আর চিরকালের নত মেরুদণ্ড
ব্রিটিশ শাসনামলে একদিন এক ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা রাগের বশে এক তরুণ ভারতীয় যুবকের গালে সপাটে চড় বসান। মুহূর্তের মধ্যেই যা ঘটল, তা উপনিবেশিক অহংকারের ইতিহাসে বিরল। কোনো দ্বিধা না করে সেই তরুণ পূর্ণ শক্তিতে পাল্টা চড় মারল। আঘাতে ইংরেজ কর্মকর্তা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বিস্ময়, অপমান আর অবিশ্বাস একসঙ্গে তাকে গ্রাস করল। কীভাবে এক “সাধারণ” ভারতীয় যুবক সাহস পেল এমন এক সামরিক কর্মকর্তার গায়ে হাত তুলতে, যে সাম্রাজ্যের সূর্য নাকি কখনো অস্ত যেত না।
ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা ছুটে গেলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের কাছে। দাবি একটাই, কঠোর শাস্তি। কিন্তু প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে কমান্ডার শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওই যুবককে শাস্তি নয়, পুরস্কৃত করতে হবে। পুরস্কার হিসেবে তাকে দিতে হবে দশ হাজার রুপি। শুনে ইংরেজ কর্মকর্তা বিস্ফোরিত হলেন। এটি কেবল ব্যক্তিগত অপমান নয়, ব্রিটিশ রাণীর অপমান, আর তার জবাবে পুরস্কার। কিন্তু আদেশ আদেশই। আপত্তির কোনো সুযোগ নেই।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্মকর্তা সেই ভারতীয় যুবকের হাতে দশ হাজার রুপি তুলে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। যুবক টাকা নিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলে গেল একদিন নিজের দেশেই এক ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার হাতে অপমানিত হওয়ার কথা। সে সময় দশ হাজার রুপি ছিল অকল্পনীয় সম্পদ। সে অর্থ কাজে লাগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয়ে উঠল ধনী, সমাজে সম্মানিত, প্রভাবশালী। একসময়ের সাধারণ মানুষ এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি।
বছর কেটে গেল। একদিন সেই একই ঊর্ধ্বতন কমান্ডার আবার তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাকে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন, ওই ভারতীয়কে কি মনে আছে। কর্মকর্তার চোখে তৎক্ষণাৎ পুরোনো অপমান জ্বলে উঠল। কমান্ডার তখন বললেন, সময় এসেছে। যাও, তাকে খুঁজে বের করো এবং সবার সামনে আবার গালে চড় মারো।
ভয়ে কাঁপতে লাগল কর্মকর্তা। সে বলল, তখন সে গরিব ছিল, তবু প্রতিশোধ নিয়েছিল। এখন সে ধনী, প্রভাবশালী। এবার সে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কমান্ডার কঠোর স্বরে বললেন, এটিও আদেশ।
আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। কর্মকর্তা গেলেন। সবার সামনে সেই ভারতীয়কে চড় মারলেন। কিন্তু এবার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া নেই। লোকটি চোখ তুলেও তাকাল না। নীরবে অপমান সহ্য করল।
হতবাক কর্মকর্তা ফিরে এসে কমান্ডারকে সব বললেন। তখন কমান্ডার ধীরে, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, প্রথমবার ওই যুবকের কাছে ছিল শুধু তার সম্মান। সেটাই ছিল তার সবকিছু। তাই সে প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু আজ সে আর সম্মান রক্ষা করল না, কারণ এখন তার কাছে এমন কিছু আছে, যা সে সম্মানের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে, তার সম্পদ। যেদিন সে ওই দশ হাজার রুপি গ্রহণ করেছিল, সেদিনই সে নিজের মর্যাদা বিক্রি করে দিয়েছিল। আর যে মানুষ নিজের আত্মসম্মান বিক্রি করে, তার মেরুদণ্ড চিরতরে নুয়ে যায়।
এই গল্প কেবল অতীতের কোনো উপনিবেশিক উপাখ্যান নয়। এটি আজকের জন্য এক নির্মম আয়না। আমরা কতবার সত্যকে চেপে গেছি সুবিধার জন্য। কতবার না জেনে কাউকে কলঙ্কিত করেছি। কতবার অবস্থান, উপহার কিংবা লোভের কাছে মাথা নত করেছি। প্রতিবারই হয়তো আমরা আমাদের আত্মসম্মানের এক একটি অংশ বিক্রি করেছি।
এখনই সময় নিজেকে প্রশ্ন করার। আমরা কি আমাদের হৃদয় ও বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করছি। ক্ষমা চাইবার সময় এখনই, যাতে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষত থাকে। পদ, উপহার কিংবা লোভের কাছে কখনো নত না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই মানুষের আসল পরিচয়। প্রশ্ন একটাই, আমরা কি সেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব।
(অনূদিত)
কেন ১ জানুয়ারি নতুন বছর? জানুন এর পেছনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস
পৃথিবীজুড়ে আতশবাজি আর উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, বছরের শুরুর এই দিনটি সবসময় ১ জানুয়ারি ছিল না। প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে বছরের শুরু হতো ১ মার্চ থেকে এবং বছরে মাস ছিল মাত্র ১০টি। যার রেশ আজও রয়ে গেছে আমাদের ক্যালেন্ডারে; ল্যাটিন শব্দ 'Septem' মানে ৭, সেই হিসেবে সেপ্টেম্বর ছিল সপ্তম মাস এবং 'Decem' মানে ১০ অনুযায়ী ডিসেম্বর ছিল দশম মাস। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের অসামঞ্জস্য দূর করতেই শুরু হয় সংস্কার।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের পরামর্শে ‘জুলিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন। সিজারই প্রথম জানুয়ারির ১ তারিখকে বছরের শুরু হিসেবে ঘোষণা করেন। এই মাসের নামকরণ করা হয়েছিল রোমান দেবতা ‘জানুস’-এর নামানুসারে। জানুসের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর দুটি মুখ—একটি পেছনের দিকে (অতীত দেখার জন্য) এবং অন্যটি সামনের দিকে (ভবিষ্যৎ দেখার জন্য)। নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে এই মাসটিকেই বছরের সূচনার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়।
রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে ইউরোপের অনেক দেশ ধর্মীয় কারণে ১ জানুয়ারিকে বছরের শুরু হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা ২৫ ডিসেম্বর বা ২৫ মার্চকে বছরের শুরু হিসেবে পালন করত। তবে ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ক্যালেন্ডারের ভুল সংশোধন করে ‘গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন এবং পুনরায় ১ জানুয়ারিকে বছরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং বর্তমানের সার্বজনীন ক্যালেন্ডারে রূপ নেয়।
বর্তমানে ১ জানুয়ারি কেবল একটি তারিখ পরিবর্তনের দিন নয়, বরং বিশ্বজুড়ে প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগের একটি সাধারণ মানদণ্ড। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রোমান দেবতা জানুসের সেই শিক্ষা—অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকাতে। হাজার বছরের সংস্কার আর বিবর্তন পেরিয়ে আজ এই দিনটি বিশ্বের বৃহত্তম ও সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।
সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস
গাছ কাটলে গাছের কি সত্যিই ব্যথা লাগে? বিজ্ঞান কী বলে
গাছের কি ব্যথা লাগে-এই প্রশ্নটি অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। উদ্ভিদের শরীরে কোনো ব্যথা অনুভবকারী রিসেপ্টর, স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক নেই। ফলে প্রাণিজগতের সদস্য হিসেবে মানুষ বা পশু যেভাবে ব্যথা অনুভব করে, উদ্ভিদ সেই অর্থে ব্যথা অনুভব করতে সক্ষম নয়। তাই একটি গাজর মাটি থেকে তুলে নেওয়া, ঝোপঝাড় ছাঁটা বা একটি আপেল কামড়ে খাওয়া কোনোভাবেই ‘উদ্ভিদ নির্যাতন’ হিসেবে বিবেচিত হয় না।
তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, উদ্ভিদ সম্পূর্ণ সংবেদনশূন্য নয়। তারা শারীরিক উদ্দীপনা, স্পর্শ বা ক্ষতির উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারে যদিও সেটি ব্যথা নয়, বরং জৈব-রাসায়নিক ও কোষীয় প্রতিক্রিয়া।
কিছু উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে। যেমন ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ নামের উদ্ভিদটি অর্ধ সেকেন্ডের মধ্যেই পাতা বন্ধ করে শিকার ধরে ফেলতে পারে। আবার লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ পেলেই পাতা গুটিয়ে নেয়, যা সম্ভাব্য তৃণভোজী প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখার একটি প্রতিরক্ষামূলক কৌশল বলে মনে করা হয়। এই উদ্ভিদগুলোর আচরণে স্পষ্টতই একধরনের সংবেদনশীল ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়।
তবে আরও বিস্ময়কর তথ্য এসেছে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে। দেখা গেছে, সাধারণ সরিষা জাতের একটি উদ্ভিদ যা গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত পাতায় পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে কোষীয় স্তরে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে পারে। এই সংকেত এক পাতা থেকে আরেক পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদকে সতর্ক করে দেয় যেন সে দ্রুত রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে। ফলে শুঁয়োপোকা বা এফিডের মতো ক্ষতিকর পোকা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
এই বৈদ্যুতিক সংকেত শুনে অনেকের মনে হতে পারে, উদ্ভিদ বুঝি ব্যথা পাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে বলছেন, এই সংকেত কোনোভাবেই প্রাণীর ব্যথার সংকেতের মতো নয়। এখানে কোনো অনুভূত যন্ত্রণা নেই, নেই সচেতন কষ্টবোধ। এটি নিছক একটি প্রতিরক্ষামূলক সংকেত ব্যবস্থা, যা উদ্ভিদের টিকে থাকার কৌশলের অংশ।
উদ্ভিদ আলো, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের প্রবাহ এমনকি ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের আক্রমণও শনাক্ত করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভূতির ফল নয়, বরং কোটি কোটি বছরের বিবর্তনে গড়ে ওঠা জৈবিক অভিযোজন। উদ্ভিদের জীবনধারা ‘কষ্ট বনাম সুখ’ দিয়ে পরিচালিত নয়; বরং এটি পরিচালিত হয় টিকে থাকা বা বিলুপ্তির সরল বাস্তবতায়।
সুতরাং, উদ্ভিদের এই অসাধারণ সক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করলেও, তাদের মানুষের মতো ব্যথা অনুভবকারী জীব হিসেবে কল্পনা করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। উদ্ভিদ অনুভব করে না—তারা প্রতিক্রিয়া জানায়।
সূত্র: ব্রিটানিকা
অলিম্পিক স্বর্ণপদক কি সত্যিই খাঁটি সোনা, জানুন ইতিহাস
অলিম্পিকের মঞ্চে সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে গলায় স্বর্ণপদক পরার মুহূর্তটি যেকোনো ক্রীড়াবিদের কাছে অমূল্য। তবে আবেগের দিক থেকে যতটাই মূল্যবান হোক না কেন, বাস্তব অর্থমূল্যের বিচারে অলিম্পিক স্বর্ণপদক রুপার পদকের চেয়ে খুব বেশি দামী নয়। এর কারণ হলো, অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণপদক আসলে সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি নয়।
অলিম্পিক গেমস–এর বিধিমালা অনুযায়ী, স্বর্ণপদকে কমপক্ষে ৯২.৫ শতাংশ রুপা থাকতে হয় এবং তার ওপরে মাত্র প্রায় ছয় গ্রাম খাঁটি সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। একইভাবে রুপার পদকও ৯২.৫ শতাংশ রুপা দিয়ে তৈরি হয়। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ পদক বানানো হয় তামা ও বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে। ফলে স্বর্ণ ও রুপার পদকের উপাদানগত পার্থক্য খুবই সীমিত।
পদক প্রদানের এই রীতি আদতে খুব প্রাচীন নয়। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয় ১৮৯৬ সালে গ্রিসের এথেন্সে। তবে সে সময়কার পদকগুলো আজকের পরিচিত স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ কাঠামোর মতো ছিল না। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসরে বিজয়ীদের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়নি।
প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস আরও পেছনে গেলে দেখা যায়, প্রায় ২ হাজার ৮০০ বছর আগে, খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে শুরু হওয়া প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের মাথায় পরানো হতো বিজয়ের মুকুট। এসব মুকুট সাধারণত স্থানীয় উদ্ভিদ যেমন লরেল পাতা বা জলপাই শাখা দিয়ে তৈরি করা হতো। তখন পদকের ধারণাই ছিল না।
১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো পদক প্রদান শুরু হলেও সেখানে মাত্র দুটি পদক দেওয়া হতো। প্রথম স্থান অধিকারী পেতেন রুপার পদক এবং দ্বিতীয় স্থান পাওয়া প্রতিযোগী পেতেন তামার পদক। তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের জন্য কোনো পুরস্কারই নির্ধারিত ছিল না।
এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। সে আসরে কিছু খেলায় প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তখনই স্বর্ণ, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকের ধারণা চালু হয়। তবে সেবার পদকগুলো ছিল আয়তাকার, যা অলিম্পিক ইতিহাসে একমাত্র ব্যতিক্রম। সেই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে পদকের পরিবর্তে ট্রফি বা শিল্পকর্মও দেওয়া হয়েছিল।
১৯০৪ সালের পর থেকে স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ পদকের রীতি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১২ সালের অলিম্পিকে দেওয়া স্বর্ণপদক সত্যিকার অর্থেই খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯১৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় খাঁটি সোনার পদক দেওয়া আর সম্ভব হয়নি।
বর্তমানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পদকের ধাতব গঠন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও, আয়োজক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে পদকে বিশেষ উপাদান যোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন, ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে পদকে জেড পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।
একই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে প্রতিটি পদকের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক আইফেল টাওয়ার–এর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এর মাধ্যমে অলিম্পিক পদক কেবল একটি পুরস্কার নয়, বরং আয়োজক শহরের ইতিহাস ও পরিচয়ের প্রতীক হিসেবেও নতুন মাত্রা পেয়েছে।
সূত্র: ব্রিটানিকা
ইন্টারনেট ছাড়াই চলবে গুগল ম্যাপস: জেনে নিন অফলাইন ব্যবহারের নিয়ম
অচেনা কোনো শহর বা নতুন কোনো গন্তব্যে যাওয়ার পথে বর্তমানে গুগল ম্যাপস আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবে অনেক সময় নেটওয়ার্কের দুর্বলতা কিংবা ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝপথে বিপাকে পড়তে হয়। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা বা বিদেশ ভ্রমণের সময় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবহারকারীদের এই ভোগান্তি দূর করতে গুগল ম্যাপসে রয়েছে ‘অফলাইন’ সুবিধা যা সক্রিয় থাকলে কোনো ধরনের ইন্টারনেট ডাটা ছাড়াই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন মোড ব্যবহারের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর। এটি ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীকে প্রথমে স্মার্টফোনের গুগল ম্যাপস অ্যাপে প্রবেশ করে প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে। সেখানে থাকা 'অফলাইন ম্যাপস' অপশনে গিয়ে ‘সিলেক্ট ইয়োর ওউন ম্যাপ’ নির্বাচন করতে হবে। এরপর যে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহরের মানচিত্র ভবিষ্যতে অফলাইনে ব্যবহারের প্রয়োজন তা জুম ইন বা আউট করে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে ডাউনলোড বাটনে প্রেস করলেই সেই এলাকার মানচিত্রটি ফোনের মেমোরিতে জমা হয়ে যাবে। একবার সফলভাবে ডাউনলোড হয়ে গেলে পরবর্তী যেকোনো সময় ইন্টারনেট ছাড়াই ওই এলাকার পথঘাট দেখা যাবে।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন সংস্করণে গাড়ি চালানোর দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুবিধা থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় রাস্তার রিয়েল-টাইম ট্রাফিক পরিস্থিতি বা জ্যামের খবর জানা সম্ভব হয় না। এছাড়া বিকল্প রুট এবং গণপরিবহনের সঠিক সময়সূচিও এই মোডে দেখা যাবে না। তবে ইন্টারনেট ছাড়াই স্মার্টফোনের জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সবসময় সক্রিয় থাকে যা ডাউনলোড করা মানচিত্রের ওপর ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান ও গন্তব্যের দূরত্ব নিখুঁতভাবে দেখাতে পারে।
ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এই ফিচারটি আশীর্বাদস্বরূপ কারণ বিদেশের মাটিতে দামী ইন্টারন্যাশনাল রোমিং বা লোকাল সিম কার্ডের ডাটা খরচ না করেই তারা মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। ভ্রমণের আগেই প্রয়োজনীয় শহরের ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখলে স্মার্টফোনটি অনেকটা পুরোনো আমলের পকেট ম্যাপের মতোই কার্যকর হয়ে ওঠে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অফলাইন নেভিগেশনের এই সুবিধা কেবল ডেটাই সাশ্রয় করে না বরং জরুরি মুহূর্তে পথ হারানোর ভয় থেকেও ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত রাখে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
জিমেইল স্টোরেজ ফুল? টাকা খরচ না করে জায়গা খালি করার ৫ উপায়
বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগাযোগে জিমেইল একটি অপরিহার্য মাধ্যম। তবে গুগলের নির্ধারিত ১৫ জিবি স্টোরেজ দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যবহারকারীরা বিপাকে পড়েন। স্টোরেজ পূর্ণ থাকলে গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইলগুলো প্রাপকের কাছে না পৌঁছে ফিরে আসে অথবা অনেক ক্ষেত্রে নতুন মেইল আসাও বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে গুগল অতিরিক্ত স্টোরেজের জন্য অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার প্রস্তাব দিলেও সামান্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে কোনো খরচ ছাড়াই এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব।
জিমেইলের জায়গা খালি করার জন্য প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ট্র্যাশ এবং স্প্যাম ফোল্ডারের দিকে। সাধারণত মুছে ফেলা ই-মেইলগুলো সরাসরি ডিলিট না হয়ে ট্র্যাশ ফোল্ডারে ৩০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে যা অযথাই স্টোরেজ দখল করে রাখে। নিয়মিত এই ফোল্ডারগুলো ম্যানুয়ালি খালি করার মাধ্যমে অনেকটা জায়গা তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার করা যায়। এছাড়া ই-মেইলের বড় অ্যাটাচমেন্টগুলো স্টোরেজ পূর্ণ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। জিমেইলের সার্চ বক্সে বিশেষ কোড ব্যবহার করে ১০ মেগাবাইটের বেশি সাইজের ই-মেইলগুলো চিহ্নিত করে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো ডিলিট করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা অপ্রয়োজনীয় নিউজলেটার জিমেইলের প্রমোশন ট্যাবে জমে থেকে ইনবক্সকে ভারী করে তোলে। নিয়মিতভাবে এই ধরনের নিউজলেটারগুলো আনসাবস্ক্রাইব করলে ভবিষ্যৎ স্টোরেজ অপচয় রোধ করা যায়। এছাড়া গুগলের ‘ওয়ান স্টোরেজ ম্যানেজার’ টুলটি ব্যবহার করে এক নজরে ড্রাইভ, ফটোস এবং জিমেইলের বড় ফাইলগুলো দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। বড় সাইজের ছবি বা ভিডিও সরাসরি মেইলে না পাঠিয়ে গুগল ড্রাইভের লিংক শেয়ার করাও স্টোরেজ সাশ্রয়ের একটি আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জিমেইলের স্টোরেজ পূর্ণ হওয়া মানেই টাকা খরচ করে নতুন মেমোরি কেনা নয় বরং ডিজিটাল হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাই এর মূল সমাধান। নিয়মিত ইনবক্স পরিষ্কার রাখা এবং ক্লাউড স্টোরেজের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা বছরের পর বছর কোনো চার্জ ছাড়াই জিমেইলের নিরবচ্ছিন্ন সেবা উপভোগ করতে পারবেন। এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে কেবল স্টোরেজই বাঁচবে না বরং জিমেইলের গতি ও কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পাবে।
পাঠকের মতামত:
- কুখ্যাত জেফ্রি অ্যাপস্টেইন ফাইলে শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেতার নাম
- এপস্টেইন কেলেঙ্কারি: তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে রাজি বিল ও হিলারি ক্লিনটন
- যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য যুদ্ধে ইতি! ট্রাম্পের ঘোষণার পরই চাঙ্গা ভারতের বাজার
- নির্বাচনি ব্যয়ের লাগাম টানার লড়াই: কালো টাকা রুখতে বিএফআইইউ-র কড়াকড়ি
- স্বর্ণের দামে বড় ধস: আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন মূল্য তালিকা
- আজ ঢাকায় যেসব এলাকার মার্কেট ও দোকান বন্ধ
- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- রাজধানীতে আজ কোথায় কী? বের হওয়ার আগে দেখে নিন কর্মসূচির তালিকা
- আজকের নামাজের সময়সূচি: জেনে নিন পাঁচ ওয়াক্তের ওয়াক্ত
- দেশে ফের ভূমিকম্প, কেঁপে ওঠে কয়েকটি জেলা
- শবে বরাতের রোজা ও তওবা-ইস্তিগফারের গুরুত্ব
- আজ পবিত্র শবেবরাত, খুলেছে রহমতের দরজা
- মঙ্গলের বুকে এআই-এর রাজত্ব: প্রথমবারের মতো মানুষের বদলে পথ দেখালো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
- বিশ্বজুড়ে তোলপাড়: এপস্টেইন ফাইলের ৩০ লাখ পৃষ্ঠায় ক্ষমতাধরদের অন্ধকার জগত
- রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের সুফল: শক্তিশালী অবস্থানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ
- নতুন নকশায় ১০ টাকার ব্যাংক নোট: এক নজরে দেখে নিন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
- সদরপুরে পদ্মা নদীর চর থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন: ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা
- নির্বাচনী উত্তাপে ‘কুমিল্লা বিভাগ’; নাম নিয়ে দীর্ঘদিনের জট কি এবার খুলবে?
- লাশের ওপর দাঁড়িয়ে জয়ের চেষ্টা করছে প্রতিদ্বন্দ্বীরা: নাহিদ ইসলাম
- সাবেক মন্ত্রী আমুর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মিলল যত টাকা
- সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ছাত্রদল নেতা রনির মৃত্যু
- গৃহকর্মী শিশুকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা! বিমানের এমডি শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার
- কক্সবাজারে ডা. শফিকুর রহমানের হুংকার: ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্যাসিবাদকে লাল কার্ডের ডাক
- স্বর্ণের বাজারে বড় ধস; ২৪ ঘণ্টায় তিন দফায় কমলো দাম
- যশোরে তারেক রহমানের হুংকার: নাম না নিয়ে জামায়াতের কড়া সমালোচনা
- ফেব্রুয়ারিতে এলপিজির নতুন ধাক্কা: আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হচ্ছে বাড়তি দাম
- নারীবিদ্বেষীরা দেশপ্রেমিক হতে পারে না: তারেক রহমান
- ২ ফেব্রুয়ারি শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- ২ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ দরপতনের ১০ শেয়ার
- ২ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ দরবৃদ্ধিকারী ১০ শেয়ার
- ২০২৬ এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে জরুরি নির্দেশনা
- শবেবরাত পালনে কী করবেন, কী করবেন না
- জামায়াত বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়: ফখরুল
- কীভাবে ইস্তেগফার করবেন, জানুন ফজিলতসহ সহজ নিয়ম
- বিটরুট কেন সুপারফুড, জানুন এর স্বাস্থ্যগুণ
- খুলনায় বিএনপির সমাবেশে নেতাকর্মীদের উপচে পড়া ভিড়
- একদিনে দুই দফা স্বর্ণের দাম কমাল বাজুস, এক ভরিতে কমল যত
- মায়ের বুকে ফেরার শেষ চেষ্টা: কবরের ভেতরেই আশ্রয় নিল ছোট্ট শিশু
- ৯ আসনে নেই ধানের শীষ: সমঝোতা ও আইনি মারপ্যাঁচে ব্যালট থেকে উধাও বিএনপির প্রতীক
- পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ও পুরুষ বন্ধ্যত্ব: গবেষণায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য
- গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের ওপর নির্ভরতা কমান: জেনে নিন ৫টি ঘরোয়া সমাধান
- আজকের টাকার রেট: জেনে নিন বিদেশি মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার
- হাজিদের অধিকার রক্ষায় কঠোর সৌদি আরব: ওমরাহ এজেন্সির চুক্তি স্থগিত নিয়ে তোলপাড়
- দুধ দিয়ে গোসল করে ধানের শীষ হাতে নিলেন আওয়ামী লীগ কর্মী
- পাক-ভারত ম্যাচ বয়কট ইস্যুতে পিসিবি-কে আইসিসি-র কড়া সতর্কবার্তা
- রাজধানীতে আজ কোথায় কী? বের হওয়ার আগে দেখে নিন কর্মসূচির তালিকা
- বাড়ছে না কমছে? সিলিন্ডার গ্যাসের নতুন দাম ঘোষণা আজ
- আজ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে জামায়াত আমির; এক দিনে ৫ জনসভায় ভাষণ
- শিল্পাঞ্চল থেকে উপশহর: আজ খুলনা ও যশোরে তারেক রহমানের বিশেষ মিশন
- স্বস্তি ফিরলো স্বর্ণের বাজারে; আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম
- স্বর্ণের দামে বড় পতন, ট্রাম্পের ঘোষণায় স্বর্ণবাজারে অস্থিরতা
- তারেক রহমানকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন: ‘Bangladesh’s Prodigal Son’
- বিশ্ববাজারে রেকর্ড দরপতন; দেশেও কমল স্বর্ণের দাম
- স্বস্তি ফিরলো স্বর্ণের বাজারে; আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম
- মেধাবীদের হাত ধরেই গড়তে হবে নতুন বাংলাদেশ: সিলেটে ব্যারিস্টার নাজির আহমদকে সংবর্ধনা
- তিন দিনে ভরিতে বাড়ল ২৮ হাজার, স্বর্ণে রেকর্ড
- আজ ৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে একাধিক এলাকা
- রুপার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ, ভরি ছাড়াল যত
- কালিগঞ্জে জমি বিরোধে সংঘবদ্ধ হামলা, চারজন গুরুতর আহত
- একদিনে দুই দফা স্বর্ণের দাম কমাল বাজুস, এক ভরিতে কমল যত
- রেকর্ড ভেঙে ছুটছে স্বর্ণ ও রুপা: নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীরা
- আজ প্রাইজবন্ডের ১২২তম ড্র: জেনে নিন প্রাইজবন্ডের ফলাফল দেখার সহজ নিয়ম
- আগামী পাঁচ দিন কেমন থাকবে দেশের আবহাওয়া
- রিয়েল এস্টেটে বড় স্বস্তি, ফ্ল্যাট ও জমি নিবন্ধনে বিরাট সুখবর
- আজ ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে যেসব এলাকা