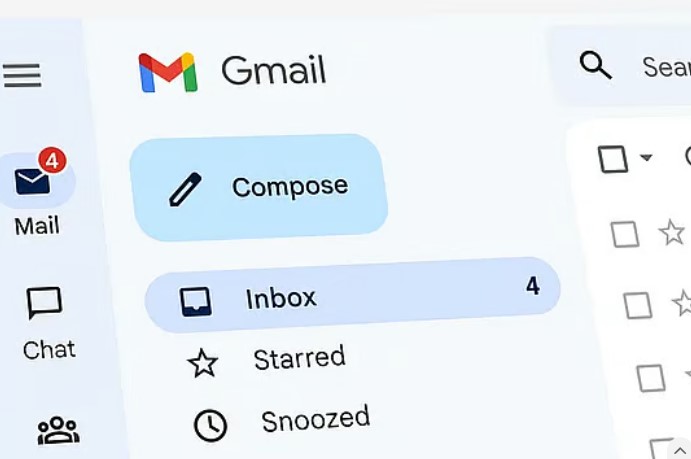কেন বিড়াল-কুকুর ঘাস খায়, বিজ্ঞান কী বলে?

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, পোষা কুকুর বা বিড়াল মাঝেমধ্যে ঘাস খায়। বিষয়টি অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে—বিশেষ করে বিড়ালের ক্ষেত্রে, যাদের খাদ্যতালিকায় সাধারণত মাছ বা মাংসই থাকে। তাহলে আসলে কেন তারা ঘাস খায়?
নিউ ইয়র্কের সিরাকিউসের স্ট্যাক ভেটেরিনারি হাসপাতাল-এর পশুচিকিৎসক ড. জেমি লাভজয়ের মতে, এই আচরণের পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। যদিও কুকুর ও বিড়ালের হজমতন্ত্র ঘাসের মতো আঁশযুক্ত উদ্ভিদ ভাঙতে তেমন উপযোগী নয়, তবুও তারা নিয়মিত এমন কাজ করে। ঘাস খাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া ও দীর্ঘ পরিপাকতন্ত্র সাধারণত তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যা বিড়াল-কুকুরের নেই।
অসুস্থতার জন্য নয়, বরং স্বভাবজাত অভ্যাসএকটি প্রচলিত ধারণা হলো—পোষা প্রাণী পেট খারাপ বা বমির উদ্দেশ্যে ঘাস খায়। তবে গবেষণা বলছে, এ ধারণা সবসময় সঠিক নয়।২০০৮ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ১,৫৭১ জন কুকুর মালিকের মধ্যে ৬৮% জানিয়েছেন, তাদের কুকুর নিয়মিত বা সপ্তাহে অন্তত একবার ঘাস খায়। কিন্তু মাত্র ৮% বলেছেন, ঘাস খাওয়ার আগে তাদের কুকুর অসুস্থতার লক্ষণ দেখিয়েছিল।
২০২১ সালে অ্যানিম্যালস জার্নালে প্রকাশিত দুটি আলাদা জরিপে বিড়াল মালিকদের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। প্রথম জরিপে মাত্র ৬% ও দ্বিতীয়টিতে ৯% মালিক বলেছেন, ঘাস খাওয়ার আগে তাদের বিড়াল অসুস্থ লাগছিল। তবে ঘাস খাওয়ার পর যথাক্রমে ২৭% ও ৩৭% বিড়াল ঘন ঘন বমি করেছে। একই গবেষণায় দেখা গেছে, ৭১% মালিক তাদের বিড়ালকে অন্তত ছয়বার লতাপাতা খেতে দেখেছেন।
চুলের জন্য ঘাস খাওয়া? প্রমাণ নেইঅনেকে মনে করেন, বিড়াল চুল গিললে তা বের করার জন্য ঘাস খায়। তবে গবেষণায় লম্বা চুলওয়ালা ও ছোট চুলওয়ালা বিড়ালের ঘাস খাওয়ার হারে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি।
স্বভাবের শিকড়ে বন্য পূর্বপুরুষ গবেষকরা জানিয়েছেন, বন্য কুকুর ও বিড়ালেরও ঘাস খাওয়ার প্রবণতা আছে। ধারণা করা হয়, এটি পরজীবী দূর করার একটি স্বভাবজাত পদ্ধতি।
২০০৮ সালের গবেষক দলের মতে, ঘাসে তেমন পুষ্টিগুণ নেই। যদিও টেক্সাস এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন কলেজ-এর ড. লরি টেলার মনে করেন, কিছু প্রাণী হয়তো ভিটামিন বি-এর মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের জন্য লতাপাতা খেতে পারে। তবে সুষম খাদ্য পাওয়া সুস্থ প্রাণীর ক্ষেত্রে এই কারণ সাধারণত প্রযোজ্য নয়।
সতর্কতার পরামর্শড. টেলার বলেন, “যদি পোষা প্রাণী সুস্থ থাকে, সুষম খাদ্য খায় এবং মাঝে মাঝে ঘাস খায়, তাহলে চিন্তার কারণ নেই। তবে যদি অতিরিক্ত খায় বা ঘন ঘন বমি করে, তখন পশুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।”
ড. লাভজয় জানান, বিড়াল-কুকুরের ঘাস খাওয়া নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, কারণ এটি খুব কম ক্ষেত্রেই গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। তার মতে, বেশিরভাগ সময় প্রাণীরা কেবল স্বাদ, উদ্দীপনা বা পরিবেশ অন্বেষণের জন্য ঘাস খায়।
তবে মালিকদের সতর্ক করে তিনি বলেন, সব উদ্ভিদ প্রাণীর জন্য নিরাপদ নয়। তাই ঘরে বা আঙিনায় থাকা গাছপালার মধ্যে কোনোটি বিষাক্ত কি না, তা আগে যাচাই করা উচিত।
তথ্যসূত্র: লাইভ সায়েন্স
ভোটের কাগজে বীজ, মাটিতে পড়লেই জন্মাবে সবজি
লিফলেট থেকে গাছ জন্মাবে শুনতে অবাক লাগলেও বিষয়টি মোটেই কল্পকাহিনি নয়। আধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির কল্যাণে এমন কাগজ ইতোমধ্যে বাস্তবতা পেয়েছে, যা ব্যবহারের পর মাটিতে ফেললে বা পুঁতে দিলে সেখান থেকে গাছ গজায়। এই বিশেষ ধরনের কাগজ পরিচিত ‘বন-কাগজ’ বা ‘সিড পেপার’ নামে।
এবার এই ধারণার অভিনব প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–এর চেয়ারম্যান তারেক রহমান–সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা ও প্রার্থী প্রচারণায় ব্যবহার করছেন বীজযুক্ত এই বিশেষ লিফলেট। প্রচারণার কাগজ মাটিতে পড়েই যেন সবজির চারা হয়ে ওঠে এমন ধারণা থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
দলীয় নেতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের লক্ষ্য কেবল ভোটারদের কাছে বার্তা পৌঁছানো নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন এবং ‘জিরো ওয়েস্ট’ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। প্রচারণা শেষে যেখানে সাধারণ লিফলেট আবর্জনায় পরিণত হয়, সেখানে বন-কাগজ মাটিতে মিশে গিয়ে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়।
বিশ্বে পরিচিত ধারণা, বাংলাদেশে নতুন প্রয়োগ
যদিও দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এটি নতুন, তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বীজযুক্ত কাগজ একেবারেই অপরিচিত নয়। পরিবেশ রক্ষার অংশ হিসেবে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন, সামাজিক সচেতনতা ও পরিবেশ আন্দোলনে সিড পেপার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পোস্টার, আমন্ত্রণপত্র এমনকি ব্যবসায়িক কার্ডেও এই কাগজের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।
কীভাবে তৈরি হয় বন-কাগজ
বন-কাগজ তৈরির প্রক্রিয়াটিও পরিবেশবান্ধব। ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করে প্রথমে ছোট টুকরো করা হয়। এরপর প্রায় ৪২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে কাগজকে সম্পূর্ণ গলিয়ে নেওয়া হয়। এই গলিত কাগজ থেকে তৈরি হয় মণ্ড। নির্দিষ্ট ফ্রেমে সেই মণ্ড ঢেলে বিশেষ কৌশলে এর সঙ্গে বীজ যুক্ত করা হয়, যাতে কাগজ শুকানোর সময় বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট না হয়। শেষে শুকিয়ে তৈরি হয় লিফলেট বা পোস্টার।
কীভাবে গাছ জন্মায় এই কাগজ থেকে
বন-কাগজের ভেতরে থাকা বীজ মাটির সংস্পর্শে এলে এবং পর্যাপ্ত আর্দ্রতা পেলে ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়। পুরো লিফলেট অথবা ছোট টুকরো করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায়। মাটি শুষ্ক হলে হালকা পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিলেই যথেষ্ট। উপযুক্ত পরিবেশে একটি বন-কাগজ থেকেই ধীরে ধীরে চারা গজিয়ে গাছে পরিণত হয়। এই কাগজ এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে, অর্থাৎ তৈরি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মাটিতে ফেললে গাছ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।
কোন বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে
এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় পাঁচ ধরনের দেশি সবজির বীজ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো বেগুন, টমেটো, মরিচ, লালশাক ও ডাঁটাশাক। এসব সবজি সহজে জন্মায় এবং ঘরোয়া পরিবেশে পরিচর্যাও তুলনামূলক কম লাগে। তাই কেউ চাইলে বারান্দা বা ছাদের টবে এই লিফলেট পুঁতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সবজির চারা পেতে পারেন। এক মাসের মধ্যেই মিলতে পারে নিজ হাতে ফলানো সবজি।
খরচ বেশি, সুফল দীর্ঘমেয়াদি
সাধারণ কাগজের তুলনায় বন-কাগজের খরচ কিছুটা বেশি। প্রতিটি সিড পেপার লিফলেট তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৮ টাকা। তবে উদ্যোক্তারা মনে করেন, পরিবেশ দূষণ কমানো, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং বর্জ্যহীন প্রচারণার সুফল বিবেচনায় এই ব্যয় যুক্তিসংগত। পরিবেশবিদদের মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।
রাজনীতির কাগজ যদি মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে ওঠে তাহলে সেটিই হয়তো হবে প্রচারণার সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা।
সবাই যেদিকে যায় সেদিকে সে নেই: ভাইরাল পেঙ্গুইনের একাকী যাত্রার নেপথ্য কাহিনী

মোঃ আশিকুজ্জামান
নিজস্ব প্রতিবেদক
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি একাকী পেঙ্গুইন তার দল ছেড়ে বিশাল বরফাবৃত পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটি আসলে কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয় বরং এটি ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জার্মান চলচ্চিত্র নির্মাতা ভার্নার হারজগের বিখ্যাত ডকুমেন্টারি 'এনকাউন্টারস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' থেকে নেওয়া একটি অংশ। ভিডিওর সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে দেখা যায় এন্টার্কটিকার একদল অ্যাডেলি পেঙ্গুইন তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সমুদ্রের খাবারের সন্ধানে এগোচ্ছে ঠিক তখনই একটি পেঙ্গুইন হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এবং দল ছেড়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে অর্থাৎ জনমানবহীন ও প্রাণহীন বিশাল এক পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করে। পরিচালক হারজগ এই একাকী পথচলাকে একটি 'ডেথ মার্চ' বা মৃত্যুর পথে যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কারণ পাহাড়ের সেই প্রতিকূল পরিবেশে কোনো খাবারের অস্তিত্ব নেই এবং এই পথচলা পেঙ্গুইনটির নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে। বিজ্ঞানীরাও এই অদ্ভুত আচরণ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে এমনকি পেঙ্গুইনটিকে জোর করে তার দলের কাছে ফিরিয়ে আনলেও সে আবারও একই জেদ নিয়ে পাহাড়ের দিকেই হাঁটতে শুরু করবে।
২০২৬ সালে এসে এই ভিডিওটি নতুন করে ভাইরাল হওয়ার পেছনে কাজ করছে এক গভীর আবেগীয় ও প্রতীকী কারণ। বর্তমান সময়ের মানুষ যারা তীব্র মানসিক চাপ বা 'বার্নআউট'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা এই পেঙ্গুইনটির একাকী ও লক্ষ্যহীন পথচলার মাঝে নিজেদের জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছেন। অনেকে সামাজিক প্রথা বা গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মতো চলার এক প্রতীকী সাহস হিসেবে একে দেখছেন যদিও সেই পথটি শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি 'হোপকোর' বা অনুপ্রেরণামূলক ক্যাটাগরিতে শেয়ার হচ্ছে যেখানে অনেকেই লিখছেন যে সে হয়তো নিজের গন্তব্য পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে নিজের ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার সাহস যুগিয়েছে। এই চর্চা আরও গতি পায় যখন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়ে একটি পোস্ট করেন তবে সেই পোস্টে গ্রিনল্যান্ড ও পেঙ্গুইনের অবস্থান নিয়ে ভৌগোলিক ভুল থাকায় তা ইন্টারনেটে হাস্যরসের সৃষ্টি করে।
মানুষ এই ঘটনাকে দার্শনিক বা বীরত্বপূর্ণ রূপ দিলেও বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অবশ্য বেশ নিস্পৃহ ও সরাসরি। তাঁদের মতে এই পেঙ্গুইনটির আচরণে কোনো মহান উদ্দেশ্য বা সাহসিকতা নেই বরং এটি মূলত একটি স্নায়বিক বিভ্রান্তি বা 'ডিসঅরিয়েন্টেশন'। পেঙ্গুইনরা সাধারণত সমুদ্রের দিক নির্ণয় করার জন্য প্রকৃতির কিছু নির্দিষ্ট সংকেত ব্যবহার করে থাকে কিন্তু কোনো কারণে এই পেঙ্গুইনটির মস্তিষ্ক সেই সংকেত বুঝতে ভুল করেছিল অথবা কোনো স্নায়বিক সমস্যার কারণে সে সঠিক দিক হারিয়ে ফেলেছিল। তবে বিজ্ঞানের এই নিরস ব্যাখ্যার চেয়ে মানুষের কাছে এটি এখন আর কেবল একটি পাখির ভুল হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি একাকিত্ব, মানসিক অবসাদ এবং প্রথা ভাঙার এক গভীর আবেগীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে যা ২০ বছর আগের একটি ডকুমেন্টারি দৃশ্যকে আজ ইন্টারনেটের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে রূপান্তর করেছে।
যে দেশে মা ও দাদির সাথে সুর মিলিয়ে কান্না না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় বিয়ে
বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিয়ে মানেই উৎসব ও নাচের আয়োজন হলেও চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টুজিয়া সম্প্রদায়ের রীতি একদম ভিন্ন। এখানে বিয়ের আগে কনের কান্না করাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য হিসেবে দেখা হয়। কিং রাজবংশের শেষ যুগ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথাটি বর্তমানে আধুনিক শহরগুলোতে কমে গেলেও গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকায় এখনও টিকে আছে। এটি কেবল চোখের জল নয় বরং একটি সংগীতময় প্রকাশ যাকে ক্রাই সং বলা হয়। কনে এই গানের মাধ্যমে তার পরিবার ও মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং নতুন জীবনে প্রবেশের আবেগ প্রকাশ করে।
বিয়ের অন্তত এক মাস আগে থেকেই কনেকে প্রতিদিন কান্নার এই প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। প্রথা অনুযায়ী কনে প্রতিদিন রাতে একটি বিশেষ ঘরে বসে এক ঘণ্টা করে কাঁদে। দশ দিন পর তার সাথে যোগ দেন মা এবং আরও দশ দিন পর দাদি বা নানি সহ পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক নারীরা এই কান্নার আসরে সামিল হন। অনেক ক্ষেত্রে কনের বান্ধবীরাও একত্রিত হয়ে কাঁদে এবং গান গায় যা টেন সিস্টার গ্যাদারিং নামে পরিচিত। এই দীর্ঘমেয়াদী কান্নার প্রক্রিয়াটি জুও তাং বা হলে বসে থাকা হিসেবে টুজিয়া সমাজে সমাদৃত।
প্রাচীনকালে এই কান্নার পেছনে একটি সামাজিক বিদ্রোহের দিকও ছিল। তখন মেয়েদের বিয়ে সাধারণত ঘটক বা মা-বাবার পছন্দে হতো বলে কনে কান্নার মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরত। এমনকি প্রথা অনুযায়ী কনে যদি যথেষ্ট পরিমাণ না কাঁদতে পারত তবে তাকে অশিক্ষিত বা নিচু পরিবারের মেয়ে হিসেবে সামাজিকভাবে সমালোচনা করা হতো। অনেক সময় কনের মা তাকে পর্যাপ্ত কান্নার জন্য শাস্তিও দিতেন। কান্নার গানের লিরিক্সে অনেক সময় ঘটককে তিরস্কার করার বিষয়টিও উঠে আসত যা এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদের প্রতীক ছিল।
বর্তমানে টুজিয়া সম্প্রদায়ের এই প্রথাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর হিসেবে দেখা হয়। কান্নার মাধ্যমে কনে তার ফেলে আসা জীবনের সব স্মৃতি ও দুঃখকে বিদায় জানিয়ে নতুন জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। গ্রামীণ ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ মনে করে এই রীতি কনের সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। আধুনিক জীবনের প্রভাবে অনেক কিছু বদলে গেলেও টুজিয়াদের এই ক্রাইং ম্যারেজ আজও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সূত্র: ডেইলি চায়না
এক চড়, দশ হাজার টাকা, আর চিরকালের নত মেরুদণ্ড
ব্রিটিশ শাসনামলে একদিন এক ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা রাগের বশে এক তরুণ ভারতীয় যুবকের গালে সপাটে চড় বসান। মুহূর্তের মধ্যেই যা ঘটল, তা উপনিবেশিক অহংকারের ইতিহাসে বিরল। কোনো দ্বিধা না করে সেই তরুণ পূর্ণ শক্তিতে পাল্টা চড় মারল। আঘাতে ইংরেজ কর্মকর্তা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বিস্ময়, অপমান আর অবিশ্বাস একসঙ্গে তাকে গ্রাস করল। কীভাবে এক “সাধারণ” ভারতীয় যুবক সাহস পেল এমন এক সামরিক কর্মকর্তার গায়ে হাত তুলতে, যে সাম্রাজ্যের সূর্য নাকি কখনো অস্ত যেত না।
ক্ষুব্ধ কর্মকর্তা ছুটে গেলেন তাঁর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের কাছে। দাবি একটাই, কঠোর শাস্তি। কিন্তু প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীতে কমান্ডার শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওই যুবককে শাস্তি নয়, পুরস্কৃত করতে হবে। পুরস্কার হিসেবে তাকে দিতে হবে দশ হাজার রুপি। শুনে ইংরেজ কর্মকর্তা বিস্ফোরিত হলেন। এটি কেবল ব্যক্তিগত অপমান নয়, ব্রিটিশ রাণীর অপমান, আর তার জবাবে পুরস্কার। কিন্তু আদেশ আদেশই। আপত্তির কোনো সুযোগ নেই।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্মকর্তা সেই ভারতীয় যুবকের হাতে দশ হাজার রুপি তুলে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। যুবক টাকা নিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলে গেল একদিন নিজের দেশেই এক ঔপনিবেশিক কর্মকর্তার হাতে অপমানিত হওয়ার কথা। সে সময় দশ হাজার রুপি ছিল অকল্পনীয় সম্পদ। সে অর্থ কাজে লাগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সে হয়ে উঠল ধনী, সমাজে সম্মানিত, প্রভাবশালী। একসময়ের সাধারণ মানুষ এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি।
বছর কেটে গেল। একদিন সেই একই ঊর্ধ্বতন কমান্ডার আবার তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাকে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন, ওই ভারতীয়কে কি মনে আছে। কর্মকর্তার চোখে তৎক্ষণাৎ পুরোনো অপমান জ্বলে উঠল। কমান্ডার তখন বললেন, সময় এসেছে। যাও, তাকে খুঁজে বের করো এবং সবার সামনে আবার গালে চড় মারো।
ভয়ে কাঁপতে লাগল কর্মকর্তা। সে বলল, তখন সে গরিব ছিল, তবু প্রতিশোধ নিয়েছিল। এখন সে ধনী, প্রভাবশালী। এবার সে আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কমান্ডার কঠোর স্বরে বললেন, এটিও আদেশ।
আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। কর্মকর্তা গেলেন। সবার সামনে সেই ভারতীয়কে চড় মারলেন। কিন্তু এবার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো পাল্টা প্রতিক্রিয়া নেই। লোকটি চোখ তুলেও তাকাল না। নীরবে অপমান সহ্য করল।
হতবাক কর্মকর্তা ফিরে এসে কমান্ডারকে সব বললেন। তখন কমান্ডার ধীরে, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, প্রথমবার ওই যুবকের কাছে ছিল শুধু তার সম্মান। সেটাই ছিল তার সবকিছু। তাই সে প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু আজ সে আর সম্মান রক্ষা করল না, কারণ এখন তার কাছে এমন কিছু আছে, যা সে সম্মানের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে, তার সম্পদ। যেদিন সে ওই দশ হাজার রুপি গ্রহণ করেছিল, সেদিনই সে নিজের মর্যাদা বিক্রি করে দিয়েছিল। আর যে মানুষ নিজের আত্মসম্মান বিক্রি করে, তার মেরুদণ্ড চিরতরে নুয়ে যায়।
এই গল্প কেবল অতীতের কোনো উপনিবেশিক উপাখ্যান নয়। এটি আজকের জন্য এক নির্মম আয়না। আমরা কতবার সত্যকে চেপে গেছি সুবিধার জন্য। কতবার না জেনে কাউকে কলঙ্কিত করেছি। কতবার অবস্থান, উপহার কিংবা লোভের কাছে মাথা নত করেছি। প্রতিবারই হয়তো আমরা আমাদের আত্মসম্মানের এক একটি অংশ বিক্রি করেছি।
এখনই সময় নিজেকে প্রশ্ন করার। আমরা কি আমাদের হৃদয় ও বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করছি। ক্ষমা চাইবার সময় এখনই, যাতে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষত থাকে। পদ, উপহার কিংবা লোভের কাছে কখনো নত না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই মানুষের আসল পরিচয়। প্রশ্ন একটাই, আমরা কি সেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব।
(অনূদিত)
কেন ১ জানুয়ারি নতুন বছর? জানুন এর পেছনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস
পৃথিবীজুড়ে আতশবাজি আর উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, বছরের শুরুর এই দিনটি সবসময় ১ জানুয়ারি ছিল না। প্রাচীন রোমান ক্যালেন্ডারে বছরের শুরু হতো ১ মার্চ থেকে এবং বছরে মাস ছিল মাত্র ১০টি। যার রেশ আজও রয়ে গেছে আমাদের ক্যালেন্ডারে; ল্যাটিন শব্দ 'Septem' মানে ৭, সেই হিসেবে সেপ্টেম্বর ছিল সপ্তম মাস এবং 'Decem' মানে ১০ অনুযায়ী ডিসেম্বর ছিল দশম মাস। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের অসামঞ্জস্য দূর করতেই শুরু হয় সংস্কার।
খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের পরামর্শে ‘জুলিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন। সিজারই প্রথম জানুয়ারির ১ তারিখকে বছরের শুরু হিসেবে ঘোষণা করেন। এই মাসের নামকরণ করা হয়েছিল রোমান দেবতা ‘জানুস’-এর নামানুসারে। জানুসের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর দুটি মুখ—একটি পেছনের দিকে (অতীত দেখার জন্য) এবং অন্যটি সামনের দিকে (ভবিষ্যৎ দেখার জন্য)। নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে এই মাসটিকেই বছরের সূচনার জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়।
রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগে ইউরোপের অনেক দেশ ধর্মীয় কারণে ১ জানুয়ারিকে বছরের শুরু হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা ২৫ ডিসেম্বর বা ২৫ মার্চকে বছরের শুরু হিসেবে পালন করত। তবে ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ক্যালেন্ডারের ভুল সংশোধন করে ‘গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার’ প্রবর্তন করেন এবং পুনরায় ১ জানুয়ারিকে বছরের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং বর্তমানের সার্বজনীন ক্যালেন্ডারে রূপ নেয়।
বর্তমানে ১ জানুয়ারি কেবল একটি তারিখ পরিবর্তনের দিন নয়, বরং বিশ্বজুড়ে প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগের একটি সাধারণ মানদণ্ড। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রোমান দেবতা জানুসের সেই শিক্ষা—অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকাতে। হাজার বছরের সংস্কার আর বিবর্তন পেরিয়ে আজ এই দিনটি বিশ্বের বৃহত্তম ও সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।
সূত্র : হিন্দুস্তান টাইমস
গাছ কাটলে গাছের কি সত্যিই ব্যথা লাগে? বিজ্ঞান কী বলে
গাছের কি ব্যথা লাগে-এই প্রশ্নটি অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। উদ্ভিদের শরীরে কোনো ব্যথা অনুভবকারী রিসেপ্টর, স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক নেই। ফলে প্রাণিজগতের সদস্য হিসেবে মানুষ বা পশু যেভাবে ব্যথা অনুভব করে, উদ্ভিদ সেই অর্থে ব্যথা অনুভব করতে সক্ষম নয়। তাই একটি গাজর মাটি থেকে তুলে নেওয়া, ঝোপঝাড় ছাঁটা বা একটি আপেল কামড়ে খাওয়া কোনোভাবেই ‘উদ্ভিদ নির্যাতন’ হিসেবে বিবেচিত হয় না।
তবে বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, উদ্ভিদ সম্পূর্ণ সংবেদনশূন্য নয়। তারা শারীরিক উদ্দীপনা, স্পর্শ বা ক্ষতির উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারে যদিও সেটি ব্যথা নয়, বরং জৈব-রাসায়নিক ও কোষীয় প্রতিক্রিয়া।
কিছু উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা আমাদের চোখেই ধরা পড়ে। যেমন ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ নামের উদ্ভিদটি অর্ধ সেকেন্ডের মধ্যেই পাতা বন্ধ করে শিকার ধরে ফেলতে পারে। আবার লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ পেলেই পাতা গুটিয়ে নেয়, যা সম্ভাব্য তৃণভোজী প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখার একটি প্রতিরক্ষামূলক কৌশল বলে মনে করা হয়। এই উদ্ভিদগুলোর আচরণে স্পষ্টতই একধরনের সংবেদনশীল ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায়।
তবে আরও বিস্ময়কর তথ্য এসেছে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে। দেখা গেছে, সাধারণ সরিষা জাতের একটি উদ্ভিদ যা গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত পাতায় পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে কোষীয় স্তরে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাতে পারে। এই সংকেত এক পাতা থেকে আরেক পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং উদ্ভিদকে সতর্ক করে দেয় যেন সে দ্রুত রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে। ফলে শুঁয়োপোকা বা এফিডের মতো ক্ষতিকর পোকা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
এই বৈদ্যুতিক সংকেত শুনে অনেকের মনে হতে পারে, উদ্ভিদ বুঝি ব্যথা পাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে বলছেন, এই সংকেত কোনোভাবেই প্রাণীর ব্যথার সংকেতের মতো নয়। এখানে কোনো অনুভূত যন্ত্রণা নেই, নেই সচেতন কষ্টবোধ। এটি নিছক একটি প্রতিরক্ষামূলক সংকেত ব্যবস্থা, যা উদ্ভিদের টিকে থাকার কৌশলের অংশ।
উদ্ভিদ আলো, মাধ্যাকর্ষণ, বাতাসের প্রবাহ এমনকি ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের আক্রমণও শনাক্ত করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভূতির ফল নয়, বরং কোটি কোটি বছরের বিবর্তনে গড়ে ওঠা জৈবিক অভিযোজন। উদ্ভিদের জীবনধারা ‘কষ্ট বনাম সুখ’ দিয়ে পরিচালিত নয়; বরং এটি পরিচালিত হয় টিকে থাকা বা বিলুপ্তির সরল বাস্তবতায়।
সুতরাং, উদ্ভিদের এই অসাধারণ সক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করলেও, তাদের মানুষের মতো ব্যথা অনুভবকারী জীব হিসেবে কল্পনা করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। উদ্ভিদ অনুভব করে না—তারা প্রতিক্রিয়া জানায়।
সূত্র: ব্রিটানিকা
অলিম্পিক স্বর্ণপদক কি সত্যিই খাঁটি সোনা, জানুন ইতিহাস
অলিম্পিকের মঞ্চে সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে গলায় স্বর্ণপদক পরার মুহূর্তটি যেকোনো ক্রীড়াবিদের কাছে অমূল্য। তবে আবেগের দিক থেকে যতটাই মূল্যবান হোক না কেন, বাস্তব অর্থমূল্যের বিচারে অলিম্পিক স্বর্ণপদক রুপার পদকের চেয়ে খুব বেশি দামী নয়। এর কারণ হলো, অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণপদক আসলে সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি নয়।
অলিম্পিক গেমস–এর বিধিমালা অনুযায়ী, স্বর্ণপদকে কমপক্ষে ৯২.৫ শতাংশ রুপা থাকতে হয় এবং তার ওপরে মাত্র প্রায় ছয় গ্রাম খাঁটি সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। একইভাবে রুপার পদকও ৯২.৫ শতাংশ রুপা দিয়ে তৈরি হয়। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ পদক বানানো হয় তামা ও বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে। ফলে স্বর্ণ ও রুপার পদকের উপাদানগত পার্থক্য খুবই সীমিত।
পদক প্রদানের এই রীতি আদতে খুব প্রাচীন নয়। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয় ১৮৯৬ সালে গ্রিসের এথেন্সে। তবে সে সময়কার পদকগুলো আজকের পরিচিত স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ কাঠামোর মতো ছিল না। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসরে বিজয়ীদের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়নি।
প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস আরও পেছনে গেলে দেখা যায়, প্রায় ২ হাজার ৮০০ বছর আগে, খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে শুরু হওয়া প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের মাথায় পরানো হতো বিজয়ের মুকুট। এসব মুকুট সাধারণত স্থানীয় উদ্ভিদ যেমন লরেল পাতা বা জলপাই শাখা দিয়ে তৈরি করা হতো। তখন পদকের ধারণাই ছিল না।
১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো পদক প্রদান শুরু হলেও সেখানে মাত্র দুটি পদক দেওয়া হতো। প্রথম স্থান অধিকারী পেতেন রুপার পদক এবং দ্বিতীয় স্থান পাওয়া প্রতিযোগী পেতেন তামার পদক। তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের জন্য কোনো পুরস্কারই নির্ধারিত ছিল না।
এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। সে আসরে কিছু খেলায় প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং তখনই স্বর্ণ, রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকের ধারণা চালু হয়। তবে সেবার পদকগুলো ছিল আয়তাকার, যা অলিম্পিক ইতিহাসে একমাত্র ব্যতিক্রম। সেই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে পদকের পরিবর্তে ট্রফি বা শিল্পকর্মও দেওয়া হয়েছিল।
১৯০৪ সালের পর থেকে স্বর্ণ–রুপা–ব্রোঞ্জ পদকের রীতি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১২ সালের অলিম্পিকে দেওয়া স্বর্ণপদক সত্যিকার অর্থেই খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯১৬ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় খাঁটি সোনার পদক দেওয়া আর সম্ভব হয়নি।
বর্তমানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পদকের ধাতব গঠন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেও, আয়োজক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে পদকে বিশেষ উপাদান যোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। যেমন, ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে পদকে জেড পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।
একই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে প্রতিটি পদকের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক আইফেল টাওয়ার–এর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এর মাধ্যমে অলিম্পিক পদক কেবল একটি পুরস্কার নয়, বরং আয়োজক শহরের ইতিহাস ও পরিচয়ের প্রতীক হিসেবেও নতুন মাত্রা পেয়েছে।
সূত্র: ব্রিটানিকা
ইন্টারনেট ছাড়াই চলবে গুগল ম্যাপস: জেনে নিন অফলাইন ব্যবহারের নিয়ম
অচেনা কোনো শহর বা নতুন কোনো গন্তব্যে যাওয়ার পথে বর্তমানে গুগল ম্যাপস আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবে অনেক সময় নেটওয়ার্কের দুর্বলতা কিংবা ইন্টারনেট প্যাকেজ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝপথে বিপাকে পড়তে হয়। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা বা বিদেশ ভ্রমণের সময় নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবহারকারীদের এই ভোগান্তি দূর করতে গুগল ম্যাপসে রয়েছে ‘অফলাইন’ সুবিধা যা সক্রিয় থাকলে কোনো ধরনের ইন্টারনেট ডাটা ছাড়াই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন মোড ব্যবহারের পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর। এটি ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীকে প্রথমে স্মার্টফোনের গুগল ম্যাপস অ্যাপে প্রবেশ করে প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে। সেখানে থাকা 'অফলাইন ম্যাপস' অপশনে গিয়ে ‘সিলেক্ট ইয়োর ওউন ম্যাপ’ নির্বাচন করতে হবে। এরপর যে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহরের মানচিত্র ভবিষ্যতে অফলাইনে ব্যবহারের প্রয়োজন তা জুম ইন বা আউট করে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে ডাউনলোড বাটনে প্রেস করলেই সেই এলাকার মানচিত্রটি ফোনের মেমোরিতে জমা হয়ে যাবে। একবার সফলভাবে ডাউনলোড হয়ে গেলে পরবর্তী যেকোনো সময় ইন্টারনেট ছাড়াই ওই এলাকার পথঘাট দেখা যাবে।
গুগল ম্যাপসের এই অফলাইন সংস্করণে গাড়ি চালানোর দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুবিধা থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় রাস্তার রিয়েল-টাইম ট্রাফিক পরিস্থিতি বা জ্যামের খবর জানা সম্ভব হয় না। এছাড়া বিকল্প রুট এবং গণপরিবহনের সঠিক সময়সূচিও এই মোডে দেখা যাবে না। তবে ইন্টারনেট ছাড়াই স্মার্টফোনের জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সবসময় সক্রিয় থাকে যা ডাউনলোড করা মানচিত্রের ওপর ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান ও গন্তব্যের দূরত্ব নিখুঁতভাবে দেখাতে পারে।
ভ্রমণপিপাসুদের জন্য এই ফিচারটি আশীর্বাদস্বরূপ কারণ বিদেশের মাটিতে দামী ইন্টারন্যাশনাল রোমিং বা লোকাল সিম কার্ডের ডাটা খরচ না করেই তারা মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। ভ্রমণের আগেই প্রয়োজনীয় শহরের ম্যাপ ডাউনলোড করে রাখলে স্মার্টফোনটি অনেকটা পুরোনো আমলের পকেট ম্যাপের মতোই কার্যকর হয়ে ওঠে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অফলাইন নেভিগেশনের এই সুবিধা কেবল ডেটাই সাশ্রয় করে না বরং জরুরি মুহূর্তে পথ হারানোর ভয় থেকেও ব্যবহারকারীকে সুরক্ষিত রাখে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
জিমেইল স্টোরেজ ফুল? টাকা খরচ না করে জায়গা খালি করার ৫ উপায়
বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগাযোগে জিমেইল একটি অপরিহার্য মাধ্যম। তবে গুগলের নির্ধারিত ১৫ জিবি স্টোরেজ দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যবহারকারীরা বিপাকে পড়েন। স্টোরেজ পূর্ণ থাকলে গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইলগুলো প্রাপকের কাছে না পৌঁছে ফিরে আসে অথবা অনেক ক্ষেত্রে নতুন মেইল আসাও বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে গুগল অতিরিক্ত স্টোরেজের জন্য অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার প্রস্তাব দিলেও সামান্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে কোনো খরচ ছাড়াই এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব।
জিমেইলের জায়গা খালি করার জন্য প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ট্র্যাশ এবং স্প্যাম ফোল্ডারের দিকে। সাধারণত মুছে ফেলা ই-মেইলগুলো সরাসরি ডিলিট না হয়ে ট্র্যাশ ফোল্ডারে ৩০ দিন পর্যন্ত জমা থাকে যা অযথাই স্টোরেজ দখল করে রাখে। নিয়মিত এই ফোল্ডারগুলো ম্যানুয়ালি খালি করার মাধ্যমে অনেকটা জায়গা তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধার করা যায়। এছাড়া ই-মেইলের বড় অ্যাটাচমেন্টগুলো স্টোরেজ পূর্ণ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। জিমেইলের সার্চ বক্সে বিশেষ কোড ব্যবহার করে ১০ মেগাবাইটের বেশি সাইজের ই-মেইলগুলো চিহ্নিত করে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো ডিলিট করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা অপ্রয়োজনীয় নিউজলেটার জিমেইলের প্রমোশন ট্যাবে জমে থেকে ইনবক্সকে ভারী করে তোলে। নিয়মিতভাবে এই ধরনের নিউজলেটারগুলো আনসাবস্ক্রাইব করলে ভবিষ্যৎ স্টোরেজ অপচয় রোধ করা যায়। এছাড়া গুগলের ‘ওয়ান স্টোরেজ ম্যানেজার’ টুলটি ব্যবহার করে এক নজরে ড্রাইভ, ফটোস এবং জিমেইলের বড় ফাইলগুলো দেখে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। বড় সাইজের ছবি বা ভিডিও সরাসরি মেইলে না পাঠিয়ে গুগল ড্রাইভের লিংক শেয়ার করাও স্টোরেজ সাশ্রয়ের একটি আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জিমেইলের স্টোরেজ পূর্ণ হওয়া মানেই টাকা খরচ করে নতুন মেমোরি কেনা নয় বরং ডিজিটাল হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাই এর মূল সমাধান। নিয়মিত ইনবক্স পরিষ্কার রাখা এবং ক্লাউড স্টোরেজের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা বছরের পর বছর কোনো চার্জ ছাড়াই জিমেইলের নিরবচ্ছিন্ন সেবা উপভোগ করতে পারবেন। এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে কেবল স্টোরেজই বাঁচবে না বরং জিমেইলের গতি ও কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পাবে।
পাঠকের মতামত:
- ভোটে কোনো কারচুপি বা ইঞ্জিনিয়ারিং হলে কঠোর প্রতিরোধের ঘোষণা
- ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পোলিং অফিসারের মৃত্যু
- ঢাকা-৮ কেন্দ্রে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা
- যাদের ওপর রোজা ফরজ নয় এবং তাদের করণীয়
- উত্তম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য হাদিসের আলোকে দোয়া
- গাংনীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ
- ভোট দিয়ে জয়ে শতভাগ আশাবাদী তারেক রহমান
- সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
- আবার বাড়ছে স্বর্ণের দাম, কী কারণ?
- নিশ্চিন্তে কেন্দ্রে আসুন, পরিবেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে: সেনাপ্রধান
- মুজিবনগরে বিএনপি-জামায়াত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
- পাতানো নির্বাচনের দিন শেষ: সিইসি
- নারী এজেন্টদের হেনস্তা করা হচ্ছে: তাসনিম জারা
- ভয়ের কিছু নেই, ভোট হবে উৎসবের: হাসনাত আবদুল্লাহ
- ১৭ বছরের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা শেষ: ভোটারদের চোখেমুখে মুক্তির হাসি
- আজ নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন: ডক্টর ইউনূস
- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল
- ঈদের ছুটিও হার মানল: ভোটাধিকার প্রয়োগের টানে ঢাকা ছাড়ল এক কোটি মানুষ!
- সুষ্ঠু ভোট হলে যেকোনো ফলাফল মেনে নেবে জামায়াত: ডা. শফিকুর রহমান
- দাঁড়িয়ে দেখার দিন শেষ, এবার ভোট দিয়ে অধিকার বুঝে নেওয়ার পালা: মির্জা ফখরুল
- জেনে নিন ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আজকের নামাজের ওয়াক্ত
- হাসিনা-খালেদা ছাড়াই প্রথম ভোট: আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন দিনের বার্তা
- ১১ দলীয় জোট সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে: নাহিদ ইসলাম
- উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট
- অসুস্থ রিজভীকে দেখতে হাসপাতালে তারেক রহমান
- টাকা বহন নিয়ে আগের বক্তব্য অস্বীকার করলেন ইসি সচিব
- ভোটের আগে নগদ টাকা বিলি! হাতেনাতে ধরা পড়ে জেলে জামায়াত নেতা
- এবার আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো না, জালিয়াতি রুখে দেব: আসিফ মাহমুদ
- চাঁদাবাজ ধরতে নাসিরুদ্দীনের নতুন সাইট ‘চান্দাবাজ ডট কম’
- নির্বাচনে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে লন্ডনে উদ্বেগ: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা
- রমজানে ওমরাহ করার ফজিলত: হাদিসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- উৎসবের আমেজে ভোট দিন: শান্তি রক্ষায় দেশবাসীর সহযোগিতা চাইলেন সিইসি
- শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ: বাজারের ভেতরের আসল চিত্র কী বলছে?
- ভোটের বাধা রুখতে জনতার প্রতিরোধ গড়ার ডাক দিলেন জামায়াত নেতা জুবায়ের
- ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরপতনের শেয়ার
- শীর্ষ আলেম-উলামাদের সমর্থনে আবেগাপ্লুত তারেক রহমান, জানালেন গভীর কৃতজ্ঞতা
- ডিএসইতে শীর্ষ ১০ দরবৃদ্ধিকারী শেয়ার
- বিএনপি প্রার্থী হাবিবুর রশিদকে সমর্থন জানিয়ে ইনকিলাব মঞ্চের জাবেরের পোস্ট
- ইসলামী পোশাকের অপব্যবহার রুখুন: মাহদী আমিন
- ৫০ নয়, জামায়াত নেতা বেলাল উদ্দিনের ব্যাগে ছিল ৭৪ লাখ টাকা
- প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন? এক নজরে দেখে নিন ভোটকেন্দ্রের বিস্তারিত নিয়মাবলি
- টাকা বৈধ হলে ৫ কোটি বহনেও বাধা নেই: ইসি সচিব
- ২০০৮–এর পর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন: গণতন্ত্রের গুণগত মানের এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা
- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল: পার্থক্য কী?
- ছোট ভুলেই বাতিল হতে পারে আপনার ভোট
- ৫০ লাখ টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমির আটক
- শনিবার যেসব এলাকায় খোলা থাকবে ব্যাংক
- বহিষ্কারের পর আবারও চাপে মঞ্জুরুল মুন্সী
- আজকের মুদ্রার বিনিময় হার: ডলার ও ইউরোর দামে নতুন পরিবর্তন
- খুলনায় ৬৭ শতাংশ কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ: নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পুরো জেলা
- স্বর্ণের দামে বড় ধাক্কা, ভরি মিলবে ২ লাখ ৮ হাজার ২০২ টাকাতে
- ২০০৮–এর পর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন: গণতন্ত্রের গুণগত মানের এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা
- বিশ্ববাজারের প্রভাবে দেশে আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম
- আবার বাড়ছে স্বর্ণের দাম, কী কারণ?
- আইনের রক্ষক পুলিশ কেন ভয়ের প্রতীকে পরিণত হয়?
- স্বর্ণের বাজারে নতুন অস্থিরতা: আজ থেকে কার্যকর স্বর্ণের নতুন চড়া দাম
- নির্বাচনে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে লন্ডনে উদ্বেগ: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা
- আজ কোন কোন এলাকায় গ্যাস থাকবে না জেনে নিন
- পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে কে এগিয়ে? সোচ্চারের জরিপে চমক!
- ১০ ফেব্রুয়ারি আজকের শেয়ারবাজারের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ
- বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার নতুন বিনিময় হার
- স্বর্ণের বাজারে বড় দরপতন: আজ থেকে কার্যকর স্বর্ণের নতুন দাম
- শীত নিয়ে বদলাচ্ছে পূর্বাভাস, জেনে নিন বিস্তারিত
- কালিগঞ্জে ধানের শীষের জনসমুদ্র: সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের হুঙ্কার
- আজ টানা ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে যেসব এলাকা